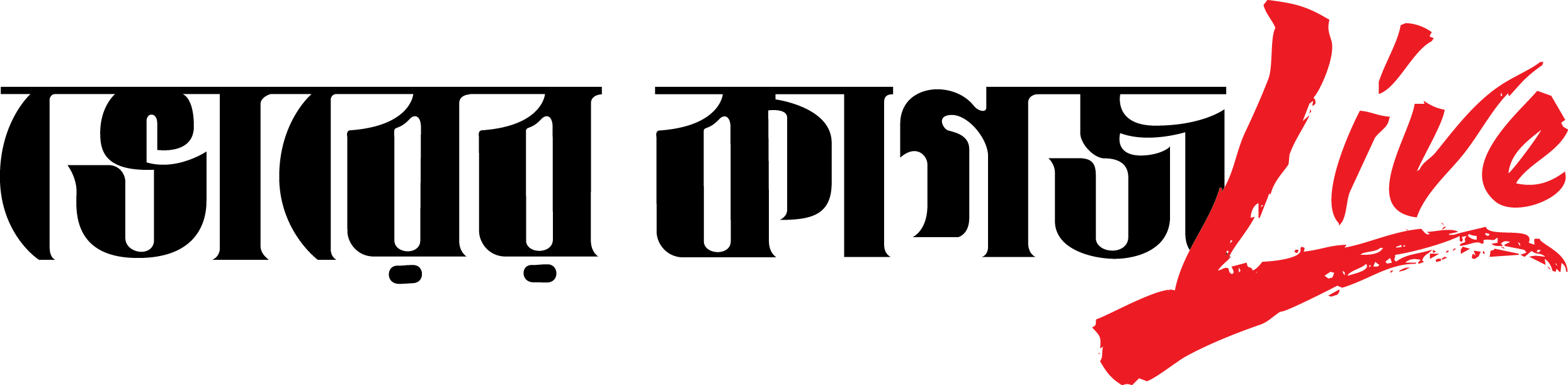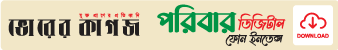বাংলাদেশে চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন ও মুহম্মদ খসরু
কাগজ প্রতিবেদক
প্রকাশ: ৩১ মে ২০১৯, ০৪:১২ পিএম
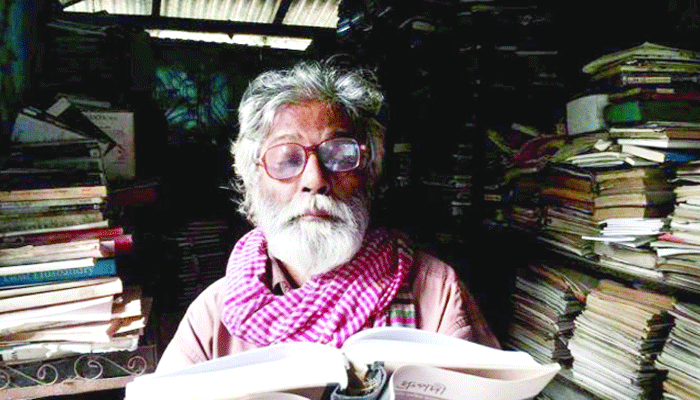
যৌবনে এক সময় জীবনের লক্ষ্য ছিল চলচ্চিত্রের অভিনেতা হওয়া, কখনোবা পরিচালক হওয়া। সে সময় চলচ্চিত্র বিষয়ক বিভিন্ন বই, ম্যাগাজিন, পত্রিকা নিয়মিত পড়তাম। চলচ্চিত্রে সাধারণ খবরাখবরের জন্য ছিল চিত্রালী, পূর্বাণী, ঝিনুক ইত্যাদি নামের পত্রিকা, পরবর্তীতে এলো চিত্রকল্প, তারকালোক ইত্যাদি। সে সময় আমার হাতে ‘ধ্রুপদী’ নামের একটা কাগজ এলো। ধ্রুপদী আমাকে চলচ্চিত্রবিষয়ক গভীর পাঠের দিশা দিলো। ধ্রুপদীর ৫ম সংখ্যাসহ আমার হাতে এসেছিল মোট চারটি সংখ্যা। ধ্রুপদীর পাশাপাশি হাতে এলো ‘চলচ্চিত্র পত্র’ নামে আরও একটি চলচ্চিত্রবিষয়ক কাগজ। সে সংখ্যাটি ছিল সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে, প্রচ্ছদে সত্যজিৎ রায়ের ছবিও ছিল; সত্যজিৎ রায় আমার প্রিয় চলচ্চিত্রকারদের অন্যতম। কাছাকাছি সময়ে ‘ক্যামেরা যখন রইফেল’ নামে কালো মলাটের একটা বই হাতে এলো। ম্যাগাজিন পড়েই আমার পরিচয় হলো সেসব সংকলনের সম্পাদক মুহম্মদ খসরু নামটির সাথে; কেবল পরিচয় নয়, বলা যায় আমি তখন তাঁর মনীষায় অনুরক্ত হয়ে উঠলাম। চলচ্চিত্রের কর্মী হবার জন্য যখন আমি বিভিন্ন চলচ্চিত্র পরিচালক-শিল্পীদের সাথে গোপনে যোগাযোগ করতে চেষ্টা করছি, সে সময় ঢাকায় দু’একবার দূর থেকে আমি দেখেছি বাংলাদেশে ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের পথিকৃৎ মুহম্মদ খসরুকে। নিজের সম্পাদিত ‘ধ্রুপদী’ কাগজের ৫ম সংখ্যায় তাঁর পরিচয় পাই এভাবে
“ষাটের দশকের শুরুতে সংস্কৃতির মাটি খুঁড়ে যারা চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনের বীজ রোপণ করেছিলেন মুহম্মদ খসরু তাঁদের মধ্যে অন্যতম। এবং সেই থেকে তিনি বিরতিহীন ‘চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন’ নামক দীর্ঘ এক ছবি নির্মাণ করে চলেছেন। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদকের গুরুত্বপূর্ণ পদটি ছাড়াও তিনি চলচ্চিত্র সংসদ ফেডারেশনের সহসভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। পেশাগতভাবে তিনি বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থার নকশা কেন্দ্রের আলোকচিত্রী। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত ‘ধ্রæপদী’ ও ‘চলচ্চিত্র পত্র’-এর সম্পাদক।”
মুহম্মদ খসরুকে নিয়ে এবং তাঁর চলচ্চিত্র সংসদ সংশ্লিষ্টতা নিয়ে আলোচনা শুরুর আগে সংক্ষেপে তাঁর পরিচয় সম্পর্কে সামান্য বলে নিতে চাই। মুহম্মদ খসরুর জন্ম পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলায় ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে (কোন কোন তথ্যে ১৯৪৬-এ)। তাঁর বাবা ছিলেন হুগলি জুটমিলের চাকুরে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর তাঁদের পরিবার ১৯৫০-এর প্রথম দিকে ঢাকায় চলে আসে এবং ঢাকার অদূরে কেরানিগঞ্জে আবাস গড়ে তোলে। কেরানিগঞ্জের রুহিতপুরে তাঁর বেড়ে ওঠা। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনের পথিকৃৎ মুহম্মদ খসরু এ দেশে সুস্থধারার চলচ্চিত্রের বিকাশের লক্ষ্যে ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে আগ্রহী তরুণদের বিশ্ব চলচ্চিত্রের সাথে পরিচিত করে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি ইউরোপ-আমেরিকা-আফ্রিকান উল্লেখযোগ্য শিল্পঋদ্ধ চলচ্চিত্র বাংলাদেশে প্রদর্শনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ প্রতিষ্ঠায়ও মুহম্মদ খসরু গুরুত্বপূর্ণ ভ‚মিকা রাখেন। তাঁর প্রণোদনা এবং বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সংসদ ফেডারেশনের দাবির প্রেক্ষিতেই ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ। যদ্দুর জানা যায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অপ্রতুলতার কারণে মুহম্মদ খসরু চলচ্চিত্র বিষয়ক কোনো সরকারি চাকরি করার সুযোগ পাননি। তাঁর সম্পাদিত চলচ্চিত্রবিষয়ক পত্রিকা ধ্রুপদী, চলচ্চিত্র পত্র আর ক্যামেরা যখন রাইফেল ইত্যাদি বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে প্রাগ্রসরতার উল্লেখযোগ্য দলিল। মুহম্মদ খসরু দ্বারা অনুপ্রণিত হয়ে বাংলাদেশের প্রথিতযশা চলচ্চিত্র নির্দেশক মহিউদ্দিন শাকের নির্মাণ করেন সূর্যদীঘল বাড়ি ও দহন, সৈয়দ সালাউদ্দিন জাকি নির্মাণ করেন ঘুড্ডি, বাদল রহমান নির্মাণ করেন এমিলের গোয়েন্দা বাহিনী, তারেক মাসুদ নির্মাণ করেন মুক্তির গান চলচ্চিত্র। তিনি নিজে চলচ্চিত্র নির্মাণে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন না, তবে ভারত-বাংলাদেশের যৌথ প্রযোজনার চলচ্চিত্র রাজেন তরফদার পরিচালিত চলচ্চিত্র ‘পালঙ্ক’র তিনি ছিলেন সহকারী পরিচালক; যে ছবিতে অভিনয় করেছিলেন উৎপল দত্ত, আনোয়ার হোসেন, সন্ধ্যা রায়, ওবায়দুল হক সরকার প্রমুখ শিল্পী। আমরা দেখেছি তিনি বরেণ্য চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক ঘটকের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন, যা সে সময় একাধিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ২০১৯-এর ১৯ ফেব্রুয়ারি মুহম্মদ খসরু ঢাকার বার্ডেম হাসপাতালে পরলোক গমন করেন। চলচ্চিত্র শিল্পে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার জন্য তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যায় চলচ্চিত্র সংসদ কর্তৃক আজীবন সম্মাননা প্রাপ্ত হন ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে; তাঁকে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের পথিকৃৎ ‘হীরালাল সেন পদক’ দিয়ে সম্মনিত করা হয়।
বাংলাদেশে চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনে মুহম্মদ খসরুর অবদান চিহ্নিত করতে এখানে আমি তাঁর সম্পাদিত ধ্রুপদী ৫ম সংখ্যার সূচিপত্রে একবার দৃষ্টি দিতে চাই। উল্লেখ থাকে ধ্রুপদীর প্রতিটি সংখ্যাই ছিল নানান কারণে গুরুত্বপূর্ণ। আশা করা যায় একটি সংখ্যার সূচিতে দৃষ্টি দিলেই পাঠক তাঁর মেধা-মনীষা আর আত্মনিবেদন সম্পর্কে সম্যক ধারণা পেয়ে যাবেন। বর্ণিত সংখ্যার প্রথম রচনাটি ছিল অনুপম হায়াৎ-এর লেখা, বিষয় ছিল ‘ঢাকার ছবির নির্বাক যুগ’; পরবর্তী রচনাগুলো ছিল যথাক্রমে গর্ডন হেইলস-এর ‘আমাদের চার্লি’ (অনুবাদ : শিহাব সরকার), পিটার এস গ্রীনবার্গ-এর ‘কস্তা গাভরাসের সাথে একটি সাক্ষাৎকার’ (অনুবাদ : হাসান ফেরদৌস), হাসনা বেগম-এর ‘চলচ্চিত্রের প্রেক্ষাপটে নারী’, অক্তেভিও গেত্তিনো-এর ‘তৃতীয় চলচ্চিত্রের লক্ষ্যে ফার্নান্দো সোলানাস’ (ভাষান্তর : কাইজার চৌধুরী), মাইকেলাঞ্জেলো আন্তোনিওনী-এর ‘চলচ্চিত্রের অভিনয় প্রসঙ্গে’ (ভাষান্তর : শামসুদ্দিন আবুল কালাম), পল্লল ভট্টাচার্যের ‘পুরনো ভারত নতুন চলচ্চিত্র’, মাহবুব আলম-এর নেয়া ‘মৃণাল সেনের সাক্ষাৎকার’, ইয়েভগেনি ইয়েভতুশেঙ্কো-এর ‘ফেলিনীর দীর্ঘ ভ্রমণ’ (ভাষান্তর : বেলাল চৌধুরী), চিদানন্দ দাশগুপ্ত-এর ‘সত্যজিৎ ও রবীন্দ্রনাথ’ (ভাষান্তর : আ. ও. ম. ফখরুদ্দিন), এবং রবিউল হুসাইন-এর ‘মাধ্যমই মধ্যমণি’। এ ছাড়া এ প্রকাশনায় যুক্ত হয়েছিল ‘সাহিত্যিকের চলচ্চিত্র ভাবনা’ শিরোনামে মহাশ্বেতা দেবী, হাসান আজিজুল হক, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, মাহমুদুল হক, ওবায়দুল হক, শামসুর রাহমান প্রমুখ ছয়জন বিশিষ্ট সাহিত্যিকের চলচ্চিত্রবিষয়ক ভাবনা। প্রকাশনার শেষ সংযোজন ছিল ‘সম্মিলিত সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন’ শিরোনামে সম্পাদক মুহম্মদ খসরুর একটি নাতিদীর্ঘ রচনা।
বিষয়বৈচিত্র্যের কারণে প্রকাশনাটি যতটা ঋদ্ধ ছিল, ততটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল চলচ্চিত্র বিষয়ক আন্তর্জাতিকতা ও প্রজ্ঞায়। বিষয় নির্বাচন এবং নির্বাচিত বিষয়গুলোকে গুণী সৃজনকর্মীদের দিয়ে অনুবাদ করিয়ে নেয়ার যে নিষ্ঠা এবং অধ্যবসায়ের দৃষ্টান্ত এ প্রকাশনায় মুহম্মদ খসরু প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, এক কথায় তা অনন্য। আবার আমরা যদি ধ্রুপদী ৫ম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে চোখ রাখি, দেখবো কী সাহসিকতা আর নিপুণ মুন্সিয়ানায় তিনি চলচ্চিত্র এবং পরিপার্শ্বকে তুলে এনেছেন। আসুন আমরা সম্পাদকীয় থেকে কিছু অংশ পড়ে নিই
“রামদা এসিড নানচাকু, ভিসিআর বু-ফিল্ম, খুন ধর্ষণ, বেশ্যালয় উৎখাত, কেবলই নারীদেহ শোভিত রমরমা রম্য সাময়িকীর মাসিক প্রসব, এফডিসি ভায়োলেন্সে চলচ্চিত্রকার হাসপাতালান্তরিত, রাজনৈতিক নেতৃত্বের দেউলেপনা, আত্মসার বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, জলোচ্ছ্বাসে লক্ষ প্রাণের জীবননাশ, জাতীয় বাজেটে বৈদেশিক
ঋণের স্যালাইন হিংসা-দুর্নীতি-নৈরাজ্য-হতাশা এবং অপশাসনের স্থবিরতায় মাত্র চৌদ্দ বছরের কৈশোরে বুড়িয়ে যাওয়া বাংলাদেশের এই যখন কোলাজ-দৃশ্য ঠিক সেই মুহূর্তে বেরুল ধ্রুপদীর পঞ্চম সংকলন।
আমাদের দেশের বিদ্বৎসমাজ ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও একটি অশিক্ষিত ধারণা প্রচলিত আছে যে চলচ্চিত্র কোনো গভীর বক্তব্য প্রকাশের মাধ্যম হতে পারে না। তাদের ধারণায় চলচ্চিত্র কেবলমাত্র মানুষের চিত্তবিনোদনের চাহিদা মেটাবে। কিন্তু তারা জানে না যে বিংশ শতাব্দীর সবচাইতে বলিষ্ঠতম প্রকাশ মাধ্যম চলচ্চিত্র নিয়ে মজাকী মারার দিন ১৯২৫ সালে, আইজেনস্টাইনের ‘বাটলশিপ পোটেমকিনে’র ওডেসা সিঁড়ির দৃশ্য চলচ্চিত্রায়িত হবার পরই শেষ হয়ে গেছে। চলচ্চিত্র কি শিল্প না, এ ধরনের সাবেকী বিতর্ক নিয়ে অল্প ঢেকুর তোলা একমাত্র গাড়লের পক্ষেই সম্ভব।”
(ধ্রুপদী \ ৫ম সংকলন \ আগস্ট ১৯৮৫ \ সম্পাদকীয়)
মুহম্মদ খসরুর চলচ্চিত্র-সমাজ-সংস্কৃতি বিষয়ক প্রজ্ঞা সম্পর্কে জানতে আমরা একবার তাঁর ‘সম্মিলিত সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন’ শিরোনামের ৩৩ পৃষ্ঠা বিস্তৃত প্রবন্ধের গভীরে প্রবেশ করতে পারি। তাঁর এ প্রবন্ধে মনোনিবেশ করলে আমরা দেখবো তাঁর বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সম্পর্কে আগ্রহ, চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন নিয়ে আশাবাদ, সমাজ-সংস্কৃতি বিষয়ে প্রজ্ঞা এবং প্রাগ্রসর মানুষের সংস্কৃতিচিন্তার বিস্তার কতটা গভীরতা পেতে পারে তার দৃষ্টান্ত। আমার খুব লোভ হচ্ছে, তাঁর এ রচনা থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করি, আশা করা যায় তাঁর এ রচনাটি পাঠ করলে পাঠকমাত্র জেনে যাবেন বিষয়টিকে নিয়ে তাঁর কতটা গভীরতা; “যে কোনো দেশে শিল্প-সংস্কৃতির অগ্রগতির পেছনে সুষ্ঠু ও বাস্তবভিত্তিক সরকারি পরিকল্পনার প্রয়োজন। অন্যথায় তার সার্বিক বিকাশ ও ব্যাপ্তি আদৌ সম্ভব নয়। আমাদের চলচ্চিত্রের উন্নয়নের জন্য সর্ববৃহৎ স্টুডিও এফডিসির কথা বাদ দিলে যে কয়টি সরকারি প্রতিষ্ঠানের ওপর চলচ্চিত্রের প্রযুক্তি ও সাংস্কৃতিক বিকাশের দায়ভাগ বর্তায় তার মধ্যে ফিল্ম আর্কাইভ, শিল্পকলা একাডেমি এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা বিভাগ (ডিএফপি) অন্যতম। এগুলো সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং জাতীয় চলচ্চিত্র উন্নয়নের দায়-দায়িত্ব এইসব প্রতিষ্ঠানের কাঁধে অর্পিত। অথচ এই প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে আজ অবধি চলচ্চিত্রের উন্নতি ও বিকাশের জন্য কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া হয়নি।.....ডিএফপি ইচ্ছা করলে প্রামাণ্য এবং ছোট ছবি নির্মাণের একটি ঐতিহ্য গড়ে তুলতে পারতো। বিভিন্ন চলচ্চিত্র সংসদের তরুণরা নানা বিষয়ে ছোট ছবি এবং প্রামাণ্য চিত্রনাট্য পকেটে নিয়ে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর্থিক আনুক‚ল্য পাওয়ার জন্য। ডিএফপির উচিত ছিল এইসব তরুণদের আর্থিক অনুদান ও যান্ত্রিক সহায়তা দিয়ে তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথকে সুগম করে দেয়া। ছবির বিষয়বস্তু নির্বাচন করে সংসদ কর্মীদের কাছ থেকে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে চিত্রনাট্য নির্বাচন করেও ভালো ছবি নির্মাণের একটি প্রচেষ্টা চালানো যেতে পারতো। কিন্তু এ ধরনের কোনো গঠনমূলক পরিকল্পনার কথা ডিএফপির ন্যায় প্রতিষ্ঠান থেকে কখনো ভাবা হয়নি।”
(সম্মিলিত সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন \ মুহম্মদ খসরু \ ধ্রুপদী ৫ম সংকলন \ পৃষ্ঠা-২৮৮-২৯০)
মুহম্মদ খসরুর সদর্থ অভিজ্ঞতায়ই সম্ভব এদেশের সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনকে ব্যাখ্যা করা। আলোচ্য নিবন্ধে তিনি সে চেষ্টাই করেছেন।
মুহম্মদ খসরু সম্পাদিত ধ্রুপদী, চলচ্চিত্র পত্র আর ক্যামেরা যখন রাইফেল আমাকে সস্তাধারার চলচ্চিত্র সম্পর্কে বিতশ্রদ্ধ করে তুললেও সুস্থধারার ধ্রুপদ চলচ্চিত্র সম্পর্কে আগ্রহী করে তুলেছিল। বিশ্ব চলচ্চিত্রের মান আর বাংলাদেশের চলচ্চিত্রশিল্পের দীনতা সম্পর্কে মুহম্মদ খসরুর দিশাই আমাকে বাতিঘর হয়ে পথ দেখিয়েছিল। দীর্ঘদিন পর আজ যখন বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনের বাস্তবতা নিয়ে ভাবতে বসি, তখন সহজেই অনুধাবন করতে পারি ঢাকাই চলচ্চিত্র কী প্রক্রিয়ায় ধাপে ধাপে অধপাতে তলিয়ে গেছে, কীভাবে সাধারণ মানুষ চলচ্চিত্র থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। অকৃতদার মুহম্মদ খসরু যেন চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনকেই নিজের জীবনে সফরসঙ্গী হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন।
বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পের আজ যে মুমূর্ষু দশা তা থেকে পরিত্রাণ পেতে আজ যেন আবশ্যক হয়ে পড়েছে তাঁর মতো অগণন সংশপ্তক চলচ্চিত্রযোদ্ধার। মুহম্মদ খসরুর স্মৃতির প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধ।