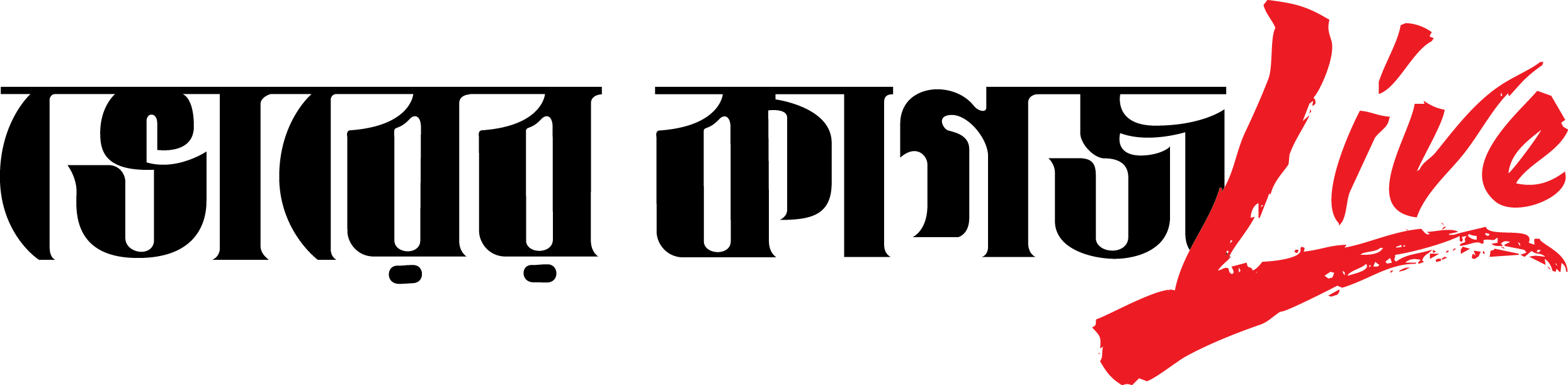সুবিনয় আসলে একটা ফানুসের নাম
কাগজ প্রতিবেদক
প্রকাশ: ২৩ অক্টোবর ২০২০, ০৭:৪৬ পিএম
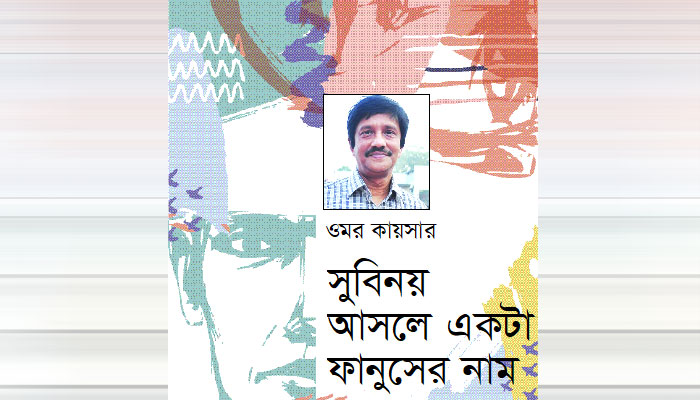
থার্মোফ্লাক্সে পানি গরম থেকে যায় কেন? নতুন বিজ্ঞান স্যার জিজ্ঞেস করেছিল সুবিনয়কে। সে দাঁড়িয়ে চুপচাপ স্যারের দিকে তাকিয়ে রইল। আগের দিন বাড়ি থেকে এটাই শিখে আসতে বলেছিলেন স্যার। খুব ভালো করে বুঝিয়েছিলেন। এখন সুবিনয় চুপ, কথা বলছে না। বাড়িতে পড়াটা শিখেছে কিনা জানতে চাইলেন স্যার। তারও কোনো জবাব নেই। গতকাল যে পড়া বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, সেটা বুঝেছিল কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। কিন্তু তার মুখে কোনো শব্দ নেই। তোমার নাম কী?
জানি কোনো উত্তর এবারও পাওয়া যাবে না। আমরা কয়েকজন তাই দাঁড়িয়ে বলে উঠলাম- স্যার ওর নাম সুবিনয় বড়ুয়া। ভেতরে ভেতরে খুব রেগে যাচ্ছিলেন স্যার। আমাদের কাছ থেকে উত্তর পেয়ে সেই রাগটা হুংকার হয়ে বেরিয়ে এলো- চুপ। আমি কি তোমাদের প্রশ্ন করেছি? চেয়ার থেকে উঠে এসে তিনি ব্যাকবেঞ্চার ছেলেটির কাছে গেলেন। আবার জানতে চাইলেন পড়া শিখেছে কিনা। কিন্তু স্যারের এত রাগ, হুংকার কোনো কাজে দিল না। ছেলেটা অবিচল, নিশ্চুপ। স্যারের চেহারা এবার কঠিন, কঠোর। আমরা সবাই ভয়ে কুঁকড়ে আছি। তিনি বাম হাতে সুবিনয়ের চুল মুঠো করে ধরলেন, তারপর হাতটা ওপরে তুলে বিশাল পাঞ্জাটা তার গালের ওপর সজোরে এবং ক্ষিপ্রগতিতে অবতরণে উদ্যত হলেন। আমি আর কোনো উপায় না দেখে চিৎকার করে বলে উঠলাম, স্যার ও কথা বলে না। চুপচাপ থাকে, ও খুব ভালো, পড়ালেখা প্রতিদিন শিখে আসে।
আমাদের এই নাটকীয় ভূমিকায় স্যারের আগুনজ্বলা চোখ ঠাণ্ডা হয়ে গেল। তিনি যে খুব অবাক হয়েছেন তা তার অবয়ব দেখেই বোঝা গেল। তার শক্ত হাত দুটি যেন কোমল হয়ে গেল। যে হাতে চুল টেনেছেন, সে হাতে আদর বুলিয়ে দিতে দিতে আমাদের বকতে লাগলেন- আমি এতক্ষণ ধরে চিৎকার করছি, অথচ কেউ আসল কথাটাই বলছ না। আমরা মাথা নিচু করে চুপ হয়ে থাকি। কথা না বাড়িয়ে স্যার ব্ল্যাকবোর্ডে গেলেন, লিখলেন- থার্মোফ্লাক্স কীভাবে বানানো হয় লেখ।
সেদিন ক্লাসে থার্মোফ্লাক্স সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো লিখেছিল সুবিনয়। তার হাতের লেখা দেখে স্যার মুগ্ধ হয়ে বললেন, টাইপ রাইটারের মতো গোল গোল অক্ষরে লেখাগুলো দেখেই তো পড়ার আগে নম্বর দিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে। সে তো শুধু উত্তর লেখেনি। থার্মোফ্লাক্সের একটা ছবিও এঁকেছে। বইয়ের ছবিটার চাইতে সুন্দর। যাকে কিছুক্ষণ আগে মারতে চেয়েছিলেন, তাকে ভালোবেসে ফেললেন নতুন বিজ্ঞান স্যার। তিনি বললেন, কথা কম, কাজ বেশি, ও তাই করল। তোমরা সবাই যদি ওর মতো হতে তবে তো আর কথাই ছিল না।
সবাই সুবিনয় হতে পারে না। হয়ও না। আমরা স্কুলের মাঠে খেলি, ক্লাসে হৈচৈ করি, মারামারি করি- এক সঙ্গে গান ধরি, স্যারদের নামে ছড়া কাটি। এইসব কৈশোরের হুল্লোড়ের ভেতর ছেলেটি ছিল না। সে চুপচাপ বসে থাকত। ছবি আঁকত, নয়তো বই পড়ত। তার হাতের লেখা আমাকে টানত। মাঝে মাঝে তার পাশে বসতাম। প্রথম প্রথম জানতে চাইতাম অনেক কথা। কিন্তু কথার জবাব ওর মুখ থেকে বের হতো না। ফুসফুসের বাতাসগুলো কথা হয়ে বেরিয়ে আসার সময় যেন মুখগহ্বরের কোথাও আটকে যেত। কিন্তু কোনোরকমে প্রথম কথাটা বের হয়ে এলে বাকিগুলোতে তেমন বেগ পেতে হতো না। তারপরও ওর কষ্ট দেখে আমি আর কথা বাড়াতাম না।
তো সেদিন ছুটির পর চট্টগ্রাম রেলস্টেশনের পদচারী সেতু পার হচ্ছিলাম। সেও যাচ্ছিল একই পথে। আমাকে দেখেই কাছে এলো। চোখে-মুখে কৃতজ্ঞতার ভাব। আমার কাঁধে হাত রেখে অনেক চেষ্টার পর বলল, স্যারের মারকে আমি ভয় পাই। তুমি আমাকে বাঁচিয়ে দিলে। পদচারী সেতু থেকে নেমে দুজন দুজনের কাঁধে হাত দিয়ে স্টেশন রোড ধরে হাঁটতে লাগলাম। হাঁটতে হাঁটতে আমরা দুজনেই নিউমার্কেটের সামনে দিয়ে চলে যাব। দুজনের গন্তব্য নন্দনকানন। আমার বাসা তুলসী ধামের সামনে, ওরটা বৌদ্ধ মন্দিরের পাশে। সেই স্কুল থেকে এখনো পর্যন্ত নানা কারণে সে আমার কাছে একটা বিস্ময়ের চিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পরিচয়ের প্রথম দিন থেকেই সে শুধু আমাকে অবাক করেছে। বুঝেছি, সে সাধারণ, স্বাভাবিক নয়, সে অন্যরকম।
একবার প্রবারণা পূর্ণিমার সন্ধ্যায় বাসার কাছে বৌদ্ধ মন্দিরে গিয়েছিলাম ফানুস ওড়ানো দেখতে। প্রবারণার রাতে আকাশের দিকে তাকালে মনে হয় অসংখ্য নবীন তারায় আকাশটা ছেয়ে গেছে। সেগুলো পৃথিবীতে থেকে মানুষের সুখ-দুঃখের বার্তা নিয়ে অনন্তের কাছে যায়। আমি ভিড়ের মধ্যে ফানুসে ওড়ানোর পদ্ধতিটা মনোযোগ দিয়ে দেখছিলাম। এ সময় আমার জামা ধরে কে যেন টান দিল। পেছনে তাকিয়ে দেখি সুবিনয়। সে আমাকে ভিড় থেকে টেনে ডিসি পাহাড়ের দিকে নিয়ে গেল। ওখানটায় মানুষজন কম। শিরিষ গাছের ফাঁক গলে একটা ফানুস ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছিল। সে আমাকে বলল, ফানুস মাটিতে আগুন, ওপরে আলো। আমি কথাটার মানে বুঝলাম না। সাহস হচ্ছে না কথাটার মানে কী জানতে। কথা বলতে তার কষ্ট হয়। আমি জানি। কথা যখন মুখের ভেতর ঘুরতে থাকে, তখন সেটি বের করে দেয়ার জন্য সে ছটফট করতে থাকে। আমি ডিসি পাহাড়ের আলো-অন্ধকারের ভেতর তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমাকে অবাক করে দিয়ে কোনো বাধা ছাড়াই সে বলল, ফানুস যখন মাটিতে থাকে তখন তার আগুন দেখা যায়। তাপ গায়ে লাগে। আর যখন ওপরে ওঠে তখন তারার মতো আলো ছড়ায়।
আমার জন্য আরো বিস্ময় অপেক্ষা করছিল সেদিন। ডিসি পাহাড়ের কিছু সময় কাটিয়ে আমাকে সে নিয়ে গেল তাদের বাসায়। ওর মা আমাকে দেখেই বলল, তোমার নাম ওমর? আমি চমকে গিয়ে বললাম, কী করে বুঝলেন? মা বললেন, ও তো তোমার কথা সবসময় বলে, সবার সঙ্গে তো সে মিশতে পারে না। কথা বলে না। সে কারণেই বুঝলাম। আর সে তো তোমার ছবিও এঁকেছে। পরে তার ড্রয়িং খাতায় দেখলাম অবিকল আমার মতো একটা ছেলে যেন সেখানে জলজ্যান্ত বসে আছে।
সেদিন একটা ব্যাপার খেয়াল করলাম ঘরের মানুষদের সঙ্গে কথা বলার সময় সে আটকে থাকে না। একেবারে স্বতঃস্ফ‚র্ত। আমি তার মাকে বললাম, আশ্চর্য, এখানে আপনাদের সঙ্গে ও তো বেশ সাবলীলভাবে কথা বলছে। মা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, এটাই তো সমস্যা। বাইরে গেলে তার মুখে কিসের যেন বাধা চলে আসে। অনেক ডাক্তার-কবিরাজ দেখালাম। কবজ দিয়েছি। কিছুতেই কিছু হয় না। তবে একটা কথা কি জানো, যাদের সে ভালোবাসে, যাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা, তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারে। তোমার সঙ্গে দেখবে আর কথা আটকাবে না।
সেটাই আমি খেয়াল করলাম। আমার সঙ্গে কথা বলার সময় সে ক্রমশ স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠছে। হয়তো এ কারণেই আমাদের দুজনের বন্ধুত্ব স্কুলের গণ্ডি ছাড়িয়ে বাসা পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। আমি তার কাছে জানতে চাইলাম, তুই আমার ছবি কীভাবে আঁকলি। আমার কোনো ফটো তো তোর কাছে নেই। সে বলল, তুই যেদিন স্যারের শাস্তি থেকে আমাকে বাঁচালি সেদিন আমি তোর ছবি তুলে রেখেছি। ‘ওই ব্যাটা, আমি কি তোর সঙ্গে স্টুডিওতে গিয়েছি নাকি?’
সত্তরের দশকে ক্যামেরা ছিল এক দুর্লভ বস্তু। ছবি তুলতে হলে মধ্যবিত্তদের স্টুডিওগুলোই ভরসা। তাও আবার সাদা কালো। সুবিনয় বলল, স্টুডিওতে যেতে হবে কেন? সম্রাট শাহজাহানের ছবি ইতিহাসের বইতে আছে না? প্ল্যাটো, সক্রেটিসের ছবি তুমি দেখনি। গৌতম বুদ্ধের ছবি? তার মূর্তি আমরা কীভাবে বানাই? তখনকার দিনে কি ক্যামেরা ছিল? সব তো আঁকা ছবি। আমিও মনে মনে ছবি তুলে সেটা খাতায় এঁকে ফেললাম। সে সময় তার অনেক কথা বুঝতাম না। এখন বহুদিন পর তার সেসব কথা চলচ্চিত্রের সেলুলয়েডের মতো স্মৃতির পর্দায় ভেসে উঠছে। আর তার কথার মর্মার্থগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তার সে সময়ের কথাগুলো না বুঝতে না পারলেও এক ঘোর তৈরি হতো আমার মধ্যে। সে নিজেও
ঘোরের মধ্যে থাকত। এই যে আমাদের চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল, সামনে বিশাল মাঠ, আইচ ফ্যাক্টরি রোড, রেল স্টেশনে শত শত মানুষের আনাগোনা, নন্দন কাননের বৌদ্ধ মন্দির সড়ক, ডিসি পাহাড়ের নিবিড় গাছপালা, টিয়ে পাখির ঝাঁক, ঘাসের ওপর শামুকের নির্বাক চলাফেরা, তুলসী ধামের ঘণ্টা এই জগতের বাইরে অন্য একটা জগতে সে চলে যেত। তখন সে আমার কাছে অচেনা একটা মানুষ। আর সেই অচেনা মানুষের কথাগুলো আমাকেও অন্যরকম করে তুলত।
বই পড়া তার নেশা। একটা এডিকশন। অনেক সময় সে এমন বই পড়ত যেগুলো বয়সের চেয়ে ভারী ছিল। সেই ভার আমার মতো সাধারণ ছেলের জন্য এক ধরনের বোঝাই হয়ে যায়। বইয়ের মধ্যে সে এমন বুঁদ হয়ে যেত যে বইয়ের চরিত্রগুলোকে সে বাস্তবের চরিত্রের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলত। আলেক্সান্দার বেলায়েভের উভচর মানুষের সেই চরিত্রটিকে মনে করত বাস্তবের কোথাও পাওয়া যাবে। বিশ্বাস করত এ রকম কোনো মানুষের সঙ্গে তার দেখা হবে। আর এ আশায় সে কাউকে না জানিয়ে পতেঙ্গার সমুদ্র সৈকতে গিয়ে বসে থাকত। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি সৈকতে সে এ রকম কাউকে খুঁজত। এদিকে তাকে খুঁজে খুঁজে পাগলপারা হয়ে যেত তার মা। অবশেষে দীর্ঘ অপেক্ষার পর ব্যর্থ হয়ে অনেক রাতে ক্লান্ত-অবসন্ন শরীরে প্রবল ক্ষুধা নিয়ে ঘরে ফিরেছে। এসব ব্যর্থতা তাকে বিষণ্ণ করে তুলত। হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান অ্যান্ডারসনের লিটল মারমেইড পরে মৎস্যকন্যাটির প্রেমে পড়ে গিয়েছিল। আমি একটা বই পড়লে তার উত্তেজনা যতক্ষণ পড়ি ততক্ষণ। কদিন পরেই রেশ কেটে যায়। কিন্তু তার ভেতরে রেশটা থেকে যায়। সে ভোলে না। সে তার খাতায় মৎস্যকন্যার অসংখ্য ছবি এঁকেছে। নদীর ধারে, সাগরের পাড়ে, কিংবা বাটালি পাহাড়ের চ‚ড়ায় গিয়ে সে একা একা বসে থাকত। বাস্তবতার জগৎ থেকে তার নিজস্ব জগতে ঢুকে পড়ার যে অভ্যাস, সেটা ক্রমশ বাড়তে থাকে। তার মানে নিজের অন্তর্গত জগৎকে সে বেশি করে সময় দিতে শুরু করল। চারপাশের সবকিছুকে ফেলে সে অলৌকিক যানবাহনে চড়ে সেখানে চলে যায়। প্রায় সময় বিড় বিড় করে। আমাকে সে বলত মহাজগতের কথা।আমাদের সৌরজগৎ যে মহাকাশের অসীম শূন্যে একটা ছোট এক বিন্দুর মতোই ক্ষুদ্র সে আমাকে বোঝাত। সে বলত, আরো অনেক অনেক সূর্য আছে। আছে আরো অনেক পৃথিবী। সেখানে আছে মানুষের চেয়েই বেশি বুদ্ধিমান প্রাণী। এতটুকু পর্যন্ত ঠিক বলে মানা যায়। কিন্তু এরপরে সে যা বলত তাতে ভয়ে হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। সে বলত সেই বুদ্ধিমান প্রাণীদের সঙ্গে তার সংযোগ আছে। তাদের সঙ্গে ভাববিনিময় হয়। তারা তাকে তাদের সেই জগতে নিয়ে যেতে চায়। আমার রোমক‚পগুলো তখন শিরশির করত। ভয়ে ভয়ে বলতাম- তো, তুই যাবি সেখানে? সে বলে- যেতে তো চাই, কিন্তু সেখানে গেলে তো আর পৃথিবীতে ফেরা সম্ভব নয়। এখানে মানুষের বেঁচে থাকার পদ্ধতি একরকম, আমরা এখানে অক্সিজেন পাই। কিন্তু সেখানে অক্সিজেন নয়, অন্য কোনো গ্যাস নিতে হয়। আমি যদি যাই আমার শরীরের গঠন পাল্টাতে হবে। যা আর বদলানো যাবে না। তারপরও আমি যেতে চাই। কিন্তু আমার মা তো পাগল হয়ে যাবে আমাকে না পেলে। মায়ের কথা ভেবে আমি প্রতিদিন ঘরে ফিরে আসি।
এ কথা শুনে আমার ভেতরে আশা জাগে। অন্তত সে মায়ের টানে পৃথিবী থেকে নিরুদ্দেশ হবে না। মায়ের কারণে পৃথিবীর বাইরে নীহারিকার সীমাহীন শূন্যতার ভেতর লুকিয়ে থাকা প্রাণময় কোনো গ্রহে সুবিনয় যায়নি ঠিক, কিন্তু এই পৃথিবীতেও তেমন থাকল কই? তার শরীর আছে ঠিকই, কিন্তু সে তো সুদূরের পিয়াসী। সে তো চঞ্চল। সে যেন বোদলেয়ারের সেই কবিতার মতোই অবিরাম উচ্চারণ করে যায়- আমি ভালোবাসি মেঘ, ওই দূরে ওই দূরে আশ্চর্য মেঘদল।
আমরা যারা বাস্তবের মাটিতে একের পর এক সিঁড়ি ডিঙিয়ে, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় পেরিয়ে চাকরি করছি, প্রতিষ্ঠার পেছনে দৌড়াচ্ছি, সভায়-সমাবেশে বক্তৃতা দিয়ে হাততালি পাচ্ছি, সংসারে গার্হস্থ্য জীবনে সুখ, আনন্দ, আরাম উপভোগ করছি, বাবা, মা, সন্তানের হাসি দেখে পুলকিত হচ্ছি। সে এসবের কিছুই তোয়াক্কা করেনি। সার্টিফিকেটের ধার ধারেনি। পুঁজিকে সে পুঁজের মতো পরিত্যাগ করেছে। প্রতিষ্ঠাকে দূরে ঠেলে দিয়ে একটা ফানুসে পরিণত হয়েছে, আর নিজের ভেতরে আগুন জ্বালিয়ে অনেক অনেক ওপরে উঠে অনন্ত নক্ষত্র বিথীর সঙ্গে অবিরাম সংযোগ রক্ষা করে আলোর কথোপকথনে ব্যস্ত।