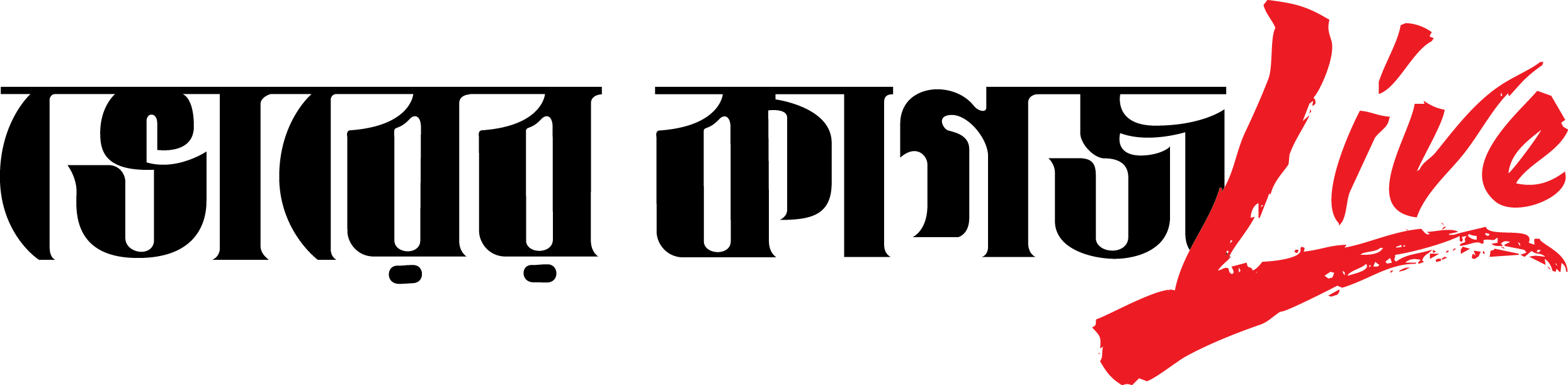শেখ মুজিব থেকে বঙ্গবন্ধু
কাগজ প্রতিবেদক
প্রকাশ: ১০ ডিসেম্বর ২০১৯, ০৭:০৬ পিএম

পঞ্চান্ন বছরের যাপিত জীবন ছিল বঙ্গবন্ধুর, যা সময়ের বিচারে সংক্ষিপ্তই বলা যায়। কিন্তু জীবনের দৈর্ঘ্যরে চেয়ে তার কর্মের প্রস্থ ছিল অনেক বেশি- ইংরেজিতে যা বলা হয়, Larger than life অর্থাৎ জীবনের চেয়ে বড়। বঙ্গবন্ধুর কর্মের পরিধি-প্রস্থ কত বড় ছিল তার প্রমাণ বহন করে লেখাটির উপশিরোনাম। অবশ্য উপশিরোনামের শেষোক্ত অভিধাটি পরে ব্যাখ্যা করা হবে। জীবনের দৈর্ঘ্য দৈবনির্দেশিত; কিন্তু জীবনে একজন মানুষের কর্মের ব্যাপ্তি ও গভীরতা জীবনধারী মানুষের মেধা-মনন, প্রণোদনা ও উদ্যোগ-উদ্যমের ওপর নির্ভরশীল। এমন মানুষই ছিলেন বঙ্গবন্ধু। কাজেই দৈর্ঘ্য দিয়ে নয়, তার জীবনকে মাপতে হবে তার কর্মের পরিধি ও গভীরতা দিয়ে। সন্দেহ নেই, কেন তিনি বিবিসি জরিপে কুড়িজন শ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকায় শ্রেষ্ঠতম হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। উল্লেখ্য, উনিশ জন বাঙালিই কর্মগুণে খ্যাত ছিলেন। তবে মনে হয়, বঙ্গবন্ধুর শ্রেষ্ঠতম হওয়ার কারণ ছিল এই যে, তিনি বাঙালির স্বাধীনতা ও রাষ্ট্র নির্মাণের কারিগর ছিলেন। উল্লেখ্য, স্বাধীনতা ও রাষ্ট্র বাঙালির শ্রেষ্ঠ অর্জন। এমন মানুষ যে তার যাপিত জীবনের চেয়ে বড় হবেন, তা স্বীকার্য।
বঙ্গবন্ধুর কর্মভিত্তিক পরিচয় তো তার একাধিক অভিধায় বিধৃত এবং যা বিশ্বের অন্য কোনো নেতার ভাগ্যে জোটেনি। তিনি প্রথমত ছিলেন জননন্দিত ও জনগণলগ্ন নেতা। ‘আমার যোগ্যতা মানুষকে ভালোবাসি; আমার অযোগ্যতা আমি তাদেরকে বেশি ভালোবাসি’- এ কথা তো তিনি নিজেই বলেছিলেন ডেভিড ফ্রস্টকে। জনগণের আকাক্সক্ষা-অভীপ্সা ও স্বপ্নকে আত্মস্থ করে তিনি বিকশিত হয়েছিলেন জনগণের নেতা হিসেবে। তাই বলে তিনি লোকানূবর্তী বা লোকরঞ্জক নেতা ছিলেন না; ছিলেন স্বীয়তাসম্পন্ন গণমানুষের নেতা। এটা ঠিক যে, তিনি জনগণের স্বপ্নকে ধারণ করে তা রূপায়নের কারিগর ছিলেন। এ কারণে ১৯৬৬ সালে সিরাজুল আলম খানের মন্তব্য ছিল- শেখ মুজিবের নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন করতে হবে। কারণ লোকে তার কথা শোনে। জানা কথা, দেশ স্বাধীন হয়েছিল তার নেতৃত্বেই।
১৯৬৯-এর ২৩ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে সদ্য অব্যাহতিপ্রাপ্ত শেখ মুজিব হলেন বঙ্গবন্ধু। সেই থেকে তিনি বঙ্গবন্ধু। এই বঙ্গবন্ধু অভিধার একটু ইতিহাস আছে, যা জেনে নেয়া উচিত। ১৯৬৮-এর শেষ দিকে ঢাকা কলেজের ছাত্রলীগ নেতা রেজাউল হক চৌধুরী মোশতাক অভিধাটি চয়ন করেন। আর ডিসেম্বরে ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ঢাকা কলেজ ছাত্রলীগ অভিধাটি ব্যবহার করে স্লোগান দেয়। তবে স্বীকার্য, সেদিন রেসকোর্সের বিশাল নাগরিক সংবর্ধনায় ডাকসু ভিপি তোফায়েল আহমেদের প্রস্তাবনায় ও জনগণের তাৎক্ষণিক সম্মতিতে অভিধাটি জনসমক্ষে এসেছিল।
বঙ্গবন্ধু জাতির জনক ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি। এমন সব অভিধাও তার প্রাপ্য এবং তা তার কর্মগুণেই। বাঙালির অগ্রজ নেতা ছিলেন শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, মওলানা ভাসানী এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, যাদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর ছিল অপরিমেয় শ্রদ্ধা। এরা সবাই বাঙালির স্বাধিকার নিয়ে সোচ্চার ছিলেন। শেরে বাংলা তো ১৯৫৩ সালেই বলেছিলেন, ‘Leave east pakistan to work out its own destiny।’ কিন্তু তাদের অনুজ বঙ্গবন্ধু যেভাবে জনতার নাড়ির স্পন্দন বুঝতেন সেভাবে তাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব হয়নি কখনো। উপরন্তু বঙ্গবন্ধুর ছিল লক্ষ্য অর্জনে ও ত্যাগ স্বীকারে দৃঢ়তা। ফিদেল ক্যাস্ত্রো ঠিকই চিনেছিলেন শেখ মুজিবকে; তাই তার স্পষ্ট উচ্চারণ- ‘আমি হিমালয় দেখিনি, শেখ মুজিবকে দেখেছি। সাহস ও ব্যক্তিত্বে মানুষটি হিমাদ্রি সদৃশ।’ সুতরাং হিমালয়ের মতো মাথা উঁচু করেই তিনি জাতির জনক ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি।
বঙ্গবন্ধুর আয়ুষ্কাল ছিল সাড়ে পাঁচ দশক, আর যার ৩ হাজার ৫৩ দিন কেটেছিল কারার লৌহকপাটের অন্তরালে। বন্দি বঙ্গবন্ধু মানসিকভাবে ছিলেন মুক্ত বিহঙ্গ। সে কারণে বন্দিত্বের অন্তরালে রচিত হয়েছিল দুটি অমূল্য জাতীয় সম্পদ- অসমাপ্ত আত্মজীবনী ও কারাগারের রোজনামচা। দুটি বই যে হাতে পেয়েছি তার কৃতিত্ব দুজন নারীর। প্রথমজন বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব, যিনি লেখার খাতা দিয়ে স্বামীকে উৎসাহিত করেছিলেন লিখতে এবং ১৯৭১-এ অবরুদ্ধ থাকার সময়ে ৩২ নম্বরের বাড়ি থেকে শেখ হাসিনাকে দিয়ে পান্ডুলিপি আনিয়ে সযত্নে আগলে রেখেছিলেন। ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট পান্ডুলিপি দুটি উধাও হয়। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী অনেক খুঁজে পেতে প্রকাশের ব্যবস্থা করেন বলেই বই দুটি আমরা হাতে পাই। অবশ্য কারাগারের রোজনামচা নামকরণ করেছেন শেখ রেহানা।
সৃজনশীল-মননশীল রাজনীতিকের কারাবাসের নিরবচ্ছিন্ন অবকাশ অনেক নন্দিত সাহিত্য-কর্মের প্রণোদনা হিসেবে কাজ করেছে। যেমন অনেক দৃষ্টান্তের মধ্যে দুজন হলেন গ্রামচি এবং নেহরু। প্রথম জনের Prison Notebooks এবং দ্বিতীয় জনের Glimpses of World History সারা বিশ্বে নন্দিত। আর বঙ্গবন্ধুর রচনা দুটি লেখনী-নৈপুণ্যে পাঠকনন্দিত। অসমাপ্ত আত্মজীবনী ইংরেজি ছাড়া আরবি ও জাপানি ভাষায় অনূদিত হয়ে বিশ্বের নানা দেশের পাঠকের হাতে পৌঁছেছে। অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর পাঠক শুধু বাঙালিই নয়, অন্য দেশের মানুষও। মনে হয়, সময় ও সুযোগ পেলে বঙ্গবন্ধু তার রচনা সম্ভারে জাতির মননের ঐতিহ্যকে অনেক সমৃদ্ধ করতে পারতেন।
১৯৪৭-১৯৭১ : বাঙালির স্বাধীনতা-স্বপ্ন নির্মাণের কারিগর পাকিস্তানের মোহমুক্ত এবং বাঙালির স্বাধীনতার উদগ্র বাসনায় প্রণোদিত তরুণ মুজিবের ঢাকার জীবন শুরু হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের ছাত্র হিসেবে। কিন্তু ছাত্রত্ব বিঘ্নিত হলো চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী আন্দোলনে সম্পৃক্ততার কারণে। হলেন বহিষ্কৃত ও কারারুদ্ধ। অবশ্য গোপালগঞ্জেই কিশোর মুজিব কদিনের জন্য জেল খেটেছিলেন। যা হোক, কিছু সতীর্থ মুচলেকা দিয়ে ছাত্রত্বে ফিরে গেলেও মুজিব এমন কোনো মুচলেকা দিলেন না, কাজেই তার ছাত্রত্বও ফিরল না।
১৯৪৮-এর ৪ জানুয়ারি ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হলো পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ, যা ছিল তরুণ প্রজন্ম বাঙালির প্রথম রাজনৈতিক মঞ্চ। প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে দিকনির্দেশনামূলক সম্পৃক্ততা ছিল তরুণ শেখ মুজিবের। কারণ তিনি বুঝেছিলেন এমনি একটি প্রতিষ্ঠান দিয়েই তার যাত্রা শুরু হবে স্বাধীনতা অর্জনের বন্ধুর পথে। ১৯৪৯-এর ২৩ জুন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের যাত্রা শুরু হয়। ভাষা আন্দোলনে সম্পৃক্ততার কারণে কারাবন্দি শেখ মুজিব সভাপতি মওলানা ভাসানীর পছন্দ অনুযায়ী উপস্থিত খন্দকার মোশতাকের প্রকাশ্য বিরোধিতা সত্তে¡ও যুগ্ম সম্পাদক হলেন। শুরু হলো এই তরুণের প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতির নতুন অধ্যায়। তখন বোধহয় কেউ অনুধাবন করেনি এই প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতি হবে বাংলাদেশে সৃষ্টির অনুঘটক, আর এই তরুণ প্রধান কুশীলব। বলা যায়, এই বিশেষ সময়টি যেন ছিল ইতিহাসের এক মাহেন্দ্রক্ষণ। আরো উল্লেখ্য, সেই থেকে শুরু মোশতাকের প্রচ্ছন্ন মুজিব-বৈরিতা। প্রকাশ্যে অবশ্য তাকে সব সময়ে বঙ্গবন্ধুলগ্নই দেখা গেছে। কিন্তু মোশতাকের বঙ্গবন্ধু-বৈরিতার চরম বহিঃপ্রকাশ হয়েছিল ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট। অবশ্য ১৯৬৬ সালেই কমরেড মণি সিংহ এই বলে সতর্ক করেছিলেন যে, মোশতাক এমন এক সাপ যে পায়ে নয়, মাথায় ছোবল দেবে। দিয়েছিলও তাই। ১৯৭৪-এর অক্টোবরে তাজউদ্দীনকে মন্ত্রিসভা থেকে সরিয়ে দিলে সাংবাদিক কামাল লোহানী বঙ্গবন্ধুকে প্রশ্ন করেছিলেন, তাজউদ্দীনকে সরিয়ে দিলেও কুচক্রী মোশতাককে কেন রাখা হলো। বঙ্গবন্ধুর উত্তর ছিল, ‘মোশতাক একটা শয়তান, ওটাকে কাছে রাখতে হয়।’ তিনি অবশ্য তাজউদ্দীন সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করেননি। মনে হয় বঙ্গবন্ধু ও তাজউদ্দীন নৈকট্যে থাকলে ১৫ আগস্ট হতো না। যা হোক, মূল কথায় ফিরে গিয়ে বলতে হয় যে, ১৯৫৫-এর ২১ অক্টোবর প্রতিষ্ঠানটি তার নাম থেকে ‘মুসলিম’ শব্দটি ছেঁটে দিয়ে অসাম্প্রদায়িক ও সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে ওঠে। অবশ্য ১৯৫৩ সালে ছাত্রলীগ এই কাজটি করেছিল। কারামুক্ত শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে আবিভর্‚ত হলেন। একই সঙ্গে একা একাই ‘পূর্ববাংলা মুক্তিফ্রন্ট’ নামে প্রচারপত্র নিজে ছেপে সাইকেলে চড়ে ঢাকা শহরময় বিলি করতে শুরু করলেন। স্বাধীনতা-পাগল মানুষটির কর্মপদ্ধতিই ছিল বিচিত্র, কিন্তু লক্ষ্যাভিসারী।
শেখ মুজিব ১৯৫৩ সালে সাধারণ সম্পাদক হলেন। ১৯৫৪-এর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে বাঙালি মোর্চা যুক্তফ্রন্টের ভ‚মিধস বিজয়ের সিংহভাগের অংশীদার হলো আওয়ামী লীগ, অংশীদার হলেন বিজয়ী শেখ মুবিজও, মন্ত্রিত্বও পেলেন। এই নির্বাচনের প্রচারে নেমে সহায়-সম্বলহীন একজন বৃদ্ধার কাছে শুভকামনা পেয়েছিলেন এমন ভাষায়- ‘গরিবের দোয়া তোমার জন্য সব সময় আছে।’ কারাগারের রোজনামচায় আছে একজন দরিদ্র সহকারাবন্দির মুখে অভিন্ন দোয়ার কথা। জানা কথা, পাকিস্তানি চক্রান্তের কারণে যুক্তফ্রন্ট সরকার স্বল্পায়ু হয়েছিল। কিন্তু সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবের পথ রুদ্ধ হয়নি। অনতিক্রম্য সাংগঠনিক দক্ষতা ও বাগ্নিতায় তিনি আওয়ামী লীগকে তৃণমূল পর্যন্ত বিস্তৃত করলেন। ১৯৫৭ সালে একবার মন্ত্রী হয়ে তা ছেড়ে দলের কাজে মনোনিবেশ করলেন। কারণ তিনি বুঝতেন দল আর সরকার আলাদা থাকা উচিত এবং সরকারের চেয়ে দল বড়। স্বাধীন বাংলাদেশেও তিনি দল ও সরকার আলাদা করেছিলেন। দল ও সরকার একাকার হওয়া গণতন্ত্রের জন্য বিপজ্জনক।
১৯৬৩ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী লোকান্তরিত হওয়ার পর আওয়ামী লীগ বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছিল। কিন্তু শেখ মুজিবের কর্মক্ষমতায় তা উতরে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল। অবশ্য ১৯৫৭-এর ফেব্রুয়ারিতে ভাসানী আওয়ামী লীগ ত্যাগ করে ন্যাপ গঠন করায় দলটি বেশ বেকায়দায় পড়েছিল। তখনো পরিস্থিতি সামাল দিয়েছিলেন সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিব। ষাটের দশকের শুরুতে এই ব্যক্তির জীবনের দুটি গোপন ঘটনা তার স্বাধীনতাপ্রিয়তার ইঙ্গিতবহ। ১৯৬১ সালে ইত্তেফাক সম্পাদক মানিক মিয়ার মধ্যস্থতায় শেখ মুজিব কমরেড মণি সিংহ ও কমরেড খোকা রায়ের সঙ্গে গোপন বৈঠক করেন। মুখ্য আলোচক তিনিই; আর মূল বিষয় স্বাধীনতা। কমরেড দুজন স্বাধীনতার প্রশ্নে একমত হলেও বললেন, এমন দাবি তোলার পরিবেশ তখন নেই। শেখ মুজিবের সোজাসাপটা কথা ছিল, ‘আপনাদের পরামর্শ মানলাম, কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা চাই।’ দ্বিতীয় ঘটনাটি ১৯৬৩-এর। আওয়ামী লীগের কাউকে না জানিয়ে একা কৌশলে সীমান্ত অতিক্রম করে আগরতলা যান। আতিথ্য গ্রহণ করেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহের। তার মাধ্যমে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহরুর সঙ্গে যোগাযোগ করলেন, চাইলেন একটি ট্রান্সমিটার, যাতে বাঙালির একটি গোপন বেতার কেন্দ্র হয়। কিন্তু চীন-ভারত যুদ্ধে ভারতের বিপর্যয়-পরবর্তী পরিস্থিতিতে নেহরু ইতিবাচক সাড়া দিলে না। সুতরাং শেখ মুজিবকে অনেক কষ্ট করে খালি হাতে ফিরতে হয়।
তবে ষাট দশকে শেখ মুজিবের জীবনে বড় ঘটনাটি ছিল ছয় দফা। ছয় দফার তাৎক্ষণিক পটভূমিতে ছিল ১৯৬৫ সালে ১৭ দিনের পাক-ভারত যুদ্ধ। এই যুদ্ধের সময়ে পূর্ব পাকিস্তান ছিল অরক্ষিত। সুতরাং বাঙালি রাজনীতিবিদরা ছিলেন ক্ষুব্ধ আর সেই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হলো মুজিবের বলিষ্ঠ উচ্চারণে- ‘পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন করে ভাবতে হবে।’ এই নতুন ভাবনার বহিঃপ্রকাশ হলো ছয় দফার মাধ্যমে, যা ১৯৬৬-এর ৫ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হয় এবং জুন মাসে প্রচারিত হয়। ‘আমাদের বাঁচার দাবী’ শিরোনামের এই ছয় দফা বাঙালির ‘ম্যাগনা কার্টা’ হিসেবে নন্দিত হয়েছিল। কিন্তু বাঙালি কেন, কোনো সমাজেই দুর্মুখের অভাব হয় না; তবে বাঙালি সমাজে বোধহয় বেশি। কুৎসার মতো তথাকথিত বাম ঘরানার পক্ষ থেকে, বিশেষ করে, মওলানা ভাসানীর পক্ষ থেকে বলা হলো, এটা সিআইএর দলিল। কেউ কেউ আবার বললেন, এটা আইয়ুবের সহযোগী আলতাফ গত্তহরের মুসাবিদা করা একটি দুরভিসন্ধিমূলক নীল নকশা। আপাতদৃষ্টিতে ছয় দফা ছিল ১৯৪০-এর লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী পাকিস্তান রাষ্ট্রকাঠামোর গণতন্ত্রায়নের পরিকল্পনা। তবে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ছিল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক স্বায়ত্তশাসনের কথা। পাকিস্তানি প্রেক্ষাপটে ছয় দফা ছিল বিচ্ছিন্নতার দলিল এবং যার ফলে শেখ মুজিবসহ ৩৫ জন বাঙালি সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তি অভিযুক্ত হয়ে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি হলেন। আগরতলা মামলা মিথ্যা ছিল না; যেভাবে সাজানো হয়েছিল তা ষড়যন্ত্রমূলক। এই মামলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে আন্দোলনমুখর হয়েছিল বাঙালি তরুণ প্রজন্ম; কারণ নিষেধাজ্ঞার ফলে রাজনৈতিক দলগুলো ছিল অন্তরালবর্তী। তরুণ প্রজন্মের কণ্ঠে সোচ্চার স্লোগান ছিল- ‘জেলের তালা ভাঙবো, শেখ মুজিবকে আনবো।’ জেলের তালা ভেঙেছিল, শেখ মুজিবও মুক্ত হয়েছিলেন; তবে তা ক’দিন পর।
১৯৬৮-এর ছাত্র আন্দোলনের ফসল ১৯৬৯-এর ৪ জানুয়ারির এগারো দফা, যা স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের আকাক্সক্ষায় ছয় দফার সম্পূরক ছিল। শহীদ আসাদের মৃত্যু (২০ জানুয়ারি) ২৪ জানুয়ারিতে সূচিত গণঅভ্যুত্থানের অনুঘটক ছিল। তারুণ্যের এই অভ্যুত্থান বাঙালির রাজনৈতিক বিবর্তন-ক্রমধারায় একটি বাঁকবদল ঘটিয়েছিল। কারণ ১৯৬৮ পর্যন্ত প্রকাশ্য রাজনীতির কৌশলমূলক প্রবণতা ছিল বাঙালির স্বায়ত্তশাসন; কিন্তু ফল্গুধারা ছিল স্বাধীনতার। ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে তারুণ্যের দীপ্ত কণ্ঠে শ্রুত স্লোগানগুলো ছিল- ‘বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন করো’; ‘তুমি কে, আমি কে? বাঙালি, বাঙালি’; ‘তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা, মেঘনা, যমুনা’; ‘ঢাকা না পিন্ডি, ঢাকা, ঢাকা।’ অর্থাৎ বাঙালির ভাষিক, নৃতাত্তি¡ক এবং ভৌগোলিক স্বাধীনতার বার্তা পাওয়া গিয়েছিল এই মন্দ্রিত স্লোগানগুলো থেকে। গণঅভ্যুত্থান বা গণশক্তির প্রভাবে আগরতলা মামলার আকস্মিক সমাপ্তি ঘটল; ২২ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিব মুক্ত হলেন। ২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্সের লাখো জনতা ডাকসু ভিপি তোফায়েল আহমেদের প্রস্তাবনায় সাড়া দিয়ে শেখ মুজিবকে বঙ্গবন্ধু অভিধায় ভ‚ষিত করল। সেই থেকে শেখ মুজিব বঙ্গবন্ধু; বিশ্ববন্ধু অভিধা তার অচিরেই প্রাপ্য। তার কণ্ঠ বজ্রকণ্ঠ হতো শুধু বাঙালির জন্য নয়, বিশ্বের তাবৎ শোষিত মানুষের জন্য।
১৯৭০-এর নির্বাচনপূর্ব পরিস্থিতি নির্বাচনবান্ধব ছিল না। দুটি কারণ ছিল। এক. ১৯৭০-এর নভেম্বরে আমাদের উপক‚ল অঞ্চলে স্মরণকালের ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ে হতাহত ও ক্ষয়ক্ষতির প্রতি পাকিস্তান সরকারের উদাসীনতা। ভাসানী তো স্লোগান তুললেন, ‘ভোটের আগে ভাত চাই।’ তিনি ও তার দল নির্বাচন বর্জন করল। দুই. আইয়ুবের উত্তরসূরি সামরিক স্বৈরশাসক ইয়াহিয়ার আইনি কাঠামো আদেশ (খবমধষ ঋৎধসবড়িৎশ ঙৎফবৎ); যার ২৫ ও ২৭ ধারা অনুযায়ী নির্ধারিত ছিল যে, পাকিস্তানের সংহতি বিনষ্টির কোনো উদ্যোগ ভবিষ্যতের সংবিধানে থাকবে না। বঙ্গবন্ধু নির্বাচনে অংশগ্রহণের পক্ষে ছিলেন; তবে তার প্রস্তাব ছিল উপদ্রুত এলাকায় পরে নির্বাচন হবে, হয়েছিলও তাই। তবে আইনি কাঠামো আদেশ নিয়ে আওয়ামী লীগের ভেতর সংশয় ছিল, কারণ দলটির লক্ষ্য ছিল ছয় দফা অনুযায়ী ভবিষ্যতের সংবিধান রচনা করা। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর প্রতিজ্ঞ ও প্রত্যয়ী উচ্চারণ ছিল, ‘নির্বাচনের পর আমি, এলএফও টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবো। আমার লক্ষ্য বাংলাদেশের স্বাধীনতা।’ বঙ্গবন্ধুর সিদ্ধান্ত যে দূরদর্শী ও বিচক্ষণ ছিল তা পরবর্তী সময়ের ইতিহাস প্রমাণ করেছে। রাজনীতিবিদ তখনই রাষ্ট্রনায়ক হন যখন তার দূরদৃষ্টি প্রমাণিত হয়।
নির্বাচনের ফল অনুযায়ী যা হওয়ার কথা তা হলো না; আওয়ামী লীগ কেন্দ্রে সরকার গঠন করতে পারল না। ১৯৭১-এর ৩ মার্চ অনুষ্ঠেয় ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির ঢাকা অধিবেশন স্থগিত হলো ১ মার্চ। সংক্ষুব্ধ ও উত্তাল বাঙালির করণীয় কী তার নির্দেশ এলো বঙ্গবন্ধুর রেসকোর্সের ৭ মার্চ ভাষণে। ১৮ মিনিট ৩১ সেকেন্ডের ১ হাজার ১০৮ শব্দের এই ভাষণের দুটি অংশ ছিল। এক. সংকট সমাধানের ৪টি শর্ত দেয়া হলো- ক. সামরিক শাসন প্রত্যাহার; খ. সেনাবাহিনী ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়া; গ. বাঙালি হত্যার বিচার বিভাগীয় তদন্ত এবং ঘ. নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা অর্পণ করা। বঙ্গবন্ধু জানতেন কোনো শর্তই মানা হবে না। কিন্তু নির্বাচিত গরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে এটা ছিল বিশ্ববাসীর জন্য তার বার্তা। দুই. এমন প্রেক্ষাপটে বাঙালির ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হলো, এমন একটি বিমন্দ্রিত উচ্চারণে, ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।’ আরো প্রত্যয় ব্যক্ত হলো, ‘বাংলার মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো, ইনশাল্লাহ’ অথবা ‘আর দাবায়ে রাখতে পারবা না।’ না এমন বাক্যগুলো লক্ষ্যাভিসারী হলেও তা সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণা নয় বা তা সম্ভব ও বাস্তব ছিল না। তবে স্বাধীনতা শব্দটি তো সেই থেকে আমাদের হলো। বঙ্গবন্ধুর জীবনের সংক্ষিপ্ততম, কিন্তু শ্রেষ্ঠতম এই ভাষণে বাঙালির ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়ে গেল। জননন্দিত কুশলী রাজনীতিবিদ আবার রাষ্ট্রনায়কোচিত বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার স্বাক্ষর রাখলেন।
১৬ থেকে ২৪ মার্চ ইয়াহিয়ার সঙ্গে আলোচনায় বসা বঙ্গবন্ধুর জন্য বেমানান লাগে, বিশেষ করে ৭ মার্চের ভাষণের পর। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এটাও ছিল তার কৌশল এবং বার্তা। তবে তথ্য-প্রমাণ বলে, আসন্ন সংগ্রাম সম্পর্কে তার প্রস্তুতি ছিল। মার্চ মাসের মাঝামাঝি ছাত্রনেতা ‘চার খলিফা’কে (আ স ম আবদুর রব, আবদুল কুদ্দুস মাখন, নূরে আলম সিদ্দকী এবং শাহজাহান সিরাজ) কাগজে না লিখে কলকাতার একটি ঠিকানা মুখস্থ করিয়েছিলেন; ঠিকানাটি ছিল-চন্দ্রশীল, ৪৯, গার্ডেন রোড, ভবানীপুর পার্ক। উপরন্তু কলকাতায় অবস্থান করা সাংসদ চিত্তরঞ্জন সুতারের কথা জানিয়েছিলেন আওয়ামী লীগের নেতাদের।
২৫ মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধু কেন বাড়ি ছাড়েননি তার ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছিলেন ১৯৭২-এর ১৮ জানুয়ারি ডেভিড ফ্রস্টকে। ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে গ্রেপ্তার হওয়ার আগে রেকর্ড করা বার্তায় বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা ছিল- ‘সম্ভবত এটাই আমার শেষ বার্তা, আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন।’ ততক্ষণে শুরু হয়েছিল বাঙালি নিধনের ‘অপারেশন সার্চলাইট’। সুতরাং আক্রান্ত হয়ে প্রত্যক্ষ স্বাধীনতার ডাক দিলেন বঙ্গবন্ধু। ৭ মার্চ স্বাধীনতার ডাক দিলে সেদিন রেসকোর্সে অঙ্কুরেই সব বিনষ্ট হতো আর বিশ্ববাসীর চোখে তিনি বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রতিপন্ন হতেন। কিন্তু ২৬ মার্চের ঘোষণায় বিশ্বের নৈতিক সমর্থন বাঙালির জন্য অবধারিত হয়েছিল। রাষ্ট্রনায়কের দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতা আবারো প্রমাণিত হলো। ৬ মার্চ ‘চার খলিফা’ স্বাধীনতার জোরালো দাবি তুললে প্রচন্ড আত্মপ্রত্যয়ী বঙ্গবন্ধুর বক্তব্য ছিল, ‘দেখ তোরা বেশি চাপাচাপি করবি না। শেখ মুজিব জানে কখন কী বলতে হবে, কী করতে হবে!’ বলা ও করার বিবেচনায় তিনি ছিলেন বাঙালির অনতিক্রম্য নেতা। তার বলা আর করার মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতি ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত সময়ে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল।
মুক্তিযুদ্ধের ৮ মাস ২১ দিন শারীরিকভাবে অনুপস্থিত থেকেও বঙ্গবন্ধুই ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের নেতা। এটা তো ছিল তার নেতৃত্বের অগ্নিপরীক্ষা, যা তিনি উতরে গিয়েছিলেন সফলভাবে। তিনি ছিলেন বাংলাদেশের প্রথম সরকারের রাষ্ট্রপতি। অবশ্য তার অনুপস্থিতিতে যুদ্ধের প্রত্যক্ষ পরিচালনে ছিলেন তার ছত্রছায়ায় গড়ে ওঠা চার জাতীয় নেতা- তাজউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ও কামারুজ্জামান। সাফল্য তাদেরও। কারণ মুক্তিযুদ্ধ ছিল সব দিক দিয়ে সফল।
ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন : বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (বিইউপি)।