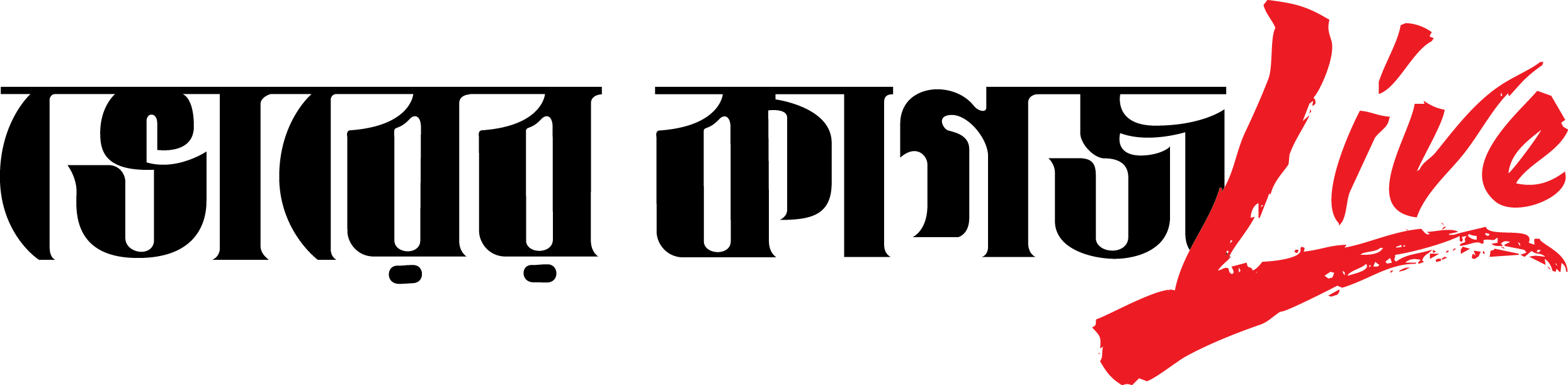অন্য সংশপ্তক
কাগজ প্রতিবেদক
প্রকাশ: ০৩ জুন ২০১৯, ০৮:১৮ পিএম

শহর-নগর জায়গাগুলোই এই রকম, দিনে দিনে এ পাশ ও পাশ ভাঙে গড়ে, বদলায়, শুধু বদলায়। আড়ে-দিঘের আয়তনে শুধু নয়, বদলায় তার চেহারা চরিত্র সব কিছু। বাংলাদেশের ছোট্ট এক জেলা শহর কুষ্টিয়া গায়ে-গতরে বাড়তে বাড়তে বর্তমানে তার চেহারার ভোল পাল্টে ফেলেছে অনেকখানি। বেড়েছে তার রূপের বাহার, চটকদার আলোর জেলা।
এই কুষ্টিয়া শহরকে একপাশে ফেলে রেখে প্রশস্ত ঢাকা-রোড চলে গেছে পূর্ব দিকে। যেতে যেতে গড়াই নদীর শুকনো বুকের কাছে এসে থমকে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে নদী দ্যাখে। নদী কোথায়, এ যেন বৃদ্ধা রমণীর ধূ-ধূ করা বুকের জমিন। দু’পারে নিঃসীম বালিয়াড়ি। এদিকে সেদিকে বালি আহরণেচ্ছু দু’চারটি ট্রাক অন্ধ দৈত্যের মতো ঘোঁৎ ঘেঁাঁৎ করতে করতে নেমে যায় নিচে, বৃদ্ধা নদীর হি হি হাসি শুনে আর এগোতে সাহস পায় না; ডালা নামিয়ে বালি তুলতে শুরু করে। নদী শুয়ে থাকে নিঃসংকোচে, যেন এই পড়ন্ত বয়সে আঁচলে বুক ঢাকার প্রয়োজন তার ফুরিয়েছে, এমনই নির্বিকার। অথচ হিমালয়কন্যা পদ্মার আত্মজা, সে নাম তার গড়াই; রবি ঠাকুর আদুরে গলায় ডাকতেন গোরাই বলে। সেই গোরাইকে চোখ রাঙিয়ে ঢাকা-রোড চলে যায় তার গন্তব্যে।
কে কবে ভেবেছিল ঢাকা রোডের দক্ষিণে উর্বর এই আবাদি জমির বুকেও গড়ে উঠবে জনবসতি! উত্তরে হাউজিংয়ের প্লট বরাদ্দ শুরু হলে রায়হান কবির এই দিকটায় মনোযোগ দেয়। অতীব সস্তায় হুট করে কিনে ফ্যালে এক বিঘে জমি। বড়ি করে আরো কয়েক বছর পরে। তখনো চারিপাশে ফাঁকা মাঠই বটে। রাতের বেলা শেয়ালের ডাক সচকিত করে রাখে পুরো এলাকা। এমনকি দিনের বেলায় তেনাদের সাক্ষাৎ লাভও দুর্লভ কিছু নয়। তা এ সব জীবজন্তুর সঙ্গে সহাবস্থানের কথা বিবেচনায় রেখেই রায়হান কবির বাড়ির কাজে হাত দেয়। বাড়ির নকশায় কোনো রকম বাণিজ্যিক ভাবনার ছায়া পর্যন্ত পড়তে দেয়নি। স্ত্রী রাজিয়া সুলতানারও সেই একই মত- ব্যবসা করতে চাও তো আপত্তি নেই, অন্য কোথাও টাকা খাটাও, ঠিকই তোমার টাকার আন্ডাবাচ্চা বেরোবে। বাড়ি ভাড়া দেওয়া একদম বাজে ব্যাপার, কেমন যেন অসভ্যতার গন্ধ পাই।
রায়হান কবির এই ‘অসভ্যতার গন্ধ’ শব্দ যুগল শুনে খুব অবাক। সে ব্যবসায়ী মানুষ। দু’তিন রকমের ব্যবসা তার। তবু ভাড়ায় খাটানোর উদ্দেশ্যে বাড়ি করার কথা সেও কখনো ভাবেনি। সে বাড়ি করতে চায় নিজেদের বাস করার জন্যই। সে কারণে আকাশ-ছোঁয়া পরিকল্পনাও তার নেই। পাঁচতলা-সাততলার ফাউন্ডেশনও দেয়নি। তার বাড়িটাকে একতলাও বলা যায়, দেড়তলা বললেও ক্ষতি নেই। উপরতলায় অ্যাটাচ্্ড বাথসহ মোটে দুটো রুম; দক্ষিণে প্রশস্ত খোলা ছাদ। চাঁদনি রাতে ওটাই হয়ে যায় নিকানো উঠোন। সব মিলিয়ে দু’চারজন মেহমানসহ স্বস্তির সঙ্গে নিজেদের বাস করার যোগ্য একটা বাড়ি। বাড়ি মানে এই-ই। এই যে নিজের মতো করে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বাস করা। ইচ্ছে মতো শ্বাস নেওয়া, ইচ্ছে মতো রোদ মাখা, ইচ্ছে মতো বৃষ্টিতে ভেজা; রাতের নির্জনতায় একে অপরের বক্ষলগ্ন হয়ে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়া। রাজিয়া সুলতানা বেশ কবিতার মতো করে দরদমাখা গলায় বলে। উনুনে ফোটা শাদা খইয়ের মতো শুভ্র হাসি ছড়িয়ে জানায়, আমরা বাপু গ্রামের মানুষ বাড়িঘর বলতে মায়ের বুকের মমতা বুঝি, বাপের কাঁধের নির্ভরতা বুঝি। নিজেই আবার প্রশ্ন করে- বাড়ি মানে কি ইট বালু সিমেন্টের স্তূপ? এর বেশি কিছু নয়?
সেই বেশি কিছুটুকুরই বাস্তবায়ন করতে চেয়েছেন রায়হান কবির। এক বিঘে জমি মানে তো কম জায়গা নয়! মাঝখানে ওই একটুখানি বাড়ি। পেছনে সবজি বাগান। সামনে ফুলবাগান। দুই পাশে দুই জোড়া নারকেলগাছ মাথা উঁচু করে দায়িত্ব নিয়েছে অতন্দ্র প্রহরার। বাড়ির সামনে যেখানে প্রাচীরের প্রধান ফটক হবার কথা, সেখানে দাঁড়িয়ে আছে কৃষ্ণচূড়া এবং রাধাচূড়া। সত্যি বলতে কি কৃষ্ণচূড়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকলেও রায়হান কবির আগে কখনো রাধাচূড়ার নামই শোনেনি। তার পরিকল্পনা ছিল- একজোড়া দেবদারু লাগবে, আকাশছোঁয়া সাধ নিয়ে অতিদ্রুত ওরা বেড়ে উঠবে; বেড়ে ওঠার কালে ওদের পাতায় পিছলে পড়বে রোদ কিংবা চাঁদের কিরণ। রাজিয়া সুলতানা ভিন্নমত জানায় অন্যভাবে- লাগাও তোমার দেবদারু, কে মানা করছে! একটু সরিয়ে লাগাও। বাড়ির দুই কোণে লাগও। সামনেটায় আমার কৃষ্ণচূড়া রাধাচূড়াই থাকবে।
শুধু মুখের কথা নয়, রাজিয়া সুলতানা একদিন সত্যি সত্যি সে কথাকে কাজে পরিণত করে। দূরের কোনো নার্সারিতে নিজে গিয়ে সংগ্রহ করে আনে কৃষ্ণচূড়া এবং রাধাচূড়ার চারা। প্রথমে ভেবেছিল সে একাই নিজ হাতে চারা দুটি রোপণ করবে মাটিতে। পরে তার সিদ্ধান্ত পাল্টায়। স্বামীকে হুট করে ডেকে এনে নির্দিষ্ট জায়গা দেখিয়ে বলে,
এই নাও ধরো। তোমারটা তুমি লাগাও।
আমার! রায়হান কবির তো ভীষণ অবাক- আমার আবার কোনটা?
এই যে একটা। এর নাম রাধাচূড়া। এটা তোমার।
আর ওইটা বুঝি কৃষ্ণচূড়া?
জি¦ জনাব।
ওরা দেখতে তো প্রায় একই রকম।
আহা, কৃষ্ণের ছায়ায় রাধার বেড়ে ওঠা যে! দুইয়ে মিলে এক ও অভিন্ন সত্তা। তাদের আলাদা করবে কে!
রায়হান কবিরের চোখে ঘোর লেগে যায়। স্ত্রীর কথা কেমন যেন রহস্যময় মনে হয়। সাহিত্যের মানুষ, কোন কথা যে কীভাবে ঘুরিয়ে বলে, তার তল খুঁজে পাওয়া কখনো কখনো ভার হয়ে ওঠে। তবু সে ভয়ে ভয়ে বলে,
কী যে বলো না তুমি! দেখতে এক রকম হলে আর আলাদা নাম কেন?
সে পরিচয় পাবে তুমি আরো পরে, ফুল ফুটলে।
তাই নাকি! দুই গাছের ফুল দুই রকম?
হ্যাঁ, তাই তো হবে! একজন রাধা, অন্যজন কৃষ্ণ; দুই রকম হবে না?
ওহ্্! তুমি যা রহস্য করতে পারো না! এই বললে এক ও অভিন্ন সত্তা, আবার দুই রকম- কোনটা সত্যি?
খিলখিল করে হেসে ওঠে রাজিয়া। হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে স্বামীর গায়ে। প্রকাশ্যে দিবালোকে নিবিড় আলিঙ্গনে আঁকড়ে ধরে তাকে। সহসা উষ্ণ চুম্বন এঁকে দেয় ঠোঁটে।
তারপর কানের কাছে মুখ নামিয়ে বলে,
দুটোই সত্যি। দুটোই।
যা! সত্যি কখনো দুটো হয়?
হয় হয়।
কীভাবে হয়?
এই যে এভাবে।
এ ভাবে মানে?
আমরা দুজন মানুষ, এটা তো সত্যি?
হ্যাঁ।
আরেক সত্যি হচ্ছে এইটা।
আগ্রাসী দু’হাত বাড়িয়ে জাপটে ধরে স্বামীকে। তারপর বলে- এভাবে সম্পূর্ণ একাকার হয়ে যাওয়া। অভিন্ন সত্তা।
রায়হান কবির নিজেকে আলিঙ্গন মুক্ত করে নিয়ে বলে,
কী যে পাগলামি হয়েছে না তোমার! দু’চার পাতা কবিতা লেখো সে আমি জানি। কবি হবার বদলে কি তুমি দার্শনিক হয়ে যাচ্ছ?
আবার খই ফোটা হাসি উথলে ওঠে রাজিয়া সুলতানার ঠোঁটে। রায়হান বিস্মিত, হাসছ কেন?
হাসছি কি আর সাধে!
কেন, হাসির কী হলো শুনি!
হাসব না! কবি আর দার্শনিক বুঝি আলাদা সত্তা হলো!
উহ্্! আমার ভুল হয়েছে ম্যাডাম। আমার মনেই থাকে না যে সম্প্রতি তুমি কলেজ-টিচার হয়েছ।
কপট রেগে ওঠে রাজিয়া,
তাই কী হয়েছে?
ছাত্রছাত্রীদের কাছে পণ্ডিতি করতে করতে আমার উপরেও ঝাড়তে পারো, এটা অনেক আগেই আমার বুঝা উচিত ছিল।
এ্যাই! ভালো হবে না বলছি!
না, না, এখন থেকে তুমি বলবে, আমি নির্বিবাদে শুনব।
দাঁড়াও দাঁড়াও, আজ রাতে তোমাকে আমি বৈষ্ণব দর্শন বুঝাব। না হলে তুমি রাধা কৃষ্ণকেই চিনবে না ঠিকমতো।
তা ঠিক। রাতের বেলা তুমি যা শেখাবে তাই শিখব ম্যাডাম। সেটা দর্শন-ইতিহাস-সাহিত্য-বিজ্ঞান যা-ই হোক, আপত্তি নেই।
দুই.
কেবল কৃষ্ণচূড়া আর রাধাচূড়াই নয়, এ বাড়ির সামনে এবং পেছনের পুরো বাগানই এক অর্থে স্বামী-স্ত্রী দুজনের যৌথ রচনা। হ্যাঁ, রচনা শব্দটিই তাদের ক্ষেত্রে সপ্রযুক্ত। সার্বিক সহযোগিতার জন্য কাজের মানুষ একজন সঙ্গে থাকলেও গোটা পরিকল্পনা দুজনের রায়হান কবির এবং রাজিয়া সুলতানার। এ বাড়ির কোন দিকে কোন গাছ লাগাতে হবে, কোন ফুল সকালের রোদে হেসে ওঠে, কোন ফুল বিকেলের তাপহীন আলোয় ডানা মেলে নেচে ওঠে, কোন ফুলের আয়ু কতদিন, রং কী রকম আকৃতি কেমন- এই সব কিছু বিবেচনায় রেখে ভেবেচিন্তে হিসেব করে সব চারা লাগানো। গাছে গাছে ফুল ফোটে প্রাকৃতিক নিয়মেই, তবু তাদের সাধনার শেষ নেই। পরিকল্পনার শেষ নেই। আর সেই সঙ্গে পরিচর্যা তো আছেই।
এ বাড়িতে বসবাস শুরু করার দু’তিন মাসের মধ্যেই বাড়ির চেহারা বদলে যায়। কী যে চোখ জুড়ানো সবুজের সমারোহ। শুরুতেই বেয়াড়া বাগান বিলাস আর তরুলতায় আটকে যাবে যে কারো দৃষ্টি। তারপরই নানা বর্ণ ও গোত্রের ফুল আর ফুল। কেউ ফুটেছে, কেউ ফোটেনি। কেউ জেগেছে, কারোবা তখনো ঘুম ভাঙেনি, অপেক্ষায় আছে। গৃহকর্ত্রীর আদরমাখা হাতের পরশ পেলেই চোখ মেলে তাকাবে, জেগে উঠবে সুষুপ্তির বুক থেকে। সব চেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে, অল্প কিছুদিনের মধ্যেই অনাহূত এক অতিথির আগমন ঘটে এই বাগানে। তার নাম আলোকলতা। কেউ বলে স্বর্ণলতা। হতে পারে, গায়ের রং তার সোনার মতোন, স্বর্ণলতা হতেই পারে। কিন্তু এখানে তাকে কে ডেকেছে, কে তাকে হাত ধরে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে! প্রকৃতিরাজ্যে কত না বিস্ময়কর ঘটনাই ঘটে চলেছে প্রতিনিয়ত। কারো আদর যত্ন নেই, কেউ করে না স্নেহ পরিচর্যা; বরং সত্যি বলতে কী মানুষের উপেক্ষাই তার নিয়তি, তবু কোথা থেকে যে এত প্রাণ প্রাচুর্য পায় আলোকলতা, (সূর্যের অকৃপণ আলো থেকেই কি!) সবিস্তারে নিজের অস্তিুত্ব ঠিকই জাহির করে, রৌদ্রকরোজ্জ্বল স্নিগ্ধ হাসি ঠিকই ছড়িয়ে দেয় বাগান জুড়ে। গোড়াতেই কথা উঠেছিল একবার- ও সব চতুরালি হাসি-টাসি দেখলে চলবে না, ওকে এখনই উচ্ছেদ করত হবে। বাড়তে দিলেই বেড়ে যাবে, অতএব এখনই। শিউরে ওঠে রাজিয়া সুলতানা। স্বামীর মুখে হাত দিয়ে বলে, এ কী নিষ্ঠুর কথার ছিরি! এভাবে বলতে পারলে তুমি!
কী আশ্চর্য! ও তোমার কাঁধে চাপবে তো!
সহসা বড্ড খুশি হয়ে ওঠে রাজিয়া,
সত্যি আমার কাঁধে চাপবে আলোকলতা!
হ্যাঁ, আলোকলতাই বলো আর স্বর্ণলতাই বলো, ওদের স্বভাবই ওই রকম। চান্স পেলেই মাথায় উঠে পড়বে।
আমার তো মাথায় উঠলেই ভালো। কালো কেশ ঢেকে যাবে সোনালি আভায়।
ইয়ার্কি হচ্ছে কেমন!
না না, পতি দেবতার সঙ্গে কি ইয়ার্কির সম্পর্ক! ইয়ার্কি চলে?
শোনো শোনো, তোমার ওই স্বর্ণলতা গোটা বাগানের সর্বনাশ ঘটাবে দিনে দিনে ছেয়ে ফেলবে সব কিছু।
তো কী করতে হবে!
উচ্ছেদ করতে হবে। সমূলে উচ্ছেদ।
হঠাৎ খিলখিল করে হেসে ওঠে রাজিয়া। হাসির গমকে কেঁপে ওঠে তার শরীর।
হাসির কী হলো হঠাৎ?
হাসতে হাসতেই কটাক্ষ করে,
যার মূলই নেই, তাকে করবে সমূলে উচ্ছেদ?
ওই হলো। উপড়ে ফেলতে হবে।
আবারও হাসি পায় রাজিয়া সুলতানার। হাসির মধ্যেই বলে,
মূলছাড়া উপড়ানো যায়?
তুমি যা-ই বলো, ওই স্বর্ণলতার ঝাড় বাগানে রাখা যাবে না।
রাজিয়া হঠাৎ স্বামীর দু’হাত ধরে অনুনয় জানায়,
থাক না সোনা, ওকে তাড়িয়ে দিয়ো না। কেটেছেঁটে সাইজ করে রাখো। দ্যাখো তো ওই আলোকলতা কেমন আলো ছড়িয়েছে। শোভা বাড়িয়েছে।
আচ্ছা। পরে কিন্তু টের পাবে বলে দিলাম।
আহা, সুন্দরের জন্য অনেক পীড়ন সইতে হয়, মনে নেই?
এইবার হুট করে ফণা নামায় রায়হান কবির। হঠাৎ অন্যমানুষ হয়ে যায়। এক ঝাঁক স্মৃতি এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে একযোগে। স্মৃতির সমুদ্রে যেনবা হাবুডুবু খায়, দম বন্ধ হয়ে আসে তার। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে,
হ্যাঁ, মনে পড়ছে বই কী! তোমাকে পাবার জন্য দুস্তর পথ পাড়ি দিয়েছি আমি অনেক কিছু সহ্য করেছি। সেও তো সুন্দরের জন্যই।
বাব্বা! ভারি বীরপুরুষ!
বীর পুরুষ আমি হই না হই, রাজকন্যা তো ঠিকই উদ্ধার করেছি।
রাজকন্যা না ছাই।
সেই রাজকন্যার জন্য রাজপ্রাসাদ না হোক একটা বাড়ি তো বানিয়েছি। এখন সেই বাড়ির একটা নাম তো লাগবে!
আমি তো রাজপ্রাসাদ চাইনি প্রেমকুমার। ভালোবাসার গাঁথুনিতে তৈরি একটা বাড়ি চেয়েছিলাম।
হ্যাঁ, সেটা তো হয়েছে। এবার নামকরণ।
বাড়ির নামকরণ নিয়ে এর আগেও বহুবার কথা উঠেছে। এ দায়িত্বটা এক রকম ছেড়েই দেওয়া আছে রাজিয়া সুলতানার উপরে। সাহিত্যের মানুষ, গল্প-কবিতার নামকরণ করতে পারে, নিজের স্বামীর নাম বদলে দিতে পারে সকালে সন্ধ্যায়; কখনো রাজকুমার, কখনো প্রেমকুমার, ঘুমোতে দেখলেই কুম্ভকর্ণ- এই রকম আরো কত কী; সেই মানুষ নিজেদের বাড়িটার জন্য সুন্দর একটা নাম রাখবে না? না, এ বেলায় তার গড়িমসির শেষ নেই। অথচ সেদিন কেমন হুট করে বলে ফ্যালে,
নাম রেখেছি আলোকলতা।
রায়হান কবিরের চোখে বিস্ময়,
বাড়ির নাম আলোকলতা?
না না, আমাদের বাড়ির নাম এটা নয়।
তাহলে।
হঠাৎ বিষ্ণু দে’র একটা কাব্যের নাম মনে এলো, তাই...
কী নাম- আলোকলতা?
রাজিয়া সুলতানা হেসে ওঠে। স্বামীর চোখে চোখ রেখে বলে,
আলোকলতা নিয়ে তুমি বেশ আতংকের মধ্যে আছ দেখছি।
নাহ্্! এই যে তুমি বললে!
বিষ্ণু দে’র কাব্যের নাম- ‘নাম রেখেছি কোমলগান্ধার’। কী সাংঘাতিক আধুনিক নামকরণ দেখেছ!
কাব্য-টাব্য নিয়ে রায়হান কবিরের বিশেষ আগ্রহ নেই। স্ত্রীর আছে কাব্যবাতিক, তাই মুখ বুজে অনেক কিছু সহ্য করতে হয়, গভীর রাতে সদ্য রচিত নতুন কবিতা মনোযোগী শ্রোতার ভান করে শুনতে হয়। কবিতা শোনাবার পর রাজিয়া যেন স্বপ্নের ঘোরে বলে- আকাশ ভরা তারাদের মাঝ থেকে এই সব শব্দেরা নেমে এলো, দ্রুত হাতে আমি কাগজে লিখে নিয়েছি বটে, তবু তোমার সঙ্গে ভাগাভাগি করতে না পারলে এ আনন্দের স্বাদই কেমন বিস্বাদ হয়ে যায়; সেই জন্য এত ডাকাডাকি। বুঝেছ? কবিতাবিমুখ স্বামীকে এতটা গুরুত্ব দিয়ে তার সঙ্গে কাব্য-আনন্দ ভাগাভাগির এ প্রস্তাবের হয়তো কোনো মানেই হয় ন। রায়হান কবিরের তবু বেশ ভালো লাগে। কোনো কোনো দিন একই কবিতা দ্বিতীয়বার পাঠেরও আবেদন জানায়। কিন্তু সেদিন বিষ্ণু দে’র কাব্যের নাম শুনে বড় একটা হাই তুলতে তুলতে তার মুখ থেকে বেফাঁস মন্তব্য বেরিয়ে আসে- তোমাদের এই আধুনিক কবিতার ভেতরে বাইরে কী যে বলো, বুঝেই উঠি না। নতুন সৃষ্টির আনন্দে রাজিয়ার মন ফুরফুরে থাকলে এসব মন্তব্য বিশেষ একটা গায়েই মাখে না। হুট করে বলে বসে- বাড়ির নাম কোমলগান্ধার রাখলে হয় না?
আলোকলতা থেকে এলো কোমলগান্ধার! এসব শব্দের বর্ণগন্ধ কিছুই ঢোকে না রায়হান কবিরের মস্তিষ্কে। ফলে বাড়ির এই নাম প্রস্তাবের পক্ষে-বিপক্ষে কোনো দিকেই দাঁড়ানো হয় না তার। রাজিয়াকে তখন গল্পের নেশায় পেয়েছে। সে ছাত্র জীবনের স্মৃতির ঝাঁপি আলগা করে জানায় কবি বিষ্ণু দে’র সঙ্গে তার পরিচয়ের কথা। সাক্ষাৎ পরিচয় নয়, সে ছিল কাব্য পরিচয়।
সে বছর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে শ’তিনেক ছাত্রছাত্রীর মধ্যেমাত্র পাঁচজন অল্টারনেটিভ পেপার হিসেবে গ্রহণ করে ত্রিশোত্তর কবিতা-গ্রুপ। একমাত্র জীবনানন্দ দাশ ব্যতীত অন্য কবিদের কাব্যগ্রন্থ তখনো রাজশাহীতে দুষ্প্রাপ্যই বলা চলে। লাইব্রেরিতেও সুলভ নয়। তাহলে উপায়! বই কোথায় পাওয়া যাবে! কবি আবু বকর সিদ্দিক অন্তরের সবটুকু দরদ ঢেলে ক্লাসে কবিতা পড়ান, বিশ্লেষণ করে উপমা উৎপ্রেক্ষা বুঝিয়ে বলেন, কিন্তু মূল বই তো লাগবে। সুধীন দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী এমনকি বুদ্ধদেব বসুর কাব্য যদিবা কোনোভাবে ম্যানেজ হয়ও, বিষ্ণু দে’র কাব্য কোথায়। সিদ্দিক স্যারের হাতে ঘোরাফেরা করে দু’একটি কাব্য, কিস্তু সে কি ছাত্রছাত্রীর হাতে আসবে কখনো? ত্রিশোত্তর গ্রুপের পঞ্চপা-রের মধ্যে একমাত্র নারী সদস্য হিসেবে রাজিয়াকেই দায়িত্ব দেওয়া হয় স্যারকে পটিয়ে সে বই ম্যানেজ করার। এক সপ্তাহের মধ্যে ফেরত দেওয়ার শর্তে রাজিয়া সেদিন সিদ্দিক স্যারের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে বিষ্ণু দে’র লেখা ‘নাম রেখেছি কোমলগান্ধার’ কাব্যটি নিয়ে আসে, সেদিন বন্ধুদের মধ্যে সে কী আনন্দ! কলকাতার সিগনেট প্রেস থেকে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণ। পাঁচজনই বইটি উল্টেপাল্টে দ্যাখে আর ভাবে, কীভাবে বইটিকে নিজেদের করে নেওয়া যায়। ফটোস্ট্যাট মেশিন তখনো রাজশাহীতে সুলভ নয়, আর সেটা করতে হলে বইয়ের সেলাই খুলতে হবে। সৌন্দর্যহানি ঘটবে। স্যার অসন্তুষ্ট হতে পারেন। সহসা দায়িত্ব কাঁধে নেয় আতাহার নামে এক বন্ধু। তার হাতের লেখা ভালো, সে বাঁধানো খাতায় পুরো কাব্যটি হাতের লেখায় তুলে নেবে। যে কথা সেই কাজ। বিষ্ণু দে তো বটেই কবি আবু বকর সিদ্দিকও জানলেন না- ‘নাম রেখেছি কোমলগান্ধার’ কাব্যের অভিনব একটি সংস্করণ হয়ে গেল মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে। অনেকক্ষণ পর রাজিয়া সুলতানা বর্তমান বাস্তবতায় ফিরে স্বামীর গায়ে নাড়া দিয়ে বলে,
জানো, আমাদের বন্ধু আতাহারের কাছে নাকি আজো সেই কাব্যের অভিনব সংস্করণটি সুরক্ষিত আছে।
রায়হান কবির চমকে ওঠে,
বলো কী! সেই হাতে লেখা কপি?
হ্যাঁ। কী যে পাগলামি- সেই হাতে লেখা কাব্যের প্রচ্ছদ পাতাটি ছিল আমার হাতে লেখা।
তোমার হাতে লেখা?
স্যারের কাছ থেকে বইটি আমি এনে দিয়েছিলাম বলে এই দুর্লভ সুযোগটুকু আমাকেই দেওয়া হয়। আতাহার বলে, প্রচ্ছদ পাতায় তুই-ই নাম লিখে দে গোটা গোটা অক্ষরে।
ও বাবা! তোমাদের মধ্যে তুই তোকারি ছিল নাকি?
রাজিয়া হেসে ওঠে। অতীতের ঘোরলাগা হাসি। হাসি থামিয়ে বলে,
আমাদের আতাহার ছিল ভীষণ ভদ্রলোক। উঁচু স্বরে হাসতে জানে না। কোনো মেয়েকে ‘আপনি’ ছাড়া তুমি বলতে পারে না। ভারি লাজুক স্বভাবের।
তাই নাকি?
আমিই তাকে জোর করে তুই তোকারিতে নামিয়ে আনি।
বাহ্্! ভারি মজার বন্ধুত্ব তো! এখনো তোমাদের যোগাযোগ আছে?
নাহ্্! শুনেছিলাম রংপুর কারমাইকেল নাকি মহিলা কলেজে ছিল। এখন কোথায় কে জানে!
ওই যে বললে- আজো তার কাছে সেই অভিনব সংস্করণ আছে; যোগাযোগ না থাকলে তুমি জানলে কী করে?
রাজিয়া সুলতানা কপালে ভাঁজ ফেলে বিশেষ ভ্রুভঙ্গ করে তাকায়,
এ্যাই! এভাবে কথা বলার মানে কী?
এভাবে মানে!
আমার সহপাঠী বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ থাকতেই পারে।
তো সেই কথাটা খোলামেলা বলাই ভালো।
খোলা থাকলেও সবকিছু তোমার নজরে পড়ে না বুদ্ধু কোথাকার!
তাই নাকি?
তাই তো দেখছি! আবার যেটা ঢাকা আছে, সেটার দিকে নজর পড়ে বেশি বেশি।
কথা বলতে বলতে রাজিয়া উঠে সাইড টেবিল থেকে শুক্রবারের খবরের কাগজ নিয়ে এসে মেলে ধরে, পাতা ওল্টায়, তারপর বলে-
এই কাগজ কি পড়েছ?
রায়হান কবির ঘাড় ঘুরিয়ে এক নজর চোখ বুলিয়েই বলে,
শুক্রবারের কাগজ। বাসি কাগজ দিয়ে কী হবে?
সাহিত্যের পাতা কখনো বাসি হয় না, কতদিন বলেছি তোমাকে। মনে আছে?
বিশেষ কিছু আছে নাকি শুক্রবারের পাতায়?
আছে মানে! পত্রিকার ভাঁজ ভেঙে সামনে মেলে ধরে দ্যাখায় রাজিয়া, এই যে দ্যাখো আমাদের আতাহার আলী আখন্দ লিখেছে- ‘নাম তার কোমলগান্ধায় : বিষ্ণু দে।’ পড়ে দেখেছ?
রায়হানের চোখে মুখে বিষণ্ন রৌদ্রছায়া, ঠোঁটে বিব্রত হাসি,
তোমার ওই সাহিত্য সাময়িকী আমার তো কখনো পড়া হয় না, তুমি জানোই।
হ্যাঁ হ্যাঁ, আমারই ভুল। পড়লে তুমি জানতে- এই লেখায় আতাহার দাবি করেছে সেই বিশেষ সংস্করণের কোমলগান্ধার এখনো তার সংগ্রহে সযতনে আছে।
থাকবে না- তোমার হাতের লেখা প্রচ্ছদ যে!
হতেও পারে। কিন্তু সেই কথাটি এখানে লেখেনি আতাহার।
মাথা খারাপ- সব কথা লিখে প্রকাশ করা যায়।
তা বেশ বলেছ। এবার যোগাযোগ হলে আতাহারকে বলব এ কথা।
এভাবেই কথায় কথায় কথা বেড়ে যায় অনেক। কথার চোখ ফোটে। কথার ডানা গজায়। কথার লেজ নেচে ওঠে। এক সময় পাখি হয়ে উড়ে যায় কথা। উড়তে উড়তে উড়তে উড়তে দূর নীলিমায় ভেসে যায়। সত্যিকারের পাখি হলে হয়তো সমস্ত দিনের শেষে নিঝুম সন্ধ্যায় ঠিকই ঘরে ফিরে আসতো। কিন্তু কথার পাখিরা ঘরে ফেরে না। কেবলই উড়ে উড়ে যায়। তাকে ধরতে গেলেই বিড়ম্বনা। ঘরের বাঁধনে বাঁধতে গেলেই দম বন্ধ করা গন্ধ বেরোয়- উৎকট, অসহনীয়। ফুলদানিতে ভিজিয়ে রাখা ফুলের সৌরভ যেমন পচাপানির কারণে দুর্গন্ধে পরিণত হয় অনেকটা সেই রকম। মুখের কথা হাওয়ায় ভাসিয়ে দেওয়ার মধ্যেই সার্থকতা। তাকে হাতের মুঠোয় ধরতে চায় কোন আহাম্মক!
এসব ক্ষেত্রে রাজিয়া সুলতানা অনেক বেশি উদার। সাহিত্যপাঠের অভিজ্ঞতা তার মনের দিগন্তকে বহুদূর বিস্তৃত এবং প্রসারিত করেছে। ধনাঢ্য পিতার একমাত্র পুত্র রায়হান কবিরের সীমাবদ্ধতার দিকগুলো সে হার্দিক সহিষ্ণুতা দিয়ে বিবেচনা করতে জানে। আবার রায়হানও কখনো কখনো শিশুর সারল্যমাখা কণ্ঠে নিজের দুর্বলতার কথা অকপটে মেলে ধরতে পারে। এই যেমন নতুন বাড়ির নামকরণ নিয়ে কত সহজেই সে বলে ফ্যালে- তোমার মতো বেশি বেশি লেখাপড়া জানলে আমি এতদিনে কবেই বাড়ির নাম দিয়ে ফেলতাম।
রাজিয়া ঘাড় বাঁকা করে তাকায়, বলে,
লেখাপড়ার কথা উঠছে কেন বলো তো! তোমার বাড়ি, দাও না তুমি একটা নাম।
এ প্রস্তাবে যেন রায়হান একটু খুশিই হয়ে ওঠে। হাত কচলে নিতিবিতি করে সে বলে,
বলব একটা নাম?
বলো।
তোমার নামে নাম- রাজিয়া মহল।
আমার নামটা তো আমারই পছন্দ হয় না। তার সাথে আবার মহল!
হ্যাঁ, রাজিয়া মহল।
মৃদু হেসে রাজিয়া বলে, সেকেলে নাম হয়ে যাচ্ছে না?
এই তো, বিএ পাসের বিদ্যের দৌড় আর কদ্দূর যাবে? সেকেলে হবে না?
কপট শাসন করে রাজিয়া,
আবার সেই বিদ্যের কথা!
তাহলে সাহিত্যের কথাই বলি। তুমি কবি মানুষ, নাম দিতে কতক্ষণ!
হ্যাঁ, কাব্যগন্ধী নাম আমার পছন্দ, সেটা ঠিক।
হোক, তবে তাই হোক।
শহীদুল্লাহ কায়সারের উপন্যাস সংশপ্তকের কথা মনে আছে তোমার?
মনে থাকবে না কেন! এই যে কিছুদিন আগে টিভি সিরিয়াল হলো, সেইটা তো?
হ্যাঁ। নাটকটা তোমার খুব পছন্দ হয়েছিল।
তুমি বুঝিয়ে বলার পর নামটাও তোমার ভালো লেগেছে।
এতদূর এগিয়ে আসার পর বেশ কায়দা করে প্রস্তাব করে রাজিয়া,
আমাদের বাড়ির নাম যদি সংশপ্তক রাখা যায়, কেমন হয়?
এক বাক্যে মেনে নেয় রায়হান কবির,
বেশ ভালো হয়।
নিজেদের নতুন বাড়ির নামকরণের এই প্রীতিমধুর পরিবেশে রায়হান কবিরের মাথার ভেতরে পুরাতন এক ভূত এসে হানা দেয়। সেই ভূতের কাজ হচ্ছে পুরাতন কথা মনে করিয়ে দেওয়া। রায়হান ঠিক সেই কাজটিই করে, রাজিয়ার কাছে জানতে চায়,
আজ তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব?
রাজিয়া বলে,
ভনিতার কী আছে, বলে ফ্যালো!
বাড়িভাড়ার মধ্যে তুমি অসভ্যতার গন্ধ পেলে কীভাবে?
কেন! তুমি বাড়িভাড়া দেবে নাকি!
মাথা খারাপ! আমি তো সে কথা বলিনি!
তাহলে এ প্রসঙ্গ উঠছে কেন? ওটা আমার কাছে অসভ্যতাই মনে হয়।
কিন্তু কেন?
এভাবে আঁকড়ে ধরলে আমি ঠিক বলতে পারব না। রাজিয়া সুলতানা এক চিলতে হেসে যোগ করে- অসভ্যতা নয়! বাড়িভাড়া আর নারীভাড়া- দুটোর মধ্যেই শরীরী ব্যাপার আছে বলে আমার মনে হয়!
রায়হান কবির বিস্মিত- শরীরী ব্যাপার!
তা নয় তো কী! ভাড়া করা নারীতে এবং বাড়িতে মানুষ তো শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যই খোঁজে!
বাব্বা! দারুণ ব্যাখ্যা!
একান্ত নিজের করে পাওয়া নারীতে এবং বাড়িতে সবাই খোঁজে মানসিক প্রশান্তি এবং নির্ভরতা। এটুকু বোধ হয় সবারই নিজস্ব।
রায়হান ফোড়ন কাটে।
সবার না হোক, অন্তত তোমার একান্ত নিজস্ব।
তা বলতে পারো।
এভাবেই হয়ে ওঠে বাড়ির নাম সংশপ্তক।
নামকরণ হয়ে যাবার পর কথা ওঠে, এবার তাহলে শ্বেতপাথরে নামটা লিখিয়ে কোথাও একটা লটকে দেওয়া যাক। না, সেখানে আবার প্রবল আপত্তি রাজিয়া সুলতানার। তার সেই পুরাতন যুক্তি পাথরে লিখো না নাম, পাথর ক্ষয়ে যাবে। তাহলে লিখছে যে সবাই! কত যত্ন করে লিখে রাখে। রাজিয়ার সোজাসাপ্টা জবাব- লিখুক সবাই। আমরা তো সবার মাতো নই। শুধু বাড়ি নয়, আমরা দু’জনেই হতে চাই সংশপ্তক। মৃত্যু আমাদের নাগাল পাবে না। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত আমরা লড়াই করে যাব, ভালোবাসার লড়াই।
এ রকম ব্যাখ্যা এবং প্রতিজ্ঞা শুনে রায়হান কবিরের মুখে কথা সরে না। সে কেবল দু’হতের অঞ্জলিতে রাজিয়ার মুখম-ল তুলে ধরে প্রগাঢ় মমতায় তার কপালে এঁকে দেয় প্রলম্বিত চুম্বন। স্বামীর বক্ষলগ্ন হয়ে রাজিয়া ঘোষণা দেয়, আগামীকাল থেকে আমার নতুন নামকরণ হবে।
ভারি রহস্যময় মনে হয় এ ঘোষণা। রাজিয়ার নতুন নামকরণ! কী আশ্চর্য, বাড়ির সাথে সাথে মানুষেরও নাম বদলে যাবে! রায়হান কবিরের খুব কৌতূহল হয়। স্ত্রীর চোখে চোখ রেখে জানতে চায়,
কী সেই নতুন নাম?
রাজিয়া সুলতানা দু’চোখের পাতা মুদে বুকের গভীর থেকে উচ্চারণ করে,
রাজিয়া রায়হান।
তিন.
রাজিয়া রায়হানের কলেজ কুষ্টিয়া শহর থেকে বেশ খানিকটা দূরে।
যাকে বলে পেটের দায়ে চাকরি করা, রাজিয়ার ক্ষেত্রে ঠিক তেমন করে বলা যাবে না। রায়হান কবিরের পৈতৃক সম্পত্তি এবং ব্যবসা বাণিজ্যে আয় উন্নতি মোটেই কম নয়। ঘরের বউকে চাকরিতে পাঠাবার প্রয়োজনও নেই, রায়হানদের পরিবারের কারো সেই দৃষ্টিভঙ্গিও নেই বলা চলে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় পড়–য়া একটি মেয়ে পটের বিবি হয়ে কতদিন ঘরের মধ্যে বন্দি থাকবে? কুমারখালি ছোট্ট একটি থানা শহর। সেই শহরের পাশেই নদী, কিন্তু ইচ্ছে হলেই কি জোছনা রাতে সেই নদীপারে যেতে পারে রাজিয়া? শহর থেকে সাত-আট মাইল দূরে শিলাইদহ, রবীন্দ্রনাথের কুঠিবাড়ি, রাজিয়া কি ইচ্ছে হলেই সেই কুঠিবাড়ির আঙিনায় ঘুরে আসতে পারে? অথবা ইচ্ছে হলেই রাজিয়া কি পারে ছেউড়িয়ায় গিয়ে লালন অনুসারী কোনো বাউলের সান্নিধ্যে দু’দণ্ড কাটিয়ে আসতে? কোনো বাঙালি মেয়ের শ্বশুরবাড়ি বেধহয় এতটা স্বাধীনতা অনুমোদন করে না। রাজিয়া তখন কী করে? কার কাছে মাথা কুটে বলবে- সুস্থভাবে বাঁচার জন্য আমার একটু স্বাধীনতা চাই, চার দেওয়ালের বাইরে একটু মুক্ত আলো বাতাস চাই!
কার কাছে বলা যায়!
খুব সরলভাবে চিন্তা করতেই আলোর দিশা পেয়ে যায় একদিন। কার কাছে আবার! সোজা সে তার স্বামীর কাছেই বলবে এবং মাথা উঁচু করে বলবে। আঁধার রাতের পরাণ সখা সে, আলোর পথে অন্যকে নিয়ে যাবে? অর্থনৈতিক অবস্থার বিবেচনায় রায়হান কবিরের পিতৃপরিচয় এবং সামাজিক অবস্থান রাজিয়াদের তুলনায় অনেক উপরে, তবু এ বিয়ের প্রস্তাবে প্রথম আপত্তি ওঠে রাজিয়ার বাবার কাছ থেকেই। রেভিনিউ অফিসের সামান্য কেরানি হয়েও মেয়ে নিয়ে কোথায় যেন একটু সূক্ষ্ম অহংকার ছিল তার। শেষে সেই অহংকারের বাতি দপ করে নিভিয়ে দিয়েছে রাজিয়া সুলতানা নিজে। রায়হানের ভালোবাসার প্রবল জোয়ারে তার দু’চোখের দৃষ্টি তখন অস্বচ্ছ ঘোলাটে, তাই বাবার অহংকারী মুখের ছবি ভালো করে দেখতে পায়নি। নাকি দেখতে চায়নি!
অথচ কী আশ্চর্য মানুষ দ্যাখো, তিনিই একদিন বিবাহিতা মেয়ের জন্য চাকরির সন্ধান এনে দেন। কতভাবেই যে মানুষ স্বস্তি খুঁজে পেতে চায়। হোক প্রাইভেট কলেজ, মফস্বলের এ ধরনের কলেজগুলোতে ঢোকার পথও কি আর মসৃণ আছে, নাকি সহজ আছে! রাজিয়ার বাবা আটঘাট সবদিক খোঁজখবর নিয়ে তারপর মেয়েকে প্রস্তাব দেন- তুই একটা দরখাস্ত করে দে তো মা!
সেই দরখাস্তই তার ডানায় হাওয়া লাগার সূত্রপাত ঘটায়।
রায়হান কবিরকে সে আঁকড়ে ধরে এবং স্পষ্ট জানায়- সুস্থভাবে বাঁচার জন্য আমি এই সুযোগটুকু চাই। এই চাকরিটা আমি করতে চাই।
সবাইকে অবাক করে রায়হান বলে ওঠে,
এটা সুযোগ হবে কেন, এটা তোমার অধিকার। তোমার যোগ্যতা আছে, তুমি নিশ্চয়ই আবেদন করতে পারো।
চোখ ভিজে আসে রাজিয়া সুলতানার। এমন উদার উত্তর পাবে সেটা যেন ভাবতেই পারেনি সে। স্বামীর মুখের দিকে ভালো করে তাকাতেও সংকোচ হয়। রায়হান বলে,
হয়তো চাকরিটা হয়ে যেতেও পারে। কিন্তু সত্যিই কি চাকরি করার খুব দরকার আছে? আছে, আছে। লাফিয়ে ওঠে রাজিয়া, খুব দরকার আছে।
আচ্ছা।
সত্যি আমার চাকরি হবে!
তুমি চাইলে এবং চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই হবে।
আমি তো চাই-ই।
তাহলে হবে।
সত্যিই সেই চাকরি হয়েছে রাজিয়া সুলতানার।
বড় কোনো কলেজ নয়। ছাত্রছাত্রীরও অনেক ভিড় নেই। শিক্ষক সহকর্মীর সংখ্যাও খুব বেশি নয়। তবু খুব ভালো লাগে রাজিয়ার। ছায়া ঢাকা গ্রামীণ পরিবেশে গড়ে ওঠা এই কলেজটি যেন এই অঞ্চলের নিস্তরঙ্গ জীবনধারাকে খুব অলক্ষ্যে হলেও বেগবান করেছে। কলেজে ঢোকার মুখেই এক ফালি শিশুবাগান। চারাগাছগুলো লকলকিয়ে বেড়ে উঠছে সবুজ পাতা ছেড়ে ছেড়ে, কী যে ছেলে মানুষের মতো বাতাসে দোল খায় ঘাড় দুলিয়ে দুলিয়ে। মাঝে মধ্যে যেনবা গলা জড়াজড়ি করে হেসে ওঠে খিলখিলিয়ে। প্রধান রাস্তা থেকে নেমে এই শিশু বাগানের ছায়ার্দ্র পথে হেঁটে হেঁটে কলেজ আঙিনায় আসতে খুব আনন্দ পায় রাজিয়া। মাত্র এইটুকু চাকরির জন্য কবে যে ভেতরে ভেতরে এত তৃষ্ণা জমে উঠেছিল সেই হিসাব মেলাতে পারে না কিছুতেই।
কলেজের প্রিন্সিপ্যালও বাংলা সাহিত্যের শিক্ষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে বেরিয়েছেন আরো বছর পনের আগে। এখনো নিজের ছাত্র জীবনের গল্প করতে ভালোবাসেন। মাত্র তের নম্বরের জন্য ফার্স্ট ক্লাস পাননি বলে মনে খুব দুঃখ তাঁর। কাউকে সে গল্প শোনাবার সময় বলেন- আনলাকি থার্টিনরে ভাই, কপালে শিকে ছিঁড়ল না। মাত্র তের নম্বরের জন্য। তার পর পরই জানিয়ে সুখ পান, সেকালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ কিছুতেই ফার্স্ট ক্লাস দিতে চাইত না। নাকের ডগায় ঝুলানো ছিল আমার সেকেন্ড ক্লাসের মূলো। আরে বাবা সেকেন্ড ক্লাস তো সেকেন্ড ক্লাসই, তার আবার আপার-লোয়ার কিসের! যত্তোসব আবোলতাবোল! বুঝলেন ম্যাডাম, এ হচ্ছে ফার্স্ট ক্লাস না দেওয়ার ফন্দি।
রাজিয়া সুলতানার এইখানে খুব আপত্তি, এই ম্যাডাম সম্বোধনে। তার এই অপছন্দের কথা ছাত্রছাত্রীদের সোজাসুজি জানিয়ে দিয়েছে। সহকর্মীদের মধ্যেও অনেকে জেনে গেছেন, কেবল প্রিন্সিপ্যাল স্যারেরই মনে থাকে না। প্রায়ই ভুলে যান। তাঁর সহপাঠী বন্ধুদের মধ্যে ফার্স্টক্লাস না পেয়েও এমফিল পিএইচডির জোরে কে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকেছে সে সব এতদিনেও বেশ মনে আছে, কেবল মনে থাকে না এই ম্যাডাম না বলার অনুরোধটুকু। বিশেষ কৌশলে একটু ঘুমিয়ে প্রতিবাদ জানায় রাজিয়া।
আপনি কিন্তু আমার নাম ধরে ডাকবেন বলে কথা দিয়েছিলেন স্যার!
ও হ্যাঁ, তাই তো! তোমারও তো অল্পের জন্য ফার্স্টক্লাস হয়নি তাই না?
জ্বি স্যার। মাত্র পাঁচ নম্বর কম ছিল।
মোটে পাঁচ নম্বর?
প্রিন্সিপ্যাল স্যারের চেহারায় ধস নামে। যেন পাঁচ নম্বরের ঘাটতির কারণে রাজিয়া ফার্স্টক্লাস না পাওয়ায় তাঁরও যারপরনাই ক্ষতি হয়ে গেছে। মুখে চুক চুক ধ্বনি তুলে বেশ দুঃখ প্রকাশও করেন। তারপর হঠাৎ সে দুঃখ সামলে উঠে চলে যান আরেক প্রসঙ্গে,
তুমি তো কবিতা টবিতাও চর্চা কর, তাই না?
জ্বি স্যার। সে অতি যৎসামান্য।
আরে নাহ! ওইটুকুই আমার কলেজের ক্রেডিটের খাতায় জমা হয়ে গেছে। লোকে বলবে এ কলেজের শিক্ষকদের মধ্যে একজন কবিও আছে।
রাজিয়া সুলতানা ভয়ানক বিব্রতবোধ করে। একান্ত ব্যক্তিগত এ প্রসঙ্গের আলোচনা আর একটুও চলতে দেওয়া উচিত নয়, কিন্তু তার দিক থেকে কীইবা করার আছে, সেটাও নির্ধারণ করতে পারে না। এ সময়ে পরম হিতৈষীর মতো এগিয়ে আসেন ইতিহাসের লতিফ সাহেব। বিগলিত ভঙ্গিতে হাসি ছড়িয়ে তিনি প্রিন্সিপ্যাল স্যারের উচ্ছ্বসিত বাক্যের সঙ্গে যোগ করেন,
আপনার কলেজে একজন সাংবাদিকও কিন্তু আছে স্যার।
প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের পূর্বের মুড সহসা আওলা মেঘের মতো সরে যায়। টেবিল থেকে চশমা তুলে নাকের উপর চড়াতে চড়াতে বলেন,
ও হ্যাঁ, আপনি তো আছেনই।
আছি মানে কুষ্টিয়ার লোকাল কাগজে তো আছিই, ঢাকার একটা দৈনিকেরও কার্ড পেয়ে যাব শিগগিরই। আসলে লোকাল কাগজ নিয়ে পড়ে থাকলে তো স্যার সাংবাদিকের মান থাকে না। আর ঢাকার কাগজের সাংবাদিক হওয়া অতো সহজ নয়।
সাংবাদিকতা নিয়ে লতিফ সাহেবের এই কচকচানি মোটেই ভালো লাগে না প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের। রাজিয়া সুলতানাও উৎসাহ পায় না। সে উঠে পড়ার উদ্যোগ নিতেই প্রিন্সিপ্যাল সাহেব জানতে চান,
তোমার এখন ক্লাস আছে?
রাজিয়া উঠে দাঁড়িয়ে বলে,
না স্যার। আমি কমনরুমে যাব।
এরই মাঝে লতিফ সাহেব হুট করে মন্তব্য করে,
রাজিয়ার কথা বলছেন স্যার! রুটিনে ক্লাস থাক আর না-ই থাক, ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে প্রতিদিনই তার আড্ডা জমানো চাই।
আড্ডা? স্যার ভ্রু ভঙ্গ করেন। লতিফ সাহেব উৎসাহের সঙ্গে বলেন,
ওই হলো স্যার। আবৃত্তি, বিতর্ক- এসব করে তো কলেজ মাতিয়ে ফেলেছে। তাই তো বলি- বড়লোকের বউ, সামান্য এই প্রাইভেট কলেজে চাকরির জন্য...
লতিফ সাহেবের কথা শেষ হবার আগেই রাজিয়া অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে,
আমি তাহলে উঠি স্যার।
আচ্ছা।
রাজিয়া সংযত পায়ে রুম থেকে বেরিয়ে যাবার পর প্রিন্সিপাল সাহেব লতিফ সাহেবকে জিজ্ঞেস করেন,
রাজিয়া কি আপনার পূর্বপরিচিত?
কী বলছেন স্যার! আমাদের এলাকার মেয়ে। এক বছরের জুনিয়র হলেও ইউনিভার্সিটিতে তো পাশাপাশি ডিপার্টমেন্টেই কাটিয়েছি চার-পাঁচ বছর। খুব ভালো করেই চিনি ওকে।
বেশ ভালো। তবু কলেজে এসে বড়লোকের বউ-টউ বলার দরকার আছে?
কেন স্যার, আমি কি খারাপ কিছু বলেছি!
না না, বাসায় বসে যেটা বলা যায়, কলেজের পরিবেশে সেটা তো ভালো নাও লাগতে পারে।
কী মুশকিল, খুব কাছে থেকে আমি ওর সব ভালো দিক দেখেছি, সেইগুলোই তো প্রকাশ্যে বলি। তাতে যদি কেউ মাইন্ড করে তাহলে আর বলব না।
না বলাই ভালো। আপনার ক্লাস কোন পিরিয়ডে?
হাতের ঘড়ি দেখে লতিফ সাহেব ঝাঁপিয়ে ওঠেন,
স্যরি স্যার। পাঁচ মিনিট লেট হয়ে গেছে। এখনই যাই।
লতিফ সাহেব ক্লাস নেয়ার জন্য তড়িঘড়ি করে উঠে গেলে প্রিন্সিপ্যাল সাহেব চেয়ারের পেছনে হেলান দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকেন। চোখের চশমা খুলে রুমালে কাচ মোছেন। তারপর আবার চোখে দেন। হয়তোবা দূরের কোনো দৃশ্য তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকবে। তিনি ভাবেন, মানুষ কতদূর দেখতে পায়? প্রকৃতপক্ষে দৃশ্যমানবতার পরিধি কতদূর ব্যাপৃত হতে পারে, কতদূর? তারপর যেন তার মনে হয়- কে বলবে সেই কথা! মানুষে মানুষে কত না বৈচিত্র্য!
চার.
নতুন বাড়িতে এসে সব দিক মোটামুটি গুছিয়ে ওঠার পর রাজিয়া সুলতানা নতুন করে সাহিত্য চর্চার প্রতি মনোযোগ দেয়। বড় কোনো কবি-টবি হবার বাসনা তার বুকের গভীরে লুকিয়ে আছে কিনা সেটা খুব স্পষ্ট বুঝা যায় না। তবে কবিতা চর্চার নামে কুষ্টিয়া শহরের নানান বয়স ও নানান পেশার আরো অনেক মানুষকে একত্রে জুটিয়ে হৈচৈ করার মধ্যে সে খুব আনন্দ পায়, প্রাণ পায়। সেই আনন্দেই নভেম্বরের এক বিকেলে সংশপ্তকের ফুলবাগানের মধ্যে চমৎকার এক সাহিত্য আসরের আয়োজন করে ফেলে।
সত্যি বলতে কি, রাজিয়া সুলতানার এই সাহিত্য আসরে প্রেরণাবিন্দু হয়ে প্রধান চাবিটি ঘুরিয়ে দেন ড. আনোয়ারুল আবেদীন। কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক ছিলেন, শেষে মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে অবসর নিয়েছেন। সিংহ-হৃদয়ের মানুষ। বুকের সব ক’টা দরজা-জানালা হাট করে খুলে রাখেন সারাদিন সারাবেলা। নিজে কবিতা-গল্প-উপন্যাস সৃজনশীল শাখার কিছুই লেখেন না, কিন্তু অন্যকে উৎসাহ দেন প্রবলভাবে। তাঁর নিজস্ব অভিনিবেশের ক্ষেত্রে মননশীল প্রবন্ধ শাখা, লোকসাহিত্য, লোকসংস্কৃতি এবং লালন-দর্শনের চর্চা হচ্ছে তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। এসব নিয়ে বেশ কয়েকটি বইও বেরিয়েছে খুব মর্যাদার সঙ্গে। শোনা যায় তাঁর বই জার্মান নাকি জাপানি ভাষায় অনূদিতও হয়েছে। এতবড় পণ্ডিত, তার একটুখানি অহঙ্কারও নেই। উঁচুস্তরের চিন্তা এবং সাদামাটা জীবনযাপনে বিশ্বাসী তিনি। হাসতে জানেন প্রাণ খুলে। আপন ভাবেন সবাইকে। যারা তার সরাসরি ছাত্র নন, ভুল করে তাদেরও ছাত্র ভাবেন। একটুখানি শ্রদ্ধাভক্তি দেখলেই আবেগে-আনন্দে বিগলিত হয়ে পড়েন। এই তো কিছুদিন আগে এন এস রোডে বইমেলার সামনে রাজিয়াকে দেখেই উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ডেকে ওঠেন,
এই যে রাজিয়া, তুমি!
রাজিয়া ঘাড় ঘুরিয়ে স্যারকে দেখে সালাম দেয়। এগিয়ে এসে বলে,
একটা বই কিনতে এসেছিলাম স্যার। আপনার শরীর ভালো তো?
স্বভাবসুলভ হাসি ছড়িয়ে দেন আনোয়ারুল আবেদীন। তারপর নিজেকে নিয়েই তামাশা করেন,
আমার শরীরের কথা বলছ! কেন, হ্যান্ডসাম লাগছে না? শোনো মেয়ে, বুড়ো হচ্ছি না সহজে, হ্যাঁ!
মুখের বাক্য শেষ করেই হা হা করে উচ্চস্বরে হাসতে থাকেন ড. আনোয়ারুল আবেদীন। সেই কবেকার পুরাপতন শিক্ষককে আবারও নতুন মনে হয় রাজিয়ার। স্নিগ্ধ কণ্ঠে সে জবাব দেয়,
আপনি তো চির সবুজ স্যার। আপনাকে বুড়ো বলবে কে!
বেশ বলেছ যা হোক। তা কী বই কিনলে? কবিতার বই নিশ্চয়।
জি¦ স্যার, জয় গোস্বামীর কবিতা।
হ্যাঁ, তুমি নিজেও বেশ কবিতা লিখছ আজকাল।
আপনার নজরেও পড়ে স্যার?
আচ্ছা, আমাকে কী মনে করো- কবিতাবিমুখ নিরস মানুষ?
না, আমি ঠিক ওভাবে বলিনি। আমার আবার কবিতা!
নিজের উপরে আস্থা রেখো বুঝেছ? কবিতা ঠিকই হচ্ছে। কিন্তু নিজের নামটা বদলে ফেললে যে!
রাজিয়া ভীষণ লজ্জা পায়। দুচোখ নামিয়ে বলে,
সেটাও আপনার দৃষ্টি এড়ায়নি স্যার?
বেশ করেছ। ভারি কাব্যিক হয়েছে নামটা।
সত্যি বলছেন!
বাহ! সত্যি নয় তো কী! রয়ে রয়ে কেমন আদ্যানুপ্রাস হয়েছে রাজিয়া রায়হান!
আমাদের নতুন বাসায় আপনি একদিন আসুন স্যার। সেদিন কবিতা পাঠের আসর হবে। নিজে হাতে কফি বানিয়ে খাওয়াব।
বাব্বা! আমার তো এখনই যেতে লোভ হচ্ছে।
ঠাট্টা করছেন না তো!
এই দ্যাখো- কফি এবং কবিতা, দুটোরই লোভ হচ্ছে আমার।
কবে আসছেন স্যার- আগামী শুক্রবার?
যাব যাব। নিশ্চয় চলে যাব।
সেই থেকে যাত্রা শুরু সংশপ্তক সাহিত্য বাসরের।
আবেদীন স্যার একা আসেননি, তার সঙ্গে এসেছেন কুষ্টিয়া বিশ্বাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. মহিদুর রহমান, সাংঘাতিক বোদ্ধা মানুষ। এদিকে রাজিয়া নিজে থেকেই আরো ১০/১৫ জন সাহিত্যকর্মীকে আহ্বান জানিয়েছে। লালনগীতি গাওয়া দু’জন শিল্পীও আছে। সব মিলিয়ে বেশ জমজমাট আয়োজন। আনোয়ারুল আবেদীন ঠিক এতটা আশা করেননি। ফুলবাগানের মধ্যে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে শুরু হয় মৃত্তিকাসংলগ্ন মানুষের কবিতা। কবিতার পর কবিতা। আবারো কবিতা। হাততালি। ড. মহিদুর রহমান কখনো প্রশংসা করেন, কখনো উপমা-উৎপ্রেক্ষার সূক্ষ্ম প্রয়োগ নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করেন, আধুনিক কাব্যভাষার ভেতর দরজা খুলে ধরেন। রাজিয়া মুগ্ধ হয়ে শোনে, মাঝেমধ্যে চোখ তুলে তাকায় এবং দুহাতে কাজ করে। তারা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই অতিথি-আপ্যায়নে ব্যস্ত। ফল-মূল, ভাজাভুজি এবং কয়েক পদের মিষ্টি মিলিয়ে সে এলাহী কারবার। আবেদীন স্যার আনন্দের আতিশয্যে রায়হানকে বলেই বসেন,
এই যে জামাই বাবাজি! এটা কী হচ্ছে বলো দেখি!
কেন স্যার!
খুব বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?
ড. মহিদুর রহমান সরেশ ভঙ্গিতে যোগ করেন,
কবিতা শোনানোর নামে এ যে দেখছি অন্নপাপ!
রায়হান সলজ্জ ভঙ্গিতে বলে,
আপনারা এই প্রথম এখানে এলেন তো!
প্রথম মানে! মহিদুর রহমান বলেন- দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ... যতবার হোক, খবর পেলেই চলে আসব।
এমনকি ওরা না ডাকলেও এখানে আসা যায়, এমন চমৎকার পরিবেশে! তাই না মহিদুর সাহেব?
আবার সেই বিখ্যাত হাসি হেসে ওঠেন ড. আনোয়ারুল আবেদীন। হাসির ঢেউয়ে ভাসতে ভাসতে রাজিয়া রায়হান বলে ওঠে,
আপনারা অবশ্যই আসবেন। আমরা মাঝেমধ্যেই এভাবে বসতে চাই।
মাঝেমধ্যে কেন! আবেদীন স্যার বলেন, মাসে নির্দিষ্ট একটা দিনে নিয়মিতই বসা যাক। শুধু কবিতা কেন, সাহিত্যের সব শাখা নিয়ে আলোচনা হবে। গল্প, প্রবন্ধ সব...।
রাজিয়া যোগ করে,
গানও হবে স্যার। লালনগীতি।
হ্যাঁ! লালনগীতি? খুব খুশি হন আবেদীন স্যার, নিজেই হাত উঁচু করে গেয়ে ওঠেন- বাড়ির কাছে আরশিনগর, সেথা পড়শি বসত করে...
আনোয়ারুল আবেদীন এই রকমই। লালন প্রসঙ্গ উঠলে আর বাহ্যজ্ঞান থাকে না। নিজের কণ্ঠস্বরের মাধুর্য হারিয়ে গেছে, তবু ভাঙা গলাতেই গান ধরেন, লালনগীতির আপাতসহজ শব্দের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন, গূঢ় অর্থ মেলে ধরেন। এই একটি বিষয়ে তার উৎসাহের ঘাটতি নেই। এসব কথা খুব ভালো করেই জানে রাজিয়া। জেনে-শুনেই স্যারকে বলে,
আজও কিন্তু গান হবে স্যার। দু’জন শিল্পী আছে লালনগীতির।
এ্যাঁ! তাই নাকি!
ওদের গান না শুনে কিন্তু যাবেন না আপনারা।
মাথা খারাপ! কই গান ধরো...
সেই থেকে গানে-সাহিত্যে মাখামাখি হয়ে মাসের শেষ শুক্রবারে ঢাকা রোডের এই সংশপ্তকে জমে ওঠে প্রাণের জোয়ার। সেই জোয়ার তরঙ্গ অচিরেই আছড়ে পড়ে ছোট্ট এই শহরের পুবে-পশ্চিমে, উত্তরে-দক্ষিণে। ছোট-বড়, নতুন-পুরনো লেখকেরা অনেকেই যুক্ত হয়। সবাই জেনে যায় মাসের শেষ শুক্রবারের বিকেল মানেই সংশপ্তক সাহিত্য বাসরের নির্মল আড্ডা।
সুনির্দিষ্ট কোনো মাংগঠনিক রূপরেখা নেই, তবু এতগুলো মানুষ নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে নিয়মিতভাবে একত্রিত হলে তো সেটা সংগঠনই হয়ে ওঠে। কে সভাপতি, কে সাধারণ সম্পাদক এই সংগঠনের? না, ওসব কিছু নয়। উপস্থিত কবি-সাহিত্যিকের মধ্য থেকে সিনিয়র কাউকে সমন্বয়কের দায়িত্ব দিয়েই শুরু করা হয় সাহিত্য পাঠ ও পর্যালোচনার অনুষ্ঠান। ‘সংশপ্তক সাহিত্য বাসর’ নামকরণও হয়েছে দুটো কি তিনটি অনুষ্ঠান হয়ে যাবার পর। এই নামকরণ নিয়ে কথা উঠেছিল শুরুতেই। রাজিয়া পাত্তা দিতে চায়নি। যুক্তি দেখিয়েছে- নাম দিয়ে কি হবে, কাজটা হলেই হলো। সবার উদ্দেশ্য সাহিত্য পাঠ, সেটা যেন কিছুতেই ব্যাহত না হয়। এভাবে দু’হাতে ঠেলে প্রতিরোধের চেষ্টা করা হলেও শেষ পর্যন্ত নামকরণের প্রস্তাব মানতেই হয়। এ প্রসঙ্গ ওঠার পরপরই গোটা কতক নামও এসে যায়। সেই নামগুলো খারাপ কিছু নয়, যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। গ্রহণ করলেই হয় যে কোনো একটা। কিন্তু পণ্ডিতপ্রবর মহিদুর রহমান হঠাৎ এমন এক প্যাঁচ কষে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেন যে কারো মুখেই আর কথা সরে না। তিনি আঁকড়ে ধরেন রায়হান কবিরকে,
এত চমৎকার বাড়ির একটা নাম নেই?
সরাসরি এমন প্রশ্ন যেন আশাই করেনি রায়হান। এই নাম নিয়ে তো কম কেচ্ছা হয়নি। এত ঠেলাঠেলির পর যদিবা বাড়ির নাম স্থির হলো, তারপরও নিষেধাজ্ঞা- পাথরে লিখো না নাম। সেই কথা মনে পড়ায় বিরস মুখে রায়হান জবাব দেয়,
আপনাদের কবিকেই জিজ্ঞেস করুন। ইঙ্গিত করে রাজিয়াকে। সে তখন অতিথি আপ্যায়নে ব্যস্ত। তবু কান খাড়া করে, চোখের ভুরু কোঁচকায়।
বাড়ির একটা নাম থাকা দরকার নয়?
মহিদুর রহমানের এ প্রস্তাব প্রবলভাবে সমর্থন করেন ড. আনোয়ারুল আবেদীন। শুধু সমর্থন নয়, তিনি আরো একটু এগিয়ে ইঙ্গিত দেন,
হ্যাঁ, বাড়ির নামের সঙ্গে যুক্ত করেও আমাদের সাহিত্য সংগঠনের নাম ভাবতে পারি।
এবার ড. মহিদুর বলেন,
নিশ্চয়ই। তা তো হতেই পারে।
একজন উঠতি কবি অতি উৎসাহে বলেই ফ্যালে,
তাহলে আগে বাড়ির নামকরণই হয়ে যাক।
এই রকম প্রস্তাব শোনার পর রায়হান কবির অতি দ্রুত স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে,
কই বলো এখন কী বলবে, বলো!
আনোয়ারুল আবেদীন প্রথমে রাজিয়া এবং রায়হানের মুখের দিকে তাকিয়ে কী যেন বুঝার চেষ্টা করেন, কিন্তু কিছুই বুঝতে না পেরে বলেই ফ্যালেন,
কেমন যেন রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি মনে হচ্ছে।
মহিদুর রহমানও নাক উঁচু করে ঘ্রাণ শোকার ভঙ্গিতে বলেন,
জি¦ স্যার, আমারও মনে হচ্ছে ঢের রহস্য আছে।
রাজিয়া সুলতানা কার্পাসফাটা হাসি ছড়িয়ে এগিয়ে আসে,
রহস্য না ছাই। আমরা দুজনে একটা নামের কথা ভেবেছি। কিন্তু সেটা প্রকাশ করতে চাইনি।
সেই উঠতি কবি, নাম মামুন রেজা, হেসে উঠে বলে,
নাম তো প্রকাশের জন্যই। গোপন করবেন কেন?
মহিদুর রহমান রবীন্দ্রনাথের গানের কলি আওড়ান,
তোমার গোপন কথাটি সখি রবে না গোপনে...
স্বামীকে কপট ভর্ৎসনা করে রাজিয়া,
ভেজা বেড়ালের মতো চুপ করে আছ কেন? ফাঁস করে দাও তোমার বাড়ির নাম।
রায়হান কবির যেন ভারমুক্ত হবার আনন্দ খুঁজে পায়, দুহাত নেড়ে ঘোষণা করে, বাড়ির নাম সংশপ্তক।
উপস্থিত সবাই একযোগে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। বেশ ক’জন হাততালিও দিয়ে ফ্যালে। মামুন রেজা বলে,
ছিল শহীদুল্লাহ কায়সারের উপন্যাস, এবার হয়ে গেল কবি রাজিয়া রায়হানের বাড়ি। বেশ হয়েছে।
খুব ভালো হয়েছে। চোখ থেকে চশমা নামিয়ে আনোয়ারুল আবেদীন বলেন, আশীর্বাদ করি দু’জনেই জীবনযুদ্ধে জয়ী হও। এত সুন্দর নাম লুকাতে চাও কেন?
রাজিয়া ব্যাখ্যা দেয়,
লুকানো তো নয় স্যার, ভেবেছিলাম আমাদের দুজনের মধ্যেই থাক নামটা।
আনোয়ারুল আবেদীন হাসতে হাসতে বলেন,
ওটাকে এবার আমরা সার্বজনীন করে দিতে চাই।
বেশ ক’জন সমর্থন জানায়,
ঠিক স্যার।
উৎসাহ পেয়ে আবেদীন স্যার ঘোষণা দেন,
ছিল বাড়ির নাম, এখন থেকে হবে সাহিত্য সভার নাম।
মহিদুর রহমান বলেন,
সংশপ্তক সাহিত্য বাসর। নাম ঘোষণা করে নিজেই আপ্লুত হন খুশিতে, বলেন, ভালোই তো লাগছে শুনতে!
সবাই সমর্থন করে, খুব ভালো লাগছে।
আনোয়ারুল আবেদীন হঠাৎ করে এক প্রস্তাব দিয়ে বসেন,
সংশপ্তক সাহিত্য বাসরের আগামী সভা শিলাইদহে করলে কেমন হয়?
এ প্রস্তাব সবাই একবাক্যে মেনে নিলেও রাজিয়া মৃদু আপত্তি জানায়,
কেন স্যার, এ বাড়িতে অসুবিধা কী হলো?
না না, অসুবিধার কথা হচ্ছে না। নতুন নামে আবার নতুনভাবে যাত্রা শুরু হচ্ছে কিনা, তাহলে সেটা রবি ঠাকুরের কুঠিবাড়ির প্রাঙ্গণ থেকেই হোক না! ঠাকুরের আশীর্বাদও রইল আমাদের সঙ্গে। আবার আমরা ফিরে আসব সংশপ্তকে।
এরপর আর কারো আপত্তি করার কিছু থাকে না।
পাঁচ.
মানুষের জীবনে যা কিছু ঘটে, সব ঘটনার পেছনের কার্যকারণসূত্র কি মানুষ খুঁজে পায়? ব্যাকুল হয়ে আতিপাতি করে মানুষ সূত্র খোঁজে, খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়; কখনো মেলে, কখনো মেলেই না। তখন অসহায় দু’হাতে কেউ নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে উদ্যত হয়, কেউবা অন্যের কাঁধে দোষ চাপিয়ে নিজেকে ভারমুক্ত ভাবতে চায়। কিন্তু কাছে হোক, দূরে হোক, সব ঘটনার পেছনেই সত্যিকারের কার্যকারণ সূত্র একটা কিছু তো থাকেই।
শিলাইদহ কুঠিবাড়িতে সংশপ্তক সাহিত্য বাসরের অনুষ্ঠান শেষ করে বাড়ি আসার পর রাজিয়া অসুস্থ বোধ করে। কপালের শিরা দপদপ করে দাপায়। মাথা ধরে আসে যন্ত্রণায়। বেশ ক’দিন বন্ধ থাকার পর বমি বমি ভাবটাও গা গুলিয়ে ধেয়ে আসে। মুখে কপাট এঁটে কোনো রকমে বাড়ি পৌঁছানোর পর সে ধপাস করে বিছানায় শুয়ে পড়ে। কয়েক মিনিট পর আবার উঠে বসে। দৌড়ে বেসিনের সামনে গিয়ে ওয়াক ওয়াক করে বিবমিষা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। রায়হান কবির স্ত্রীর কপালে হাত রেখে শুধায়- এমন কেন হলো বলো তো!
স্ত্রীর চিকিৎসা কিংবা নিদেনপক্ষে সেবা শুশ্রুষাই যখন সবচেয়ে জরুরি, তখন রায়হানের প্রশ্ন শুনে মনে হতেই পারে তার কাছে কার্যকারণ সূত্র জানা ব্যতিরেকে বুঝি তার আর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণের সুযোগ নেই। রাজিয়া আকুল হয়ে হাত বাড়িয়ে বলে, এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি দাও না!
রায়হানের আগে কাজের মেয়ে পারুল এগিয়ে আসে
ফিরিজের পানি দেব খালাম্মা।
রাজিয়ার সারা মুখে ফুটে বেরোয় কষ্ট নিয়ন্ত্রণের কুঞ্চন রেখা। তারই মধ্যে সে বলে,
দে।
রায়হান ঠিকই গজর গজর করে,
নিজের বাড়িতে ছিল ভালো, রাধা নাচতে গেল ঠাকুরবাড়ি। কী দরকার ছিল এত নাচানাচির?
রাজিয়ার মুখে কথা নেই।
নাচানাচি শব্দটি কানের দরজায় খট করে দাঁড়িয়ে পড়ে। কান খোলাই থাকে। কেবল সে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। গতকাল দুপুরেই মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল রাজিয়ার। খুব জরুরি কাজে ড. আনোয়ারুল আবেদীনকে হঠাৎ ঢাকা যেতে হচ্ছে, প্রবল আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও শিলাইদহের প্রোগ্রামে উপস্থিত থাকতে পারছেন না বলে গভীর দুঃখ প্রকাশ করে খবর পাঠিয়েছেন। আবার সংশপ্তক সাহিত্য বাসরের সাফল্যও কামনা করেছেন। মন খারাপ হয়ে যায় রাজিয়ার। রায়হান তো অনুষ্ঠান বাতিলেরই প্রস্তাব দিয়ে বসে। কিন্তু সেও কি সম্ভব! অন্য সবাই তো ঠিকই হাজির হবে সময়মতো। কার্যক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। ড. মহিদুর তো কুষ্টিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আরো দুজন তরুণ অধ্যাপককেও সঙ্গে নিয়েছেন। আবেদীন স্যার না থাকায় একটা শূন্যতা প্রায় সবাই অনুভব করেছে, কিন্তু ঠাকুরবাড়ির আঙিনায় পৌঁছুনোর পর কবিতায় গানে আড্ডায় সেটা আবার ভরেও ওঠে। নদী সরে গেছে অনেক দূরে। কুঠিবাড়ির পশ্চিমে আছে শান বাঁধানো পুকুর। সেই পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে তরুণ অধ্যাপক মনিরুল হাসান তো চমৎকার একটি বক্তৃতাই করে শোনান। প্রসঙ্গ- রধীন্দ্রসাহিত্যে শিলাইদহের প্রভাব ও অবস্থান। সবাই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শোনে। সব শেষে সংগীত। জুলফিকার হায়দার পরিবেশন করে গগন হরকরার গান- ‘আমি কোথায় পাব তারে/আমার মনের মানুষ যে রে...।’ হুবহু এই মেঠো সুরটিই রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছেন আমাদের জাতীয় সংগীতে। কে এই গগন হরকরা? শিলাইদহ পোস্ট অফিসের ডাক হরকরা। কাজের ফাঁকে সুযোগ পেলেই জমিদার রবীন্দ্রনাথের কাছারিতে এসে গান শোনাতেন। চোখ বুজে শুনতেন রবীন্দ্রনাথ বাউলাঙ্গের এই সব গান। শুধু এক গগন হরকরা নয়, শোনা যায় ছেঁউড়িয়া থেকে লালন অনুসারী বাউলও দু’চারজন এখানে গান শোনাতে আসতেন।
শিলাইদহে এসে বিপাকে পড়েছিল রায়হান কবির। উপস্থিত সকলের অনুরোধ তাকে কবিতা পড়তে হবে। নইলে গান শোনাতে হবে। একটা কিছুতে অংশগ্রহণ করতেই হবে। নিজের বাড়ির অনুষ্ঠানে অতিথি আপ্যায়নের অজুহাতে নিজেকে আড়াল করার সুযোগ পেলেও লিশাইদহে সে অবকাশ মেলে না। ভয়ানক বিব্রত বোধ করে রায়হান। কবিতা বলো, গান বলো, এসব সুকুমার বৃত্তির চর্চার সঙ্গে তার কোনোরকম যোগ ছিল না কোনো কালেই। রাজিয়াকে ভালোবেসেই কবি এবং কবিতার কাছে আসা। তাই বলে এত মানুষের মধ্যে কবিতা পড়বে সে! মাথা খারাপ! অকপটে স্বীকার করে সে কবি-টবি কিছুই নয়, কবিদের ভালোবেসেই তার এখানে আসা। তাকে উদ্ধার করতে রাজিয়া এগিয়ে আসে, কাজ হয় না। যে কোনো একটি কবিতা তাকে শোনাতেই হবে। অবশেষে শৈশবে শেখা শিশুতোষ কবিতা তালগাছ একপায়ে দাঁড়িয়ে মুখস্থ শুনিয়ে তার রক্ষে। এতেই বেশ মজা পায় সকলে। করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানায়। কিন্তু রায়হান কবির এত মানুষের উপস্থিতিতেও এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা তালগাছের মতোই নিজেকে নিঃসঙ্গ নিরবলম্ব মনে করে।
কবিতা পাঠের সেই সময় থেকেই হয়তো রায়হান কবিরের বুকের ভেতরে অন্য রকম ভাঙচুর হয়। সবার আনন্দে সেও শামিল হবার চেষ্টা করে। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে হা হা করে হেসে ওঠে। শতেক জোড়াতালি দেবার পরও নিজেকে যেন কাকতাড়ুয়ার মতো নিঃসঙ্গ মনে হয়। রাজিয়া হয়তো দৃশ্যাতীত এই রক্তক্ষরণের ব্যাপারটা কিছুটা অনুভব করে থাকবে। তাই সেই কবিতা পাঠের পর থেকে বাড়ি ফেরা পর্যন্ত সে এক রকম দৃষ্টিকটু ভঙ্গিতে স্বামীর সান্নিধ্যে লেপ্টে থাকে। কথায় কথায় সমর্থন জানায়। তবু তার ভেতরের ক্ষরণ হয়তো নিঃশেষ মুছিয়ে দিতে পারে না। কিন্তু তাই বলে স্ত্রীর আকস্মিক অসুস্থতা টের পাবার পরও কেউ তার চোখের সামনে এভাবে প্রতিশোধের চাবুক ঘোরাতে পারে।
রাজিয়ার ভয় করে। গায়ে কাঁটা দেয়। ভয়ানক দুর্ভাবনা হয়- এ সব কিসের পূর্বাভাস! ভেতরে ভেতরে এত ওলোট-পালোট মনে হচ্ছে কেন! কোথাও খুব নিভৃতে কারো দীর্ঘশ্বাস পড়েছে কি? স্বমীর মুখের দিকে তাকানোর সাহস হয় না। ভারী হয়ে আসে চোখের পাতা। নিদ্রা নয়, তন্দ্রা নয়, অন্য এক অচেনা পাথর যেন দৃষ্টি আড়াল করে দাঁড়ায়। ভাবতে ভাবতে মাথার ভেতরে চক্কর দিয়ে ওঠে। আবারও তার বমনের ইচ্ছে হয়। অতিদ্রুত উঠে বসে বিছানায়। মুখে হাত চেপে ওয়াক ওয়াক করতে করতে বেসিনের কাছে ছুটে যায়। কিন্তু বমি করার বদলে তলপেটে হাত দিয়ে মেঝেতে বসে পড়ে। রায়হান ছুটে এসে দুহাত ধরে তুলে রাজিয়াকে বুকের মধ্যে জাপটে ধরে, প্রবল উৎকণ্ঠায় কেঁপে ওঠে তার কণ্ঠ,
কী হয়েছে রাজি! কী হয়েছে তোমার?
আবেগঘন মুহূর্তে রাজিয়াকে তার স্বামী ডাকে রাজি বলে। এত উদ্বেগের মধ্যেও কেন যে সেই মিষ্টি নাম মনে এলো কে জানে! কিন্তু রাজিয়া কোনো সাড়া দেয় না।
কী হয়েছে বলো!
রাজিয়ার মুখে তালা আঁটা
পেটব্যথা করছে?
ব্যথায় কুঞ্চিত চোখমুখ তবু সে মুখে বলে,
না।
তাহলে কী কষ্ট, সেটাই বলো।
পানি খাব।
পারুল দৌড়ে যায় পানি আনতে। রায়হান দুহাতে জাপটে ধরে রাজিয়াকে নিয়ে অসে বিছানায়। বালিশটা এগিয়ে এনে ধীরে ধীরে শুইয়ে দেয়। রাজিয়া শুয়ে পড়ে ঠিকই, কিন্তু চোখ মেলে তাকায় না। এক হাত উঁচু করে এমনভাবে কপালের উপরে বিছিয়ে দেয়, তাতেই দুচোখ আড়াল হয়ে থাকে। রায়হান চেষ্টা করেও সে হাত সরাতে পারে না। রাজিয়ার অন্য হাত তলপেটের জমিন আগলে রেখেছে। যেনবা বাইরের আঘাত প্রতিহত করার এটাও একটা চেষ্টা তার। রায়হান হাত বাড়ায়। রাজিয়া হাত শক্ত করে রাখে। জোর খাটাবার প্রবৃত্তি হয় না রায়হানের। আস্তে করে ডাকে,
রাজি!
এতক্ষণে কপালের উপরে ফেলে রাখা হাতটা একটুখানি সরিয়ে নেয় রাজিয়া। দুচোখের পাতা কেঁপে ওঠে। আর তখনই তার চোখ থেকে গড়িয়ে পড়া অশ্রুধারার প্রতি দৃষ্টি পড়ে রায়হানের। সে চমকে ওঠে।
এ কী, তুমি কাঁদছ!
হাতের তেলোয় চোখ মোছার চেষ্টা করে, কিন্তু মুখে কিছুই বলে না রাজিয়া।
উদ্বেগ বাড়ে রায়হানের। স্ত্রীর মাথার পাশে বসে শুধায়,
বলো না রাজি, কী হয়েছে তোমার?
রাজিয়া মুখ খোলে,
কিছু হয়নি।
এটা যে মোটেই সত্যিকারের জবাব নয় সেটা দুজনেই জানে। স্ত্রীর কপালে হাত রাখে রায়হান, পাঁচ আঙুলের চিরুনিতে বিলি কাটে তার চুলের অরণ্যে। আঙুলের ডগা ভিজে যাচ্ছে দেখে সে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলে,
তুমি তো ঘামছ দেখছি! দাঁড়াও মুছিয়ে দিই।
তোয়ালে আনার জন্য উঠতে উদ্যত হয় রায়হান। রাজিয়া তখন হাত বাড়িয়ে চেপে ধরে তাকে। রায়হান ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায়,
কিছু বলছ,
নাহ।
ডাক্তারকে খবর দেব?
না।
মুখে যতোই না বলুক, রাজিয়া যে যথেষ্ট অসুস্থ এটা বুঝতে মোটেই বাকি থাকে না রায়হানের। ভয় হয় রাত বাড়তে বাড়তে যদি অসুখ আরো বেড়ে যায়! রাজিয়ার শরীরের ভেতরে নতুন আরেক শরীরের উন্মেষ ঘটছে, তাদের দুজনের সংসারে আসছে নতুন অতিথি, তার যদি কোনো ক্ষতি হয়! ভাবনার এই প্রান্তে এসে রায়হানের বুকের ভেতরে তোলপাড় হয়। গীর্জাবাড়ির ঘণ্টা বাজে দূরে কোথাও। সেই ঘণ্টাধ্বনি অবিরাম প্রতিধ্বনিত হয় নিজের বুকে। চমকে উঠে সে ফিরে তাকায় রাজিয়ার মুখের দিকে। এত চেনা মানুষটিকে কখনো কখনো ভারি অচেনা মনে হয়। কাছে তবু দূরে মনে হয়। রায়হান যেন বহু চেষ্টা করেও তার নাগাল পায় না। এমন কথা শুনলে রাজিয়া হাসে, হেসে উড়িয়ে দেয়া। তখন রাযহানের মনে হয় সে যা বলতে চেয়েছিল, তা বুঝি বোঝানোই গেল না।
রাজিয়া কনসিভ করার পর ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া হয়েছে। ডাক্তার বলেছেন রেস্ট নিতে, সাবধানে থাকতে। খুব ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছেন, প্রথম তিন মাস কেন এত ঝুঁকিপূর্ণ। কোনো চিকিৎসা নয়, মেয়েদের সর্বোচ্চ সতর্কতাই হচ্ছে এ সময়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এসব কথা যে রাজিয়া মোটেই বোঝে না এমন তো নয়, আসল কথা হচ্ছে সব জেনে বুঝেও সে পাত্তা দিতে চায় না। সবকিছুতেই তার গা-আলগা ভাব। সতর্কতার বিষয়ে জোর করে চেপে ধরলে সে অবলীলায় বলে- বজ্র আঁটুনি মানেই কিন্তু ফসকা গেরো, বুঝেছ?
তাই বলে ডাক্তারের পরামর্শ মানবে না?
কত সহজ সরল জবাব তার,
কী মুশকিল, আমি কি রোগী নাকি!
রায়হান বুঝাতে চেষ্টা করে,
হ্যাঁ, রোগীই তো! এই সময়ে মেয়েরা রোগীই হয়ে যায়।
বাব্বা! ডাক্তারের চেয়েও বেশি বুঝে ফেলেছ দেখছি!
সেই তুমি যা-ই বলো, কলেজ থেকে ছুটি নাও।
ছুটি নাও বললেই হলো!
ঠিক আছে, প্রিন্সিপ্যাল স্যারকে না হয় আমিও রিকোয়েস্ট করব।
হ্যাঁ, সব জায়গার ঢাক পিটিয়ে দাও- আমি বাপ হতে চলেছি।
ঢাক পেটানো লাগবে না ম্যাডাম, ক’দিন পরে সবাই জানবে- তুমি মা হতে চলেছ।
এই ভালো হবে না বলছি!
মন্দটা কী হবে শুনি! রাজকুমার অসছে পতাকা উড়িয়ে, লোকে জানবে না?
রাজকুমার আসছে? তোমাকে বলেছে কানে কানে?
আহা, সে আমি রাজমাতার মুখ দেখেই বুঝেছি!
হ্যাঁ, খুব গণকঠাকুর হয়েছ তো!
সে তুমি দেখে নিয়ো।
রাজিয়া নির্মম তামাশা করে,
আমি তো বলছি খন্ডারনি আসছে। তোমাকে জ¦ালিয়ে পুড়িয়ে মাছভাজা করবে।
ক্ষেপে ওঠে রায়হান,
কী যা তা বলছ!
তাহলে রাজকুমারী আসছে বললে না কেন?
ওহ্। এই কথা! মুখে এলো না যে!
মুখে এলো না তো? হামাগুড়ি দিয়ে এসে যখন বুকের উপরে উঠবে, তখন টের পাবে।
এ তুমি কী বলছ রাজি!
বলছি মানে, সময় হোক- দেখে নিয়ো।
না, না আসুক সেই রাজকুমারীই আসুক। আপত্তি নেই। আমি যেন তার ছবিটুকু দেখতে পাচ্ছি।
এ্যাঁ! ছবি দেখতে পাচ্ছ?
হ্যাঁ, মনে হচ্ছে ছোট্ট পায়ে নূপুর বাজিয়ে নাচতে নাচতে এগিয়ে আসছে।
রাজিয়া হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে, হাসির মধ্যেই বলে,
তোমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে, তাই না?
হ্যাঁ, তাই তো মনে হচ্ছে।
ওরে বাব্বা! শুধু কবি নয়, ব্যবসায়ীও কল্পনাপ্রবণ হয় তাহলে!
এই ধাক্কাতেই বাস্তবে ফিরে আসে রায়হান। শক্ত হাতে চেপে ধরে রাজিয়াকে, সোজাসুজি বলে,
খুব ইয়ার্কি হয়েছে। এবার থামো।
অ। এতক্ষণ ইয়ার্কি হলো তাহলে!
না না, সিরিয়াসলি বলছি- তোমাকে ছুটি নিতেই হবে। রেস্টে থাকবে হবে।
মাথা খারাপ! ছুটি নেওয়া মানেই তো বাড়িতে বসে থাকা! তাহলে কিন্তু আমার দম বন্ধ হয়ে যাবে। তা ছাড়া, সত্যিই আমি এমন কিছু অসুস্থ হইনি।
বেশ। অসুস্থ হওনি। হতে কতক্ষণ?
এতক্ষণে রায়হান কবিরের মনে হয়- তাহলে তুমি সেই অসুস্থই হলে এতদিনে! কতবার কতভাবে বললাম, আমার কথা তো শুনলেই না। কলেজ তোমাকে কী দিয়েছে আর কী কেড়ে নিয়েছে সে হিসাব মিলিয়েছ কখনো? আহা! উনি না গেলে কলেজ অচল হয়ে যাচ্ছে। নবীনবরণ অনুষ্ঠান থমকে দাঁড়িয়ে পড়ছে! হায় রাজিয়া সুলতানা, এখন তোমার পাশে কে দাঁড়ায় বলো দেখি!
হ্যাঁ, রায়হানে প্রবল পীড়াপীড়িতে রাজিয়া কলেজে ছুটির দরখাস্ত পাঠিয়ে বাড়িতে বসেছিল সপ্তাহখানেক। সপ্তাহ না পেরোতেই স্বয়ং প্রিন্সিপ্যাল সাহেবই এক বিকেলে এ বাড়িতে হাজির। ভদ্রলোকের শিষ্টতাবোধ অসামান্য। শুনেছেন রাজিয়ার অসুখ। কী অসুখ সে বৃত্তান্তের গভীরে তিনি যাননি। রোগী দেখতে আসছেন, কাজেই আঙ্গুর-আপেল-কমলা ইত্যাদি নানান পদের ফলমূল বেঁধে নিয়ে আসেন। কণ্ঠে কন্যাপ্রতিম মমতা ঢেলে ডেকে ওঠেন- কই, আমার রাজিয়া সুলতানা?
রাজিয়ার তখন আকাশ থেকে পড়ার দশা।
স্যার আপনি এতদূর।
দূর কোথায়! অসুস্থতার কথা শুনে তো আরো আগেই আসা উচিত ছিল!
রাজিয়া বিব্রত বোধ করে। এদিকে রায়হান তখন বাসায় নেই। পারুলের সহযোগিতায় অতিথি আপ্যায়নের ব্যবস্থা করে। তারপর কথায় কথায় আকার ইঙ্গিতে তার অসুস্থতার ধরন সম্পর্কে ধারণা দিতেই আনন্দে আটখানা হয়ে হা হা করে হেসে ওঠেন স্যার। নিজের ডায়াবেটিসের কথা ভুলে গিয়ে মিষ্টি খাওয়ার আবদার জানান। ছুটি প্রসঙ্গে বলেন- সে তো মেটারনিটি লিভ তুমি নিশ্চয়ই পাবে। কিন্তু কলেজে ছেলেমেয়েরা যে ভারি এক ঝামেলায় ফেলেছে!
ঝামেলা বলতে আর কিছু নয়, কলেজের নবীনবরণ অনুষ্ঠান। নানা কারণে সে অনুষ্ঠান পিছাতে পিছাতে দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। আর বিলম্ব করা সম্ভব নয়। ছাত্রছাত্রীর সবার দাবি- তারা রাজিয়া আপার তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠান করতে চায়। কাজেই রাজিয়াকে এ দায়িত্ব নিতেই হয়।
বেশ ক’দিন আগে থেকেই ইংরেজির সেতাবউদ্দীনকে সঙ্গে নিয়ে ইতিহাসের লতিফ সাহেব কলেজের নবীববরণ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি শুরু করেছেন। সাংস্কৃতিক পর্বের জন্য ছাত্রছাত্রীদের রিহার্সেলের আয়োজনও হয়েছে। কিন্তু তারা শুরু করেছে গোয়ার্তুমি- রাজিয়া আপাকে চাই। প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের বিশেষ আহ্বানে রাজিয়া সুলতানা কলেজ আঙিনায় পা ফেলামাত্র তারা আনন্দে হইহই করে ওঠে। মেতে ওঠে অনুষ্ঠানের কার্যক্রমে। দেখেশুনে লতিফ সাহেব মন্তব্য করেন,
দেখেছেন সেতাব সাহেব, কীভাবে ছেলেমেয়েদের মাথা খাওয়া হচ্ছে?
সেতাবউদ্দীন অবশ্য আপত্তি জানান,
না না, ম্যাডামের কী দোষ! ছেলেমেয়েদের মধ্যে তার গ্রহণযোগ্যতাটুকু দেখবেন না?
আপনিই দেখুন ভাই। আমার অনেক কাজ আছে।
উঠতে উদ্যত হন লতিফ সাহেব। হঠাৎ রাজিয়া এসে বলে,
যাচ্ছেন কোথায় লতিফ ভাই?
তুমি এসে গেছ, আমার আর কী কাজ!
এটা কোনো কথা হলো! আপনারও অনেক কিছু দেখার আছে।
তুমি দ্যাখো সবদিক। আমি সাংবাদিক মানুষ, আমার কাজ বাইরে।
এরপর সত্যি সত্যিই লতিফ সাহেব নবীনবরণের বিশেষ কোনো দায়িত্ব পালন করেন না। তবু অন্য সবার সহযোগিতায় অনুষ্ঠান ঠিকই যথাসময়ে ভালোয় ভালোয় হয়ে যায়। ছাত্রছাত্রীদের প্রাণে নতুন সাড়া জাগে। আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করে কলেজ-জীবনের সকল অধ্যায়। কিন্তু চাঁদেও তো কলঙ্ক থাকে! সেই রকমই একটি অঘটন সবার অলক্ষে ঘটে যায় নবীনবরণের। লিজা নামে ফার্স্ট ইয়ারের একটি মেয়ে নাকি অনুষ্ঠানশেষে আর বাড়ি ফেরেনি। অভিভাবকরা নানান জায়গায় খোঁজ করেও তার সন্ধান পায়নি। পরদিন কলেজে এ নিয়ে বিস্তর কানাঘুষা শোনা যায়। লতিফ সাহেব স্থানীয় যে কাগজে সাংবাদিকতা করেন, সেই কাগজে এ ঘটনার গায়ে বিস্তর রঙ লাগিয়ে মুখরোচক সংবাদ ছাপানো হয়েছে। সেই সংবাদভাষ্য পড়ার পর কোরো মনে হতে পারে, এ ঘটনের জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ দায়ী। বিশেষভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে রাজিয়া সুলতানার প্রতি। নবীববরণের নামে বাংলা বিভাগের এই ম্যাডাম যেনবা ছেলেমেয়ের অবাধ মেলামেশাকে উৎসাহিত করেছেন এবং তারই পরিণাম হচ্ছে লিজার অন্তর্ধান।
হাওয়াশূন্য বেলুনের মতো নবীনবরণ অনুষ্ঠানের সব আনন্দ এক নিমেষে চুপসে যায়। খুব মন খারাপ করে রাজিয়া সুলতানার। লিজার চেহারা মনে পড়ে যায়। গায়ের রঙ শ্যামলা, তবু কী যে আলগা লাবণ্য ভরা মুখ! লালনগীতি গাইবে বলে নাম লিখিয়েছিল, অথচ যথাসময়ে তাকে পাওয়া যায়নি। অনেক গ্রাম্য ছেলেমেয়ে এ রকম করে। মঞ্চে উঠতে সাংঘাতিক ভয়। এই ভয়কে তো সবাই জয় করতে পারে না! যারা পারে তারা ঠিকই প্রতিভার স্ফূরণ ঘটিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয়। রাজিয়া ভাবে মঞ্চে ওঠার লজ্জা এড়াতেই সে বুঝি নিজেকে আড়াল করেছে। কিন্তু ওই কাগজঅলারা তো লোমহর্ষক কিডন্যাপের ইঙ্গিত দিয়ে সবার পিলে চমকে দিয়েছে!
কলেজের অনেকে ভাবে এবং বলাবলি করে- লতিফ সাহেব যেহেতু ওই কাগজের সঙ্গে যুক্ত আছেন, তিনি কি পারতেন না এই সংবাদের গতিমুখ একটু ঘুরিয়ে দিতে! এভাবে আকাশের দিকে থুতু ছুড়লে সে থুতু কোথায় পড়ে, সে হিসাব আছে তার? না, তিনি নির্বিকার। সাংবাদিকেরা নাকি এরকম নির্বিকার এবং নিরপেক্ষই হয়! হয়তো সে কারণে তার মধ্যে কোনো উদ্বেগই কাজ করে না। তারই কলেজের ছাত্রীকে জড়িয়ে নানান রকম কেচ্ছা ভাসছে হাওয়ায়, তিনি সে হাওয়া গায়েই মাখেন না। এমনই নির্লিপ্ত এবং নিরপেক্ষ সাংবাদিক আব্দুল লতিফ।
রাজিয়া সুলতানা অনেক অগে থেকেই চেনে এই লতিফ সাহেবকে। ভালো করেই চেনে। গায়ে পড়া স্বভাব। কাণ্ডজ্ঞানের অভাব। রাজিয়া চিরদিন ভদ্রোচিত দূরত্ব বজার রেখেই চলতে চেয়েছে। কিন্তু এলাকার মানুষ বলে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে খানিকটা গার্জেনগিরি ফলাতে চেয়েছেন লতিফ সাহেব। কে জানত যে কর্মজীবনে এসেও এই লোকটার মোকাবিলা করতে হবে!
ছয়.
অবশেষে সেই আশংকাই সত্যি হলো।
সেদিন মধ্যরাত গড়িয়ে যাবার পর দূরের আকাশ থেকে সবার অলক্ষে একটি তারা ঝরে যায়। কী নাম তার কে জানে- স্বাতী নাকি অরুন্ধতী! অথবা কে জানে সে অরিত্র কী না! কেউ জানে না রাতের বৃন্ত থেকে খসে পড়ে আলোর কুসুম। রাতজাগা কোনো পাখি সে রাতের স্তব্ধ প্রহরে সহসা সচকিত হয়ে ডেকে উঠেছিল কিনা- কে বলবে সেই কথা!
রাজিয়ার গোঁয়ার্তুমিকে এতটা পাত্তা না দিলেও পারত রায়হান কবির। কিছু হয়নি বলে নিজের কষ্ট রাজিয়া যতই আড়াল করার চেষ্টা করুক, রায়হান একটা বিপদের আশংকা ঠিকই করে এবং ফোন করে তার দূর সম্পর্কের মামাতো ভাই ডা. মিজানকে ডাকিয়ে আনে। কিন্তু ততক্ষণে সর্বনাশের আর বাকি থাকে না কিছুই। অবিরাম ব্লিডিংয়ের ফলে নেতিয়ে পড়েছে রাজিয়ার শরীর। ডা. মিজান এসে রোগীর পালস-টালস দেখে কয়েক মিনিটি গম্ভীর মুখে বসে থাকে চুপচাপ। রায়হান গভীর উদ্বেগের শুধায়,
চুপ করে আছিস কেন ভাই? অবস্থা কি খুব খারাপ?
খারাপ মানে! লাফ দিয়ে ওঠে ডা. মিজান,
ভাবী আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল, নাকি তুমিই হত্যা করতে চেয়েছিলে তাই ভাবছি।
এ সব কী বলছিস!
ঠিকই বলছি। ডা. মিজান হাত বাড়িয়ে দেয়,
নাও ধরো। ভাবীকে এখনই হাসপাতালে নিতে হবে।
চৈতন্যের ওপার থেকে এ সিদ্ধান্ত শুনতে পায় রাজিয়া। তখনো আপত্তি জানায়,
না।
ডা. মিজান ধমকে ওঠে,
তুমি থামো তো ভাবী!
রায়হানকে বলে,
কই, ধরো! হাত লাগাও। বউয়ের কথা শুনেছ কী মরেছ।
রাজিয়াকে ধরাধরি করে তুলে আনার জন্য রায়হান হাত বাড়ায়। ডা. মিজান তখনো গজগজ করে বকে চলেছে,
তোমরা মরতে চাইলে আলাদা কথা, তাই বলে তোমাদের যে উত্তরাধিকার আসছে, তাকেও মেরে ফেলবে?
নাটকীয়ভাবে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই একসঙ্গে চিৎকার করে ওঠে,
না।
কিন্তু না, তাদের এই প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর বেশিদূর পৌঁছুতে পারে না। দেওয়ালে দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসে আপন বিবরে। হাসপাতালের সাদা দেওয়ালে লেজ খসে পড়া একটি পেটমোটা টিকটিকি মুখ ভেংচিয়ে পালিয়ে যায়। ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডের পেশেন্ট বেডে শুয়ে রাজিয়া দাঁতমুখ খিঁচিয়ে কষ্ট নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে চলেছে। ডাক্তার-সিস্টার ডাকাডাকির সব দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে মিজান। স্ত্রীর কষ্টকুঞ্চিত মুখের ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় রায়হান এলোমেলো পায়চারী করছে। কী হয় কী হয় দুশ্চিন্তার শেষ নেই। ডা. মিজান ক্ষিপ্রহাতে একটা স্লিপ ধরিয়ে দিয়ে রায়হানকে বলে- গেটের সামনে মুন মেডিকেলে ইঞ্জেকশনটা পাও কিনা দ্যাখো তো দেখি।
ইমার্জেন্সি গেটের উল্টোদিকে মুন মেডিকেল খোলা থাকে দিবারাত্রি চব্বিশ ঘণ্টা। রায়হান দৌড়ে গিয়ে প্রয়োজনীয় ওষুধ ঠিকই নিয়ে আসে, ডা. মিজান হাত বাড়িয়ে সে ওষুধ গ্রহণ করে, কিন্তু বিমর্ষ মুখে সে বলেই ফ্যালে- ইট্স টু লেট।
কণ্ঠ কেঁপে ওঠে রায়হানের,
কী হলো মিজান?
অ্যাবরশন হয়ে গেছে।
কী বলছিস?
হ্যাঁ, তাও ইনকমপ্লিট অ্যাবরশন। এখন নানান কমপ্লিকেশন দেখা যাবে।
সাত.
সংশপ্তকে প্রাণের সাড়া নেই।
বাগানের গাছে গাছে ফুল ফোটে। দিবসের রৌদ্রদাহে তারা চোখ মেলে রাখে। বুঝিবা সারা রাতে তারা ঘুমোয় না। চোখের পাপড়ি মেলে জেগে থাকে। যদিবা কখনো তার দেখা পায়! এই যে সবিন্যস্ত পুষ্পবীথি, এই স্বপ্নগালিচা কে রচনা করেছে! কী সকালে কী সন্ধ্যায় প্রতিদিন কে এসে মমতামদির হাতের পরশ বুলিয়ে দিয়েছে পাতায় পাতায়। নিদ্রাহীন রাতে সে তো স্বামীকেও সঙ্গে নেয়নি, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে একা; শিশিরভেজা রজনীগন্ধার শিষে আঙুল ছুঁয়ে প্রশ্ন করেছে- এখনো ঘুমোস নি? জুঁই ফুলের ঝাড়ের কাছে দাঁড়িয়ে জানতে চায়- কোন নামটা তোর পছন্দ- যুথিকা না জুঁই? দুগ্ধধবল সেই ফুলের গায়ে হাত ছুঁয়ে বলে, বিলেতের সাহেবরা তো ডাকে জেসমিন নামে, জানিস? কিছুই জানিস না? কিছু না জেনেই বুঝি আপন মনে গন্ধ বিলিয়ে যাস? যুথিকা নয়, আমার কিন্তু যুথি নামটাই খুব পছন্দ। শুনেছি জন্মের পর আমার মা আমাকে যুথি বলে ডেকেছিল, কিন্তু সে নাম প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। বাঙালি মায়েরা তাই পারে নাকি। সংসারে মায়েদের কথার কীইবা মূল্য। আমার আব্বা নাম রেখেছেন রাজিয়া সুলতানা, সেটাই সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। পুরুষ মানুষের কথা, কে নড়চড় করবে। রাজিয়া এইভাবে সংগোপনে কথা বলে ফুলের সঙ্গে। সত্যি মিথ্যে যা-ই হোক, রাজিয়া দাবি করে, ফুলেরাও নাকি সুযোগ পেলেই তাকে গান শোনায়।
এসব দেখে শুনে রায়হানের মনে বিস্ময় জাগে, হয়তো অবিশ্বাসও হয়। তবু সে কথা সহজে প্রকাশ করে না। বরং আড়াল থেকে রাজিয়ার এই ছেলেমানুষি খেলা দেখতে ভালোই লাগে। মনে মনে সিদ্ধান্ত নেয়- আপন ভুবনে মগ্ন থেকে যদি সে আনন্দ পায় তো ক্ষতি কী! কাজ কী ধ্যানভঙ্গ ঘটিয়ে!
কোথা থেকে কী যে হয়ে গেল, পুষ্পপ্রিয় সেই মানুষ এখন অন্য ধ্যানে মগ্ন। ফিরেও তাকায় না তার সাধের ফুলবাগানের দিকে। কোথায় সেই ফুলের সঙ্গে আলাপচারিতা, কোথায় বা গান শোনা। ফুলেদের চোখে যে ফুটে ওঠার স্বপ্ন ছড়িয়ে দিত, তার স্বপ্ন যে এভাবে মুকুলেই ঝরে যাবে, কে জানত সেই কথা।
হাসপাতাল ছেড়ে আসার পর রাজিয়ার শারীরিক সুস্থতা ফিরে আসতে বেশ সময় লেগে যায়। কিন্তু মানসিক বিপর্যস্ততা যেন সে কাটাতেই পারে না। কলেজে যাওয়া বন্ধ। সংশপ্তক সাহিত্য বাসরেরও আপাতত বিশেষ খবর নেই। ফোন এলে ধরে না। কেউ দেখা করতে এলেও ভালো লাগে না। বাইরে কোথাও যাবার তো প্রশ্নই ওঠে না। নিজেকে এক রকম বিচ্ছিন্ন দ্বীপের বাসিন্দা করে তোলে রাজিয়া। স্বেচ্ছায় গৃহবন্দিও বলা চলে। কারো সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে না। এমন কি গান শুনতেও ইচ্ছে করে না। রায়হান কবির চোখের সামনে দেখতে পায় একজন মানুষের স্বেচ্ছানির্বাসন কেমন হয়।
এরই মাঝে কলেজ থেকে কয়েকজন সহকর্মী দল বেঁধে এক বিকেলে আসে রাজিয়ার সঙ্গে দেখা করতে। দেখা হয়, কিন্তু রাজিয়া তাদের সঙ্গে কথা বলতে মোটেই উৎসাহ বোধ করে না। সহকর্মীদের নানা রকম প্রশ্নের উত্তরে কেবল হ্যাঁ-না বলে দায় সারে। সেই বিকেলেই ডা. মিজান এসে তার ভাবীর সঙ্গে এ কথা সে কথা বলতে বলতে এক সময় সবার সামনে একেবারে ধমকানি দিয়ে ওঠে।
আমি বলছি তো ভাবী তোমার কিচ্ছু হয়নি। যা হয়েছে তা মেয়েদের জীবনে এক-আধবার হতেই পারে। তুমি একটু স্বাভাবিক হও দেখি।
অঘটনের পর থেকে একমাত্র মিজানকেই সহজভাবে গ্রহণ করে রাজিয়া। বয়সে দু’তিন বছরের ছোট, সম্পর্কে দেবর; বন্ধুর মতো সখ্য আগে থেকেই গড়ে উঠেছিল, বিপজ্জনক সেই রাত থেকে যুক্ত হয়েছে নির্ভরতাও। মিজান কথা বললে মনোযোগ দিয়ে শোনে, তার পরামর্শ মানতেও চেষ্টা করে। ডা. মিজানের কর্মস্থল কুমারখালী। পাস করে বেরুনোর পর প্রথম পোস্টিং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে। কুষ্টিয়া থেকে যাতায়াত করে। বিকেলে কুষ্টিয়াতেই একটু প্র্যাকটিস জমানোর চেষ্টা তার। কলেজ রোডের সেই চেম্বারে ঢোকার আগে অথবা চেম্বার থেকে বেরিয়ে রাত আটটা-নটায় ভাবীর খোঁজখবর নিয়ে যাওয়া তার রুটিনের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একদিনে গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে মেয়েদের গর্ভধারণ প্রক্রিয়ার শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা দিয়ে সে বুঝিয়ে বলেছে, অঘটন অঘটনই। অঘটন অনেকভাবেই হতে পারে। আবার নাও হতে পারে। গ্রামের মেয়েরা কত কঠিন পরিশ্রম করছে না। তারই মধ্যে গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব- কিছুই থেমে নেই। চলছেই। আবার খুব কেয়ারফুল থাকার পরও অঘটন ঘটতে পারে। কাজেই তোমার ক্ষেত্রে কলেজের ফাংশন বা শিলাইদহের অনুষ্ঠানই এ জন্য দায়ী, এমন ভাববার কোনো মানেই হয় না।
মিজানের কথা শুনে ভালোই লাগে। বাঁচার আশা জাগে। রাজিয়ার বুকের ভার অনেক হালকা হয়ে আসে। স্বামীর চোখের দিকে তাকাতে পারে। পারুলকে ডেকে বলতে পারে- ডাক্তারকে চা-নাস্তা দে। বিয়ের পর যখন জানতে পারে দেবর মিজান মেডিকেল-স্টুডেন্ট, তখন থেকেই রাজিয়া তাকে ডাক্তার বলে সম্বোধন করে। মিজান বহুদিন শুধরে দিয়েছে, ডাক্তার এখনো হইনি ভাবী, দু’বছর বাকি আছে। রাজিয়া তখন তামাশা করেছে, ক্ষমতা আমার হাতে থাকলে আমি এখনই সার্টিফিকেট দিয়ে দিতাম- আমাদের মিজান অনেক বড় ডাক্তার হবে।
সেই বড় ডাক্তার যখন সহকর্মীদের সামনে ধমকানি দেয়, তখন কোনো প্রতিবাদ করে না রাজিয়া, কেবল দু’চোখের কোণা বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে নীরবে। উপস্থিত সবার সামনেই সে হাত বাড়িয়ে দেয় স্বামীর হাতের দিকে। হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরে স্বামীর হাত। তারপর সবাইকে অবাক করে স্বামীর বুকে মাথা হেলিয়ে দিয়ে দু’চোখের পাতা বন্ধ করে ফ্যালে। মুক্তোদানার মতো দু’ফোঁটা অশ্রুবিন্দু গড়িয়ে পড়ে সেই বন্ধ পাতার ফাঁক গলিয়ে। ডা. মিজান তার ভাবীর সহকর্মীদের বুঝিয়ে বলে, আপনারা বিরক্ত হবেন না। আবার আসবেন। আপনারা মাঝেমধ্যে সঙ্গ দিলে মানসিক অবসাদ কেটে যাবে। আসবেন অবশ্যই।
প্রিন্সিপাল সাহেবও একদিন আসেন রাজিয়ার সঙ্গে দেখা করতে। রাজিয়া এবং রায়হান তখন নাস্তার টেবিলে। ডোরবেল বাজতেই পারুল গিয়ে দরজা খুলে দেয়। আর তখনই শোনা যায় গমগমে কণ্ঠের ডাক- কই, আমার রাজিয়া সুলতানা কোথায়? রায়হান উঠে গিয়ে জোর করে ধরে নিয়ে আসে প্রিন্সিপাল সাহেবকে। তিনি ড্রয়িং রুমেই বসেত উদ্যত হয়েছিলেন। কিন্তু রায়হান তাকে সোজা নিয়ে আসে ডাইনিং টেবিলে। রাজিয়াও অনেকটা সুস্থ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলে ওঠে,
খুব ভালো হলো স্যার আপনি আসাতে। আপনাকে দেখতে ইচ্ছে করছিল খুব।
রায়হান পারুলকে হুকুম করে,
নাস্তা দে পারুল। স্যার আমাদের সঙ্গে নাস্তা করবেন।
প্রিন্সিপ্যাল সাহেব না না করতে করতে উঠে দাঁড়ান। তিনি মেয়ের বাসা থেকে নাস্তা পর্ব সেরে আসছেন। কুষ্টিয়া শহরের আড়–য়াপাড়ায় মেয়ের বাসা। জামাই পাবলিক হেলথের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার। অল্প দিনেই তাদের প্রথম বাচ্চাকাচ্চা হবে। তাই নিয়ে প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের মিসেসের ব্যস্ততার অন্ত নেই। নাতিনাতনির মুখ দেখবার জন্য কোনো মানুষ যে এত উতলা হতে পারে সেটা নাকি টের পাওয়া যায় তার মিসেসকে দেখলে বা তার নানাবিধ তৎপরতা দেখলে। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব একা একাই গড়গড়িয়ে বলে যান হাজার কথা। বাঁধা ছাঁদার তো শেষ নেই। তারপরও একে একে যে জিনিসের কথা মনে পড়ে, অমনি মোবাইল ফোনে হুকুম চালান- যেখান থেকে পারো জোগাড় করে দিয়ে যাও, মেয়ে খাবে যে। গত রাতে প্রিন্সিপাল সাহেব এই রকমই এক বায়নার খেপ কাঁধে নিয়ে এসছিলেন মেয়ের বাসায়। রাত কাটিয়েছেন। এখন আরেক মেয়েকে দেখে কলেজে যাবেন। সোজাসুজি জানিয়ে দেন- নাস্তা খাবেন না, খাবেন এক কাপ চা।
আচ্ছা, আপনি তাই খাবেন স্যার। রায়হান বলেন, পারুল, চা দে।
প্রিন্সিপাল সাহেব তাগাদা দেন,
তোমাদের নাস্তা সারা হয়নি তো। কী মুশকিল।
আপনি আমার সামনে বসে থাকুন স্যার। আমি আপনাকে দেখি।
পাগলি মেয়ের কথা শোনো। আমি তো বসেই আছি। তোমরা খাও।
খালাম্মা আর কী বলে স্যার?
প্রথম মেয়ে তো! খুব সাধ আহ্লাদ এই আর কী!
একদিন খালাম্মাকে নিয়ে আসবেন আমাদের বাসায়?
আচ্ছা সে দেখা যাবে পরে।
দেখা যাবে কেন স্যার, আপনি কথা দিন, খালাম্মাকে নিয়ে আসবেন।
প্রিন্সিপাল সাহেব একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে যান। রাজিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে কী যেন হিসাব কষেন। তারপর জোর দিয়ে বলেন,
বরং তোমাদের খালাম্মা ফিরে আসুক। তোমরাই আমার বাসায় এসো একদিন। সারাদিন কাটাও। আনন্দ কর।
রাজিয়া আবদার জানায়,
আমি আগে দাবি করেছি। আমার কথাই আগে শুনতে হবে স্যার।
কাঁপা কাঁপা হাতে চায়ের ট্রে নিয়ে আসে পারুল। রায়হান চায়ের কাপ পিরিচ তুলে নিয়ে নিজে হাতে বাড়িয়ে ধরে বলে,
ওর কথাই মানতে হবে স্যার। ওর সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য মা-খালা কেউ পাশে থাকলে খুব ভালো হয়।
প্রিন্সিপাল সাহেব দীর্ঘশ্বাস আড়াল করতে চান। চোখের চশমা খুলে আবারও পরেন। আশ্বস্ত করেন,
বেশ তাই হবে।
চা-পর্ব শেষে বিদায় নেয়ার সময় গেটের কাছ থেকে আবারও ফিরে আসেন। রাজিয়ার মাথায় হাত রাখেন। কী যেন বলতে চান। বেশ দু’বার ঢোক গেলেন। কী যে বলতে চান, সেটা যেন গুছিয়ে উঠতে পারেন না। অগত্যা তিনি যেন কথার কথা বলছেন এমনই ভঙ্গিতে বলেন- কলেজে তো ইন্টার্নাল পরীক্ষা শুরু হচ্ছে ২৫ তারিখ থেকে, এখন আর একদিন কলেজে না গেলেও চলবে। তুমি আগে সুস্থ হয়ে ওঠো মা।
প্রিন্সিপাল সাহেব ধীর পায়ে বেরিয়ে যান সংশপ্তক থেকে।
রাজিয়ার সঙ্গে তার বয়সের তফাৎ ঠিক পিতৃতুল্য নয় হয় তো, তবু ওই মানুষটির স্নেহপ্রবণ অন্তরের পরিচয় পাবার পর তার কাছে নত না হয়ে কিছুতেই পারে না। কেমন করে যেন বুক নিংড়ানো শ্রদ্ধা আদায় করে নিতে জানেন। রাজিয়া ভাবে আমারও যদি মা কিংবা শাশুড়ি বেঁচে থাকতো তাহলে কি প্রিন্সিপাল খালাম্মার মতো পাহারায় বসে যেত। বাঙালি নারী রসগোল্লা এবং রসগোল্লার ঝোল- দুই-ই ভালোবাসেন। নাতি-নাতনি মাত্রই তাদের কাছে রসের ভাঁড়ার। মা এবং শাশুড়ির কথা ভাবতে ভাবতে তার মনে হয়- তারা দুজনই কি আগেভাগে টের পেয়েছিলেন, এই অপয়া মেয়েকে দিয়ে তাদের নাতি-নাতনির আশা পূরণ হবে না? মায়েরা অনেক কথা আগাম টের পায়, এই অলক্ষুণে অঘটনের পূর্বাভাস কি টের পাননি তারা? খুব টের পেয়েছেন। টের পেয়েছেন বলেই তো এভাবে নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছেন। নইলে কি দু’জনকেই এভাবে চলে যেতে হয় এমন মাতৃহীন করে?
প্রিন্সিপাল সাহেব চলে যাবার পর রাজিয়ার বুকের ভেতরে আবার ধস নামে। আবার অন্ধকারে ছেয়ে যায় তার নিজস্ব ভেতরবাড়ি। আবার অবসাদে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে দেহমন। খুব ভয়ে ভয়ে রায়হানের মুখের দিকে তাকায়। চোখের ভেতরে চোখ রেখে তার চোখের ভাষা পড়তে চেষ্টা করে। তারপর দু’হাতে গলা জড়িয়ে ধরে বলে ওঠে, আমার ভালো লাগছে না সোনা, একটুও ভালো লাগছে না।
এত দ্রুত যে একটা মানুষের মনোজগতে পরিবর্তন ঘটতে পারে, এ কথা ভেবে ওঠাই মুশকিল। রৌদ্র-মেঘের এ কী লুকোচুরি। প্রিন্সিপাল স্যার রোদ্দুরে স্নান করে বেরিয়ে গেছেন, তিনি এই সঘন মেঘ কিংবা এই বর্ষণের কী জানবেন? স্যার চলে যাবার পর পরই রায়হানের বুকে মাথা রেখে ডুকরে ওঠে রাজিয়া, শুরু হয় অশ্রুপাত। কত আর সান্ত¡নার কথা শোনাবে। প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের উপস্থিতি যেটুকু আশা জাগিয়েছিল মনে, সহসা এই ভেজা হাওয়ার দমকে তাও যেন নিভে যাবার উপক্রম হয়। তখন কী করে রায়হান। স্ত্রীর মাথায় হাত রেখে সে মমতামাখা কণ্ঠে বলে,
তুমি একটু স্বাভাবিক হও রাজিয়া, সহজ হও।
রাজিয়া ফুঁপিয়ে ওঠে। রায়হান চোখ মুছিয়ে দেয়।
জীবন তো এখানেই থেমে থাকবে না, তোমাকে নতুন করে বাঁচতে হবে।
এতক্ষণে মুখ খোলে রাজিয়া,
বাঁচব আমি কিসের আশায়।
তুমি সহজভাবে গ্রহণ করলেই জীবন আবার সহজ হয়ে যাবে; দেখো।
বুক থেকে মাথা তুলে এবার সোজাসুজি তাকায় রাজিয়া, বলে,
কোনোদিন আমার যদি আর সন্তান না হয়, তুমি সহজভাবে নিতে পারবে?
কে বলেছে সন্তান হবে না?
আমি জানি, হবে না।
মিজান বলেছে এই কথা?
সে তো দিনরাত মিথ্যে সান্ত¡না দেয়। তার কথা বাদ দাও।
তাহলে কার কথা নেব? তুমি কোথায় পেয়েছ এই তথ্য?
হাসপাতালে ডি এ্যান্ড সি করার সময় আমি শুনেছি। অনেকে বলাবলি করছিল। অনেকের কথা না শুনে ডাক্তারের কথা শোনো। কী বলেছে গাইনির ডাক্তার? আমার কান খোলা ছিল। আমি কিন্তু জ্ঞান হারায়নি। সব শুনতে পাই, বুঝেছ?
কী শুনেছ বলো!
শুনেছি।
বেশ, কী শুনেছ তুমি?
আমি সত্যি বলছি, কিন্তু তুমি সত্যি বলবে তো!
এ আবার কী কথার ধরন!
না না, বলো সত্যি বলবে?
মিথ্যে কেন বলব! বলো কী শুনেছ!
একটুখানি সময় নেয় রাজিয়া। তারপর স্বামীর ডান হাত নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে আদর করতে করতে সে বলে,
আমাকে রক্ত দেবার সময় জটিলতা দেখা দেয়নি?
রায়হান যেন একটুখানি ইতস্তত করে, উত্তর সাজাতে একটু বিলম্বও হয়ে যায়, না, মানে ব্লাডের গ্রুপ ম্যাচিংয়ের সময় কী যেন একটু...
ওই তো, আমার শরীরে এই রক্ত থাকতে আর কখনোই...
বাজে কথা বোকো না তো!
আচ্ছা। আমি চুপ করে থাকলেও যেটা সত্যি সেটা তো ঘটবেই।
ঘটুক। যখন ঘটবে তখন দেখা যাবে।
রাজিয়া আর কোনো কথা না বাড়িয়ে বিছানায় গিয়ে বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ে। রায়হান বুঝতে পারে যেখান থেকে যে কথা শুনেই হোক রাজিয়ার আতঙ্কিত মনে এখন আশঙ্কার পাথর জমেছে, আপাতত কারো যুক্তিই সে পাথর গলাতে পারবে না। হয়তো রায়হানের সব কথাই তার কাছে মিথ্যে আশ্বাস মনে হচ্ছে, তাই এসব কথাই সে বাহুল্য বিবেচনা করছে।
রায়হান তবু পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে বিছানার কাছে। রাজিয়ার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়, তার শরীর ফুলে ফুলে উঠছে, সে নিঃশব্দে ফুঁপিয়ে চলেছে। ধীরে ধীরে বিছানার একপাশে বসে পড়ে রায়হান। স্ত্রীর পিঠে মমতার পরশ বুলিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। হাত বাড়িয়েও সে আবার ফিরিয়ে আনে হাত, যদি বিরক্ত হয় রাজিয়া। উঠে আসে বিছানা থেকে। রাজিয়ার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে সে জানায়,
একটা কথা তোমাকে বলা হয়নি রাজিয়া। তোমাদের সাহিত্য বাসরের বেশ ক’জন সদস্য তোমাকে দেখতে এসেছিল গত দুদিনে। আমি তাদের ফিরিয়ে দিয়েছি, পরে আসতে বলেছি।
রাজিয়া হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে,
কেন বলেছ আসতে। কাউকে আসতে হবে না।
আমিও তাই চাই। কিন্তু ওরা যে আসবেই।
আচ্ছা আসুক। ওদের মুখের ওপর বলে দেব- আমি আর কবিতা টবিতা লিখব না। সেই ভালো। কী লাভ কবিতা লিখে।
রাজিয়া আবার বালিশে মুখ গুঁজে দেয়। আবার ফুঁপিয়ে ওঠে।
বড্ড রহস্যময় মনে হয় রায়হানের। আর কী বলবে এই মহিলাকে। কী বলে বুঝানোর চেষ্টা করবে? আপন মনেই সে বিড় বিড় করে- কবিতা না লিখলে কী হয়! যারা কবিতা লেখে না, তারা কি বাঁচে না? নাকি তারা মানুষ নয়? যত্তোসব আগডুম বাগডুম কল্পকাহিনী। কী হয় ও সব ছাইপাশ না লিখলে। রবীন্দ্রনাথ হতে চায়। হুঁ!
তুমি থামবে!
নড়ে চড়ে ওঠে রাজিয়া। দুচোখে অশ্রুজলের মাখামাখি। তারই মধ্যে সে জানিয়ে দেয়, কবিরা কবিতা না লিখলে বাঁচে না। তুমি সেটা বুঝবে না।
আট.
রাত আটটার পর আর কোনো রোগী না থাকায় ডা. মিজান চেম্বার থেকে বেরিয়ে একটা রিকশা ধরে চলে আসে সংশপ্তকে। তার মুড যথেষ্ট ফুরফুরে। পরপর দুদিন সে এ বাড়িতে আসেনি বলে ভেতরে ভেতরে একটুখানি অপরাধবোধ জমেছিল বটে, কিন্তু বাড়িতে ঢুকেই উঁচু গলায় ভাবীকে ডাকতে ডাকতে তার সেই বোধ শূন্য উড়িয়ে দেয়। ডাক্তার মানুষ, রোগীর ভালোমন্দ জিগ্যেস করবে কি কিছু, তা না করে সোজা ভাবীর সামনে এসে বিচিত্র এক প্রশ্ন করে,
আলতাছুনু মানে জানো ভাবী?
এমন বিদঘুটে শব্দ সারা জীবনেও কখনো শুনেছে বলে মনে পড়ে না রাজিয়ার। চোখ গোল গোল করে সে জানতে চায়,
কী মানে?
হা হা করে হাসতে হাসতে রায়হান আবারও বলে,
আলতাছুনু। শুনেছ কখনো?
রাজিয়া হাঁ করে শোনে। একটি নয়, তার কাছে মনে হয় দুটি শব্দ একত্রে গেঁথে উচ্চারণ করা হচ্ছে। আলতা এবং স্নো এক সঙ্গে মিশে গ্রাম্য উচ্চারণে হয়তো ওই রূপ পেয়েছে। সে সরল চিত্তে বলে ফেলে,
হ্যাঁ, শুনেছি তো।
শুনেছ!
আমরা গ্রামের মেয়ে, শুনব না কেন! কত শুনেছি।
তাহলে আলতাছুনু মানে বলো!
কী মুশকিল! আলতা মানে পায়ে পরা আলতা। গ্রামের মেয়েরা...
রাজিয়ার এ বিবরণ শেষ হবার আগেই ডা. মিজান অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। যেনবা নিজে হেসে হেসে ভাবীকে হাসাবার জন্য একটা জোর প্রস্তুতি নিয়েই সে বাসায় এসেছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে নিজের হাসি তার ঠিকই হচ্ছে, এত চেষ্টা করেও ভাবীর মুখে হাসি ফুটছে না। বরং সে অবাক হয়ে জানতে চায়,
এত হাসির কী হলো!
আমি তো আলতা মানে জানতে চাইনি ভাবী, আমি বলেছি আলতাছুনু...
ওই হলো। গ্রাম্য উচ্চারণে স্নো অনেক সময় ছুনু হয়ে যায়। এই আলতাছুনু।
মিজান আবারও হাসে। দেখে মনে হবে কে যেন আড়াল থেকে সুড়সুড়ি দিচ্ছে, তাই তার হাসি কিছুতেই ফুরাচ্ছে না। এমনকি সংক্রমিত করছে অন্যকেও। পারুল এসে হাসির বহর দেখে নিজেও হাসতে হাসতে কিচেনে ঢুকে পড়ে। এদিকে কিছু না বুঝেও রায়হান এসে দিব্যি হাসিতে যোগ দেয়। হাসতে হাসতেই বলে,
কী হয়েছে বল তো দেখি!
একটুও দেরি না করে মিজান এবার তার ভাইকেই বলে,
আলতাছুনু মানে জানো?
আলতাছুনু?
আবার হাসি। একেবারে গড়িয়ে পড়া হাসি। রাজিয়া কপট ক্ষোভ ঝাড়ে, তা আলতাছুনুর কী হয়েছে বলবে তো!
তুমি তো ওই শব্দটার কোনো অর্থই ধরতে পারোনি, তোমাকে কী বুঝাব?
রায়হান ধমকে ওঠে,
তোর মেডিকেল টার্মের শব্দ হলে আমরা কী করে বুঝব!
যাক তুমি তো তবু মেডিকেল টার্ম পর্যন্ত গেলে, আমি তো প্রথমে তাও পারিনি। ভেড়ামারা থানার এক রোগীর কাছে আজ শিখলাম, আলতাছুনু মানে হচ্ছে আলট্রাসনো।
এ্যাঁ!
রায়হান এবং রাজিয়া দুজনেই বিস্মিত হয়। দুজনেই এক সঙ্গে হেসে ওঠে। রায়হান বলেই ফ্যালে- এতক্ষণে এই কথা!
মজার গল্প শোনো ভাই। বৃদ্ধা এক রোগী পেয়েছিলাম আজ। সে তার রোগের কথা বলবে কী, রাজ্যের গল্প জুড়ে দেয়। বৌদের গল্প, মেয়েদের গল্প। তার মেজ মেয়ের পেটে বারবার কন্যা সন্তান জন্ম নিচ্ছে দেখে জামাই বাবাজি আবার একটা বিয়ে করেছে। সেই মেয়ের এখন চলছে ছয় মাসের গর্ভ। আলতুছুনু করে জেনেছে সেই গর্ভেও আসছে কন্যাসন্তান। বুড়ির সে কী আনন্দ- শুধু আমার মেয়ের দোষ, ক্যামুন! আলতাছুনু কইরে দ্যাখো গা, দোষ কার!
চমৎকার এই হাসির গল্পটি শোনার পর রাজিয়া আর হাসতে পারে না। তার মুখের মানচিত্র থেকে ঝলমলে রোদ্দুর সরে যায়। কালো মেঘে ছেয়ে যায় সুনীল আকাশ।
বিষণ্ন মুখে সে মিজানের দিকে তাকিয়ে জানতে চায়,
আচ্ছা মিজান, তিন মাসের মধ্যে কি কিছুই জানা যায় না?
অনেক কিঝুই জানা যায়।
ডা. মিজান এই বাক্যটি বলার পর রাজিয়া ভাবীর চোখেমুখে কী যেন জরিপ করে। কী খোঁজে আর কী যে বোঝে সে-ই জানে। একটু পরে সাহস করে বলেই ফ্যালে, জানা যায়। তবে তুমি যা জানতে চাও, সেটা জানা যায় না।
যায় যায়, জানা যায়। আমি ঠিকই জানি।
কী জানো তুমি?
তোমার ওই আলতাছুনু মেশিনে যা জানে না, আমি তাও জানি।
তা জানতেও পারো। মেয়েদের থার্ড আই থাকে যে!
আমি খুব ভালোই জানি, দিগি¦জয়ী বীরের মতো রাজকুমার আসছিল। আমার অনাদরে, আমারই অবহেলায় সে ফিরে গেছে।
কথা বলতে বলতে শেষের দিকে গলা ধরে আসে রাজিয়া সুলতানার। গলা ভিজে আসে অবদমিত কান্নায়। রায়হান এগিয়ে এসে তার পাশে বসে। হাতের উপরে হাত রেখে সে অনুনয় করে ওঠে,
তুমি থামো তো রাজি! সহজ হও।
দুচোখের কোণা মুছে রাজিয়া শান্তস্বরে বলে,
আচ্ছা থামছি। কিন্তু তুমি বলো তো ডাক্তার, অনাদরে যে মুখ ফিরিয়েছে, সে কি আর ফিরে আসবে!
ডা. মিজান অবলীলায় জানায়, আসবেই তো!
মিথ্যে বলো না ডাক্তার! ভাবীকে খুশি করতে গিয়ে চিকিৎসাশাস্ত্রকে খাটো করো না। আমি জানি, এই শরীরে আর সন্তান ধারণ সম্ভব নয়।
শোনো ভাবী, এ কথা চূড়ান্তভাবে বলার সময় এখনো আসেনি।
এতক্ষণে রায়হান তার ভাইকে বলে,
তোর ভাবী কোথায় কী শুনেছে, এখন এই এক গাওনা শুরু করেছে। ঘটনা কী বল দেখি মিজান?
ডা. মিজানা প্রথমে চুপ করে থাকে। তারপর ভাবীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, এমন গুরুত্বপূর্ণ কথা তুমি কোথায় শুনলে ভাবী?
রাজিয়া এবার শক্ত করে চেপে ধরে দেবরকে।
সত্যি কথা বলো ডাক্তার- আমার রক্তে সমস্যা নেই?
মিজান হো হো করে হেসে বলে, বাপরে বাপ গ্রেট হেমাটোলোজিস্ট হয়ে গেছ দেখছি!
না না ঠাট্টা নয়, তুমি সত্যি করে বলো। সমস্যা নেই?
সমস্যা না ছাই! কুষ্টিয়ার রিপোর্টের উপরে ভরসা করা যায়?
রিপোর্ট তাহলে ভালো না, এই তো?
মিজান এবার বিরক্তির সঙ্গে বলে,
দ্যাখো ভাবী, রোগদের এত বেশি না জানাই ভালো। কে বলেছে তোমাকে, এ সব কথা?
তোমরাই বলা-কওয়া করছিলে সেই রাতে, আমি শুনেছি।
আচ্ছা, তোমরা হচ্ছো নন্মেডিকেল পারসন, আমাদের সব আলোচনা বুঝবে? স্বামী-স্ত্রী দুজনেই বেশ জব্দ হয়। দুজনেই চুপ করে থাকে। এই সুযোগটা গ্রহণ করে ডা. মিজান। বেশ গুরুগম্ভীর ভঙ্গিতে দুজনকে উদ্দেশ্য করেই বলে- আমি যতক্ষণ আছি, আমার উপরে ভরসা রাখো। যখন যেটা জানাবার, আমি নিশ্চয় জানাব, বুঝেছ?
ছোটভাইয়ের বকুনি খেয়ে দু’জনেই চুপ। কারো মুখে কথা নেই। পরিবেশটা বেশ গুমোট হয়ে যাচ্ছে দেখে মিজান একেবারে ভিন্ন প্রসঙ্গ উত্থাপন করে,
আচ্ছা ভাবী, তোমার সেই সাহিত্য সংগঠনের কী হয়েছে বলো তো!
রাজিয়া সুলতানা এতক্ষণে মুখ খোলার সুযোগ পায়, সহজ ভঙ্গিতে বলে, কী আবার হবে! আমরা তো প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে বসি। সে তো এখনো দেরি আছে। আজ কয় তারিখ?
না না, সে নিশ্চয় দেরি আছে। কিন্তু আমি শুনলাম- ওই সংগঠনের কাউকে নাকি এখানে আসতেই দেওয়া হচ্ছে না। সংগঠন তো তাহলে ভেঙে যাবেই!
তুমি এ সব কোথায় শুনেছ?
এইটুকু শহর। কথা তো কানে আসেই। দুজন তরুণ কবি খুব দুঃখ করছিল। তোমার দেখা না পেয়ে তারা খুব কষ্ট পেয়েছে মনে হলো।
রাজিয়া সুলতানার কানের লতি গরম হয়ে ওঠে। ভেতরে ভেতরে খুব বিব্রত বোধ করে। স্বামীর দিকে দুচোখ তুলে তাকিয়ে প্রশ্ন করে,
ওদের তাহলে তাড়িয়ে দিয়েছ?
না না, তোমার শরীর খারাপ। তাই তাদের পরে আসতে বলেছি।
ভালোই করেছ। কবিদের অভিমানের তুমি কী বুঝবে!
তারা আবার আসবে, দেখো।
বিষণ্নতায় ছেয়ে যায় রাজিয়ার সারা মন। দুই ভাইয়ের কারো সঙ্গেই আর কথা বলতে ইচ্ছে করে না তার। সে উঠে দাঁড়ায়। দুপা বাড়ায়। আবার মুখ ঘুরিয়ে জানতে চায়,
আবেদীন স্যার ফিরে যাননি তো!
মাথা খারাপ! তুমি আমাকে কী ভেবেছ বলো তো!
না, কিছুই ভাবছি না তোমাকে। তবে ভাবছি। আমার মরে যাওয়াই ভালো।
কী মুশকিল! আবেদীন স্যার তো এখনো ঢাকা থেকেই ফেরেননি! তুমি ঠিক জানো?
অবশ্যই জানি।
তাহলে ফোন দাও। আমি ফোনে কথা বলব।
রায়হান ফোন এনে হাতে ধরিয়ে দেয়। মিজান ঝট্ করে উঠেই পড়ে। কথায় কথায় রাত হয়ে গেছে অনেক। উঠবার সময় সে পরামর্শ দেয়- সবার সঙ্গে মেলামেশা, কথা বলা, গল্প করা, ভাবীর জন্য এ সবই ভালো। তার মনটা ভালো থাকবে। মনটা ঝরঝরে হলে শরীরটাও হালকা লাগবে।
ডা. মিজান ভাবীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে আসে। বাগানে পা ফেলার পর মনে হয়, এতটা বকাবকি করাটা কি ঠিক হলো! ভাবীর শারীরিক সংকট যদি মানসিক অসুস্থতার দিকে গড়িয়ে যায়, সেটা তো আরো দুশ্চিন্তার কারণ হবে! সবার সঙ্গেই তার এখন খোলামেলা মেলামেশা দরকার। একথা কি আরো একবার বলে আসবে সে? পেছনে ফিরে তাকাতেই চমকে ওঠে। রায়হান কবির চোরের মতো সন্তর্পণে পা ফেলে এগিয়ে আসে ছোটভাই মিজানের কাছে। অসহায়ের মতো হাত চেপে ধরে ডুকরে ওঠে।
তোর ভাবীর রক্তে কী গোলমাল দেখা গেছে আমাকে বল!
আবছা আলো আঁধারীতে ভাইয়ের মুখ স্পষ্ট দেখতে পায় না মিজান। তবে স্ত্রীর জন্য তার উদ্বেগটুকু বেশ উপলব্ধি করে। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে চেষ্টা করে- যদি হেমাটোলজিক্যাল রিপোর্ট নির্ভুল হয় তাহলে চিকিৎসা শাস্ত্র অনুযায়ী এ ধরনের রোগীদের গর্ভধারণ কতোটুকু ঝুঁকিপূর্ণ তা কি ভাইকে এখনই বুঝিয়ে বলা ঠিক হবে! রক্তের স্যাম্পল পাঠানো হয়েছে ঢাকায়। সে রিপোর্ট না হয় হাতে আসুক। এই বিবেচনা থেকেই সে বলে,
তুমি কি পাগল হলে ভাই! বললাম তো শেষ কথা বলার সময় এখনো আসেনি!
না মানে, তোর ভাবীর কোনো আশঙ্কা নেই তো!
মিজান পাত্তা দেয় না, বলে,
কী যা তা বলছ! এ সব বাজে ভাবনা ঝেড়ে ফ্যালো মাথা থেকে। একটা কথা মনে রেখো ভাই, ভাবীকে মানসিকভাবে সুস্থ করে তোলার দায়িত্ব অনেকাংশেই তোমার।
রায়হান কবির বাগানের ভেতর দিয়ে হেঁটে হেঁটে মূল গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বলে,
আমার তো ব্যবসা-বাণিজ্য আছে। সারা দিন বাইরে বাইরে থাকতে হয়। সময়-সুযোগ পেলে তুই একটু আসিস ভাই।
ডা. মিজান শেষ বেলায় একটু রসিকতা করে, একজন ডাক্তার হিসেবে রোগীর খবর তো আমি রাখবই। আসব নিশ্চয়। কিন্তু তোমার...
না না, কোনো কিন্তু নয়। তুই জানিস তোর ভাবী তোকে কতটা পছন্দ করে। তুই এলেই সে ভালো হয়ে যাবে। আসিস।
নয়.
মানুষের মনের কত যে বিচিত্র গতিধারা, কে কবে তার হিসাব মেলাতে পেরেছে ঠিকঠাক! একটু গভীরভাবে দেখলে নিজের কাছে নিজেকেই অচেনা মনে হতে পারে। আজকের আমি আর গতকালকের আমি দুজন মানুষ হয়ে যাওয়াও মোটেই অস্বাভাবিক নয়। রায়হান কবির খুব ঠা-া মাথায় গত কয়দিনে নিজের আচরণসমূহের চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে বসে একটি বিশেষ জায়গায় এসে চমকে ওঠে, মনে মনে একটু লজ্জিত হয়; নিজেকেই প্রশ্ন করে- এ আমি কী করেছি, সংশপ্তক সাহিত্যবাসর কি আমার শত্রু নাকি?
রায়হান কবিরের সামনেই রচিত হয়েছে সংশপ্তক সাহিত্য বাসর। এই তো মোটে কয়টি সভা হয়েছে। সাহিত্যের প্রতি বিশেষ কোনো অনুরাগ থাক বা না থাক, রাজিয়ার আনন্দের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখতে পারায় ভেতরে ভেতরে এক ধরনের ভালোলাগা বোধ নিশ্চয় কাজ করে। এই যে রাজিয়াকে এবং হোক না রাজিয়ার সুবাদে তাকেও এতগুলো মানুষ সম্মান করছে, ভালোবাসছে; রাজিয়ার এক ছাত্রী-কবি তো তাকেই অকবি জেনেও একদিন একটি কবিতা উৎসর্গ করে বসে; এ সবের মধ্যে তো রায়হানেরও আনন্দ পাবারই কথা। খুব আড়ালে কোথাও কি ঈর্ষার কাঁটাও লুকিয়েছিল! না হলে রাজিয়ার এই অসুস্থতার কালে সাহিত্য বাসরের সবাইকে দুহাতে ঠেলে সরিয়েছে কেন? বেশ ক’জন দেখা করতে এসেছে, দেখা না পেয়ে ফিরে গেছে, ফোনে কথা বলতে চেয়েছে কেউ কেউ, সে সুযোগও কাউকে দেয়নি সে; কিন্তু কেন? আবার এসব কথা রাজিয়ার কাছেও দিব্যি লুকিয়ে রেখেছে। অঘটন ঘটে যাবার পরদিন বিকেলে রাজিয়ার সহকর্মী লতিফ সাহেব আসেন হন্তদন্ত হয়ে, স্থানীয় একটি কাগজের কপি তার হাতে, সে কাগজে নাকি সংশপ্তক সাহিত্য বাসরের শিলাইদহ-অধিবেশনের সচিত্র সংবাদ ছাপা হয়েছে, সেই কাগজের কপি রাজিয়ার সামনে উপস্থাপনের জন্য তার প্রবল ব্যাকুলতা। রায়হান খবরের কাগজের কপি হাতে নিয়ে তাঁকে বিদায় দিয়েছে। ভদ্রলোক রাজিয়ার সঙ্গে দেখা করার জন্য অভদ্র রকমের পীড়াপীড়ি করেছিলেন বলে তার বিদায় যে মোটেই ভদ্রোচিত হয়নি সে কথা এখন বেশ মনে পড়ে রায়হানের। কী লিখেছে কাগজে সেটা খুলেও দেখা হয়নি। লোকটিকে ভালো করে চেনাজানারই বিশেষ সুযোগ হয়নি, তবু কেন যে তাকে প্রচ- ধরিবাজ মনে হয কে জানে!
বহু খুঁজে পেতে রায়হান সেই পুরনো খবরের কাগজ আবিষ্কার করে আনে। ভাঁজ ভেঙে মেলে ধরে চোখের সামনে। না, প্রথম পাতা শেষ পাতায় উদ্দিষ্ট খবর নেই। ভেতরে গিয়ে ৬-এর পাতায় দেখতে পায় শিরোনাম- শিলাইদহে বিশেষ সাহিত্য সভা। এরপর বিস্তারিত বিবরণ। সেদিনের সভায় কে কী ভূমিকা পালন করেছে, খুঁটিনাটি সবই লেখা হয়েছে। অনিবার্য কারণবশত ড. আনোয়ারুল আবেদীন এ সভায় যোগ দিতে পারেননি, সে কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এমন কি ড. মহিদুর রহমান যে দাবি করেছেন- দৃশ্যের আড়ালে হলেও শিলাইদহের এ সাহিত্য বাসরে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত আছেন, তিনি সব দেখছেন সব শুনছেন; এ সব কথাও বাদ যায়নি। বাদ গেছে শুধু রায়হান কবিরের তালগাছ প্রসঙ্গ। রায়হান খুব স্বস্তি পায়। কাগজের সংবাদভাষ্যে সবচেয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে রাজিয়া রায়হানের ভূমিকার প্রতি। রাজিয়া সুলতানাই যে নামের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ঘটিয়ে বর্তমান নাম গ্রহণ করেছে সে কথার উল্লেখসহ তাকে নিয়েই একটা অনুচ্ছেদ ছাপা হয়েছে। মনে মনে ভাবে, এ কাগজ পড়লে কি খুশি হবে না রাজিয়া?
কিসের খুশি হওয়া! এ কাগজ হাতে পাবার পর বাস্তবে দেখা গেল রাজিয়া তো রেগেমেগে একেবারে অগ্নিশর্মা। রায়হান যে আনন্দে আটখানা হয়ে কাগজের পাতা খুলে ধেই ধেই করে নাচতে নাচতে তাকে দেখাতে গেছে এমন নয়। রবং রাজিয়ার সামনে এই কাগজ কেমনভাবে উপস্থাপন করা উচিত হবে, বারান্দার গার্ডেন চেয়ারে বসে রায়হান মনে মনে সেই পরিকল্পনার ছক আঁকছিল। সহসা রাজিয়া এসে তাকে হাতেনাতে ধরে ফ্যালে। মানুষ কখনো কখনো কর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। রায়হানের হয়েছে সেই রকম। এমন অসময়ে রাজিয়া পায়ে পায়ে এই বারান্দায় এসে দাঁড়াবে এটা সে ভাবতে পারেনি বটে, তাই বলে রাজিয়াকে দেখে চমকে ওঠার কোনো মানে হয়! নাকি হাতের কাগজটা অমন দুমড়ে মুচড়ে লুকানোর চেষ্টা করার যুক্তিসঙ্গত কোনো ব্যাখ্যা হয়। রাজিয়ার তো কৌতূহল জাগতেই পারে। ওরে বাপরে! পুরনো সেই কাগজ কেড়েকুড়ে নিয়ে বিশেষ খবরটি নজরে পড়তেই সে তেড়ে ওঠে,
এ কাগজ তুমি কোথায় পেলে?
কী মুশকিল! এ কি গোপন কোনো ইশতেহার কিংবা প্রচারপত্র! এ কাগজ তো এই শহরে প্রকাশ্যেই ছাপা হয়, হকারের হাতে হাতে প্রকাশ্যেই বিক্রি হয়, যে কোনোভাবেই রায়হানের হাতে আসতে পারে। অথচ জেরা করার ধরন দ্যাখো- এ কাগজ তো আমাদের বাড়িতে নেওয়া হয় না। তাহলে এটা এলো কোত্থেকে?
রায়হান ভেবেই পায় না, হঠাৎ কোত্থেকে কী হয়ে গেল। রাজিয়ার এ রকম উত্তেজিত হবারই বা কারণ কী! কাগজে এমন খারাপ কিছুই তো ছাপা হয়নি! শিলাইদহের অনুষ্ঠানে যেমনটি ঘটেছে তারই আনুপূর্বিক এবং বিশ্বস্ত বিবরণ তারা ছেপেছে। সেদিনের অনুষ্ঠানে যারা অংশ নিয়েছে, এ খবর পড়ে তাদের খুশি হবারই কথা। ক’টা দিন এমন ওলোটপালোট হয়ে কেটেছে, এ খবরের প্রতিক্রিয়া কারো কাছ থেকেই জানা হয়নি। তাই বলে এই সংশপ্তকে এমন অগ্নিস্ফূলিঙ্গ! কণ্ঠ সপ্তমে চড়িয়ে রাজিয়া আবারও প্রশ্ন করে।
এ সব খবর তারা পেলই বা কোথায়! লতিফ সাহেব তো সেদিন শিলাইদহে ছিলেন না!
রায়হান কী জবাব দেবে! সে তো জানেই না- রাজিয়াদের কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক লতিফ সাহেব এই কাগজে সাংবাদিকতা করেন। সে অনুমান করতেও পারে না, সংশপ্তক সাহিত্য বাসরের এই সংবাদ ছাপার নেপথ্যে ওই ভদ্রলোকের কোনো ভূমিকা থাকতে পারে! আর যদি তার সে রকম ভূমিকা থাকে, তাতেই বা কী এসে যায়! রাজিয়ার এই আকস্মিক উত্তেজনা প্রশমনের জন্য সে সোজাসুজি জানিয়ে দেয় এ কাগজ কবে কীভাবে এখানে এসেছে। ভয়ে ভয়ে তার অপরাধও অকপটে কবুল করে- রাজিয়ার অসুস্থতার কথা বিবেচনা করেই সেদিন লতিফ সাহেবকে দেখা করতে দেয়নি।
অবাক কাণ্ড! সহকর্মীকে সাক্ষাতের সুযোগ না দেওয়ার জন্য রাজিয়া একটুও অসন্তুষ্ট হয় না। রায়হানকে বকাঝকা তো দূরের কথা, উল্টো আরো আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানায়। মাথামু-ু কিছুই বুঝতে পারে না রায়হান। ঘাড়-মাথা নিতিবিতি চুলকিয়ে সে জানতে চায়,
সত্যিই রাগ করোনি তাহলে!
রাজিয়া দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানায়,
আরে নাহ! ওই লোকটাকে দেখলে আমি আরো অসুস্থ হয়ে পড়তাম।
কী বলছ তুমি! তোমার সহকর্মী যে!
হ্যাঁ, আমি তাকে হাড়ে হাড়ে চিনি। ভাবছি, আমাদের সাহিত্য সভার এতো ডিটেইল্স নিউজ তাকে দিল কে!
সাংবাদিকের জন্য এটা আবার সমস্যা হলো?
না না, আমার ধারণা- আমাদের মধ্যেই তার কোনো সোর্স আছে তাহলে! কে সেই বর্ণচোরা লোকটা?
রায়হান একটু হেসেই ওঠে,
আচ্ছা, এটা কোনো প্রশ্ন হলো! যাকে জিজ্ঞেস করবে সেই বলবে- অনুষ্ঠানে কী কী হয়েছে। সত্যি যা, তা বলবে না!
তাহলে তুমিই তাকে ব্রিফ করেছ! আর সেই খবর কাগজে ছেপে তোমাকে দেখাতে চলে এসেছে ওই ভণ্ড সাংবাদিক!
রায়হানের মুখে কথা সরে না। ভেবেই পায় না, এ সব কথার মানে কী! রাজিয়ার প্রতিক্রিয়া এমন আঁকাবাঁকা পথে কেন ধাবিত হচ্ছে! লোকটি যে এতটা অপছন্দের, তা তো কখনো বুঝতে পারেনি সে! স্থানীয় কাগজে ছাপা সামান্য এক খবর নিয়ে কথা বলতে বলতে এমন কাদাপাঁকে তলিয়ে যেতে হবে সে কথা কে জানত আগে! রায়হান বেশ ভয়ে ভয়ে স্ত্রীর চোখে চোখ রেখে বলে,
একেবারে ভণ্ড বানিয়ে দিলে! আফটার অল তোমরা এক সঙ্গে চাকরি কর তো! তো কী হয়েছে! তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে রাজিয়া, ভণ্ডকে ভণ্ড বলব না?
আহা, ভণ্ডামির কী দেখেছ তুমি!
রাজিয়া এবার ঘুরে দাঁড়ায়,
আমি তাকে চিনি অনেক আগে থেকে। তার ভালো দিক জানি, কপটতা জানি; কিন্তু তুমি হঠাৎ তার হয়ে সাফাই গাইছ কেন বলো তো!
রায়হানের তখন মাথায় হাত। সে মরিয়া হয়ে বলে,
এটা সাফাই গাওয়া হলো! আমি তাকে বাড়ির মধ্যে ঢুকতেই দিলাম না। কার জন্য এমন অভদ্র হলাম বলো দেখি!
বেশ করেছ। ওই অভদ্রলোকের সঙ্গে ভদ্রতা দেখানোর কোনো মানেই হয় না। লতিফ সাহেবের অভদ্রতা সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানে না রায়হান। অনেকদিন কলেজের অনেক প্রসঙ্গ নিয়েই রাজিয়ার সঙ্গে কথা হয়েছে, কিন্তু এ প্রসঙ্গ কখনোই ওঠেনি। একজন সহকর্মী সম্পর্কে কবে কবে যে তার ভেতরে এতটা বীতশ্রদ্ধার বিষবাষ্প জমা হয়েছে, সে কথা মোটেই অনুমান করা যায়নি। এখন গরল উদ্গীরণের এই সময়ে সে পথে পা বাড়াতেই সাহসে কুলায় না। ভাগ্যিস রাজিয়া নিজে থেকেই অন্য প্রসঙ্গে চলে যায়। বহুদিন পরে যেন তার দৃষ্টি পড়ে স্বরচিত বাগানের দিকে। পায়ে পায়ে নেমে আসে বাগানের মধ্যে। বেশ ক’টা ফুলগাছ মাথা নুইয়ে কুর্নিশ করে। তবুও সেদিসে ভ্রুক্ষেপ নেই মহারাণীর। কয়েক কদম এগিয়ে যাবার পর উঁচু হয়ে তুলে আনে নামগোত্রহীন কয়েকটি ঘাসফুল। খুব ছোট, নাকে পরা নাকছবির মতো উজ্জ্বল, ধবধবে সাদা। হাতের মুঠোয় সেই ফুলগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে ধীরে ধীরে তার মন ভালো হয়ে যায়। এতই ক্ষুদে আকৃতির ফুল যে তার বোঁটা খুঁজে পাওয়াই ভার, তবু রাজিয়ার ইচ্ছে হয় খোঁপায় পরার। বার দুয়েক হাত বেঁকিয়ে চেষ্টা করার পর সে টের পায় তার চুলে খোঁপা বাঁধা হয়নি অনেকদিন যাবৎ। ওই ক্ষুদে ফুল সেখানে দাঁড়াবে কোথায়! ফুলগুলো হঠাৎ রায়হানের হাতে তুলে দিয়ে সে জিজ্ঞেস করে,
বলো তো এই ফুলের নাম কী?
ইতস্তত করে রায়হান বলে,
তা তো জানি না। তুমি জানো?
জানি।
পরক্ষণেই ঘাড় নেড়ে বলে, না না জানি না। জানি না। তবে আমিই ওদের নাম রেখেছি লিজা।
লিজা?
হ্যাঁ, হ্যাঁ, লিজা। আমার ছাত্রী। খুব মিষ্টি মেয়ে। ওর নামে নাম রেখেছি। রায়হান বিস্মিত হয়,
কী যা তা বলছ! তোমার ছাত্রীর নামে ফুলের নাম!
হবে না কেন! ফুলের নামে মানুষের নাম হয়, মানুষের নামে ফুলের নামও হতেই পারে। লিজা নাম কি খারাপ?
নাহ! খারাপ কোথায়! লিজা তাহলে ফুলের নাম!
হ্যাঁ। মেয়েটা কোথায় যে হারিয়ে গেল!
তাই নাকি! হারিয়ে গেছে!
কেন দ্যাখোনি- তোমার ওই বিখ্যাত সাংবাদিক ছবিসহ নিউজ ছেপেছিল যে! রায়হানের মুখে কথা সরে না। রাজিয়ার মাথা থেকে ওই সাংবাদিকের ভূত নামেনি এখনো! রায়হান কোন দুঃখে ওই সাংবাদিকের সব সংবাদ পড়তে যাবে! ওই কাগজই তো এ বাসায় রাখা হয় না; তাহলে! সে অনুমান করে, রাজিয়ার এত উষ্মার নিশ্চয় গুরুতর কোনো কারণ আছে। যাক, এখন খুঁচিয়ে কাজ নেই। পরে এক সময় সেই কষ্টের কালো পর্দা উন্মোচন করলেই হবে। রায়হান এভাবে নিজেকে বুঝাতে চায়, শান্ত করতে চায়; কিন্তু রাজিয়া হঠাৎ সংশয়ের বিষবাষ্প ছড়িয়ে দেয়। রায়হানের হাত ধরে সে বলে ওঠে,
প্রমাণ চাইলে আমি দিতে পারব না জানি, কিন্তু আমার মন বলে- লিজার হারিয়ে যাওয়ার পেছনে এই লোকটার হাত আছে।
আকাশ ভেঙে পড়ে রায়হানের মাথায়। দু’চোখ বিস্ফারিত হয়ে ওঠে,
এ সব কী বলছ তুমি!
হ্যাঁ, বলছি। আমার মন বলছে তাই বলছি।
কলেজের আর কেউ এমন সন্দেহ করে?
আমি কেমন করে বলব! সেই যে নিখোঁজ হলো মেয়েটা, তার একটা খবর কেউ আমাকে জানানোর দরকার মনে করে না। প্রিন্সিপাল স্যার পর্যন্ত মুখ খুললেন না। আমি আর কাকে কী বলব!
রায়হান উপলব্ধি করে, লিজা কেবল ফুলের নাম নয়, রজিয়ার বুকের গভীরে লুকিয়ে রাখা রক্তাক্ত এক ক্ষতচিহ্নেরও নাম। বলা যায় সেই দৃশ্যাতীত ক্ষতস্থান থেকেই জন্ম নিয়েছে ওই শ্বেত শুভ্র পুষ্পরাজি। সে আর কথা বাড়ায় না। রাজিয়ার ডান হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে আশ্বস্ত করে,
আমিই চেষ্টা করব লিজার সংবাদ সংগ্রহ করতে। তুমি অত দুর্ভাবনা করো না।
দশ.
সেদিন রাতের বেলা রাজিয়ার চন্দ্রালোকিত মুখের দিকে তাকিয়ে রায়হান কবিরের মনে প্রশ্ন জাগে, কাকে বলে কোজাগরী জোছনা?
কবে যেন একদিন, কুয়াশার চাদর সরিয়ে রায়হান খুঁজে ফেরে সেই অতীত, রাজিয়াকে সঙ্গে নিয়ে চাঁদের রেনু গায়ে মেখে মেখে ঢাকা রোড ধরে হেঁটে হেঁটে যেতে যেতে সে প্রথম শোনে কোজাগরী জোছনার গল্প। শুধু কি তাই! নজরুলের গানের বাণী ব্যবচ্ছেদ করে সেই রাতে রাজিয়া বুঝাতে চেষ্টা করে জোছনার সাথে চন্দন মেশালে কী প্রঘাঢ় আলতা রং তৈরি হয়। প্রকৃতিরাজ্যে এ কী সাংঘাতিক রঙের খেলা! জোছনা ভেজা সেই শারদ রাতে লক্ষ্যবিহীন হেঁটে যেতে যেতে কখনো নজরুল কখনো রবীন্দ্রনাথ তাদের সঙ্গ দেয় কত যে সব গানে গানে! সে রাতে দু’জনেই কেমন চন্দ্রাপ্লুত হয়ে পড়ে। কানায় কানায় উপচে ওঠে তাদের প্রাণের পাত্র। কোথায় চলেছে কোন সুদূরে, পথের কোনো শেষ নেই, নেই উদ্দিষ্ট কোনো ঠাঁই-ঠিকানা; ঢাকা-রোড যেন মায়াবী আঠায় জড়িয়ে তাদের টেনে নিয়ে চলেছে। হাঁটতে হাঁটতে এক সময় হাতের বামে বন্ধ রেলগেটের কাছে এসে তারা থমকে দাঁড়ায়। রেলগেট পেরিয়ে বাম দিকের অপ্রশস্ত রাস্তা ছেঁউড়িয়া গ্রামের বুক চিরে সোজা চলে গেছে মরমী সাধক লালন সাঁইয়ের মাজারে। রাজিয়া কান খাড়া করে, রায়হানের বামহাতে টান দিয়ে ফিসফিসিয়ে বলে- ওই যে গান শুনতে পাচ্ছ, লালনের গান?
কে যেন দরদী গলায় গাইছে, চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে, আমরা ভেবে করব কী!
দুরূহ সমস্যাই বটে।
কিন্তু কোথা থেকে ভেসে আসছে এই গানের বাণী, এই একতারার টুং টাং ধ্বনি! লালন মাজারের প্রাঙ্গণ থেকে? দূরত্ব খুব বেশি নয় বটে, তবু মনে হয় দূরে নয় কাছেই কোথাও নেচে নেচে গাইছে কোনো লালনভক্ত বাউল- ‘ছয় মাসের এক কন্যা ছিল/নয় মাসে তার গর্ভ হলো/এগার মাসে তিনটি সন্তান/কোনটা করবে ফকিরী....।’ রায়হান শুনেছে বটে এ তল্লাট জুড়ে পুরোটাই নাকি বাউলপল্লী, প্রায় সব ঘরে ঘরেই অনেক রাত অবধি গানের আসর চলে, গানে গানেই চলে বাউলদের সাধন-ভজন; লোকমুখে এ সব শুনলেও বাস্তবে কখনো কাছে থেকে দেখার সুযোগ তার হয়নি। রাজিয়াই সেদিন আঙুল তুলে দেখায়- ওই যে ওই বাড়িতে গান হচ্ছে।
রায়হান অবাক কণ্ঠে বলে, ওটা তো ডাক্তার বাড়ি।
তা যে বাড়িই হোক, গান হচ্ছে ওই বাড়ির উঠোনে।
চাটাই ঘেরা উঠোনে হারিকেনের মৃদু আলোয় বসেছে গানের আসর। একটু বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে টের পাওয়া যায় কে একজন নেচে নেচে গান গাইছে। রাজিয়া কৌতূহল নিয়ে জিগ্যেস করে, যাবে নাকি গান শুনতে?
রায়হান আপত্তি জানায়,
নাহ্্। এত রাতে আর গিয়ে কাজ নেই। চলো ফিরে যাই।
সেদিনের জোছনাবিধুর রাতে তারা বন্ধ রেলগেটের মুখ থেকে ফিরেই আসে।
রাজিয়া মুখে কিছুই বলে না, চুপচাপ অনুসরণ করে রায়হানকে। ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে আসে গানের ধ্বনি। তবু চৈতন্যের উঠোন থেকে গানের রেশ কিন্তু নিঃশেষে ফুরায়। রায়হান যেন সেই ঘোরের মধ্যে থেকেই শুধায়,
লালনের গানের অর্থ বোঝো তুমি?
রাজিয়া কোনো কথা বলে না। নিঃশব্দে পাড়ি দেয় রাতের নিস্তব্ধ পথ। এতক্ষণে রায়হানের মনে হয় ডাক্তার বাড়ির গানের আসরে না যাওয়ায় রাজিয়া তাহলে বেশ কষ্ট পেয়েছে! লালনগীতির প্রতি তার এমন প্রবল আকর্ষণের কথা তো সে কখনো প্রকাশ্যে বলে না। হ্যাঁ, অধ্যাপক আনোয়ারুল আবেদীনের আশকারা পেয়ে চুলদাড়ি আচ্ছাদিত এক সাঁইজি বেশ ক’দিন আসা-যাওয়া শুরু করেছিল, গরুমুখী বিদ্যার গুপ্তমন্ত্র জানার জন্য তখন রাজিয়ার সে কী উত্তেজনা! দেহতত্ত্ব নিয়ে সে কী বাড়াবাড়ি! রায়হান গোড়া থেকেই ব্যাপারটাকে প্রশ্রয় দিতে চায়নি। ফলে সেই সাঁইজির যাতায়াতও এক সময় মরা নদীর ধারার মতো রুদ্ধ হয়ে যায়। রাজিয়ার এই আকস্মিক নীরবতা সেই সব কথা মনে করিয়ে দেয়, রায়হান তবু সাবানের ফেনা সরাবার মতো করে সেই স্মৃতির স্তূপ ঠেলে সরিয়ে দিব্যি বলে,
লালনগীতির অর্থই কেমন দুর্বোধ্য, রহস্যময়, তাই না?
রাজিয়া এতক্ষণে কথা বলে,
পুরো ব্যাপারটাই হচ্ছে গুরুমুখী, কিন্তু তুমি তো সে সব জানতেই চাওনি কখনো!
অকপটে বলেই ফ্যালে রায়হান,
সে তো তোমাকে হারানোর ভয়ে।
চাঁদের হাসির বাঁধ ভাঙ্গা ঢেউয়ের মধ্যে রাজিয়া মাখা উঁচু করে তাকায়,
আমার ভয়ে?
হ্যাঁ, আমার চেয়ে যদি তোমার গুরুজির গুরুত্ব বেড়ে যায়!
সহসা রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে রাজিয়া জাপটে ধরে রায়হানকে। আবেগে থরো থরো কণ্ঠে বলে,
তুমিই আমার গুরুজি, তুমিই আমার সাঁইজি, হলো তো!
সহসা রায়হানের ধ্যান ভেঙে যায়। সে এক রকম চম্কে ওঠে- রাজিয়ার মুখ থেকে এভাবে আলো নিভে গেল কেন! মাথার কাছে জানালা খোলা আছে ঠিকই, শিউলির গন্ধভরা মৃদুমন্দ হাওয়া আসছে ঘরে, আলো আসবে না কেন? এই যে কিছুক্ষণ আগে রাজিয়ার মুখম-লে বসরা-ই গোলাপ ফুটেছিল, পূর্ণিমা চাঁদ উঠেছিল; সেই মুখে হঠাৎ কিসের ছায়া! এ কী! ছায়ার আড়ালে তার ঠোঁট জোড়া যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে। কিছু বলতে চাইছে কি। রায়হান মাথা নুইয়ে জানালার ফাঁক গলিয়ে দূরের দিগন্তে তাকিয়ে দ্যাখে, কালো মেঘের ওড়না এসে আড়াল করেছে কোজাগরী চাঁদ। এতক্ষণে বেশ বুঝতে পারে, দূরের আকাশ থেকে তারই ছায়া এসে পড়েছে রাজিয়ার মুখে। বুঝার পরও রায়হান পাগলের মতো দু’হাত মেলে ধরে রাজিয়ার মুখের উপরে, যেনবা দু’হাত দিয়ে প্রতিহত করতে চায় আগ্রাসী ওই অশুভ ছায়ার বিস্তার।
এরই মাঝে রাজিয়ার কপালে ফুটে ওঠে কুঞ্চনরেখা। রেখাগুলো নদীর ঢেউয়ের মতো; মাথা উঁচু করে ফুলে ওঠে, আবার ফণা নামিয়ে নেয়। এ কি তবে রাজিয়ার অব্যক্ত কোনো কষ্টের বহিঃপ্রকাশ! কী সেই কষ্ট? হিসাব মেলাতে গিয়ে নানান প্রসঙ্গ মাথায় আসে, কিন্তু কোনো কিনারা হয় না। ডা. মিজানকে মনে পড়ে। বেশ কয়েকদিন এ বাড়িতে আসছে না সে। কেন আসছে না। রাজিয়ার হেমাটোলজিক্যাল রিপোর্ট কি তাহলে চলে এসেছে ঢাকা থেকে? খুব খারাপ সেই রিপোর্ট? এই রক্ত শরীরে থাকলে কি গর্ভস্থ ভ্রুণ বেড়ে ওঠার পথে কোনো সমস্যা হবে? রিপোর্ট যদি খুব খারাপই হয়, সেই খরাপ মানে যে কী, মিজান সে কথা বুঝিয়ে বলতে চায় না। নিজের ভাই হলে হবে কী, রায়হান বেশ টের পেয়েছ সব ডাক্তারই রোগী কিংবা রোগীর আত্মীয়স্বজনের সামনে মুখোশ এঁটে ঘুরে বেড়ায়, হাত নেড়ে নেড়ে নানা রকম উপদেশ ছড়ায়, সান্ত¡না বিতরণ করে এবং খুব ব্যস্ততার ভান করে। ফলে মুখোশের আড়ালের মানুষটিকে কেউ দেখতে পায় না বললেই চলে। মিজানেরও হয়েছে তাই। ভাবীর সঙ্গে তার একগলা খাতির, অথচ তার অসুখ বিসুখের প্রসঙ্গে খোলামেলা কথা বলতে মোটেই রাজি নয়। ভাবীকে সব কথা বলতে না পারিস তো ভাইকেই না হয় খুলে বল! না, সে বেলায় তিনি মুখোশ আঁটা ডাক্তার।
রাজিয়ার পাশে শুয়ে নানান কথা ভাবতে ভাবতে কখন যেন ঘুম নেমে আসে রায়হানের চোখে। রাজিয়া একবার বুকের কাছে জড়ো করে রাখা হাত দুটো বিছানার উপরে আছড়ে ফ্যালে, তারপরই তার বুক চিরে বেরিয়ে আসে একটি দীর্ঘশ্বাস। ঘুমের ভেতরেও মানুষের দীর্ঘশ্বাস পড়ে তাহলে! এই ভাবনার ভেতরেই ঘুমিয়ে পড়ে রায়হান।
মধ্যরাত পেরিয়ে যাবার পর অকস্মাৎ ঘুম ভাঙে রায়হানের, তাও স্বাভাবিকভাবে নয়, রাজিয়ার ভয়ার্ত চিৎকারে। প্রথমে শোনা যায় তার গোঙানির শব্দ। কারো মুখে কাপড় গুঁজে দেওয়ার পর শারীরিক নির্যাতন করলে যেমন হয় অনেকটা সেই রকম আর্তি ফুটে বেরোয় তার গোঙানির ফাঁক গলিয়ে। ঘুম ভাঙতেই বিছানার উপরে ধসমস করে উঠে বসে রায়হান। হাত বাড়িয়ে আলো জ¦ালতেই দ্যাখে রাজিয়া প্রবল শক্তিতে হাত পা ছুড়ছে, অদৃশ্য কারো বিরুদ্ধে যেন প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, দু’পাশে মাথা নাড়িয়ে তীব্রভবে প্রতিবাদ জানাচ্ছে- ‘না’,
রায়হান শুকনো গলায় ডেকে ওঠে,
রাজি! এ্যাই রাজি! কী হয়েছে তোমার? এ্যাই রাজি!
সমস্ত দাপাদাপি থেমে যায় এক নিমেষে। রায়হান তার কপালে হাত রেখে শুধায়, খারাপ স্বপ্ন দেখেছ?
চোখ মেলে তাকায় রাজিয়া। স্বমীর মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। তার চাখের কোণে অশ্রুরেখা। রায়হান সেই অশ্রু মুছিয়ে দিতেই রাজিয়া তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ওঠে। বিমূঢ় রায়হান স্ত্রীর পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে শুধায়, কী হয়েছে রাজি? কী দেখেছ স্বপ্নে?
রাজিয়ার মুখে কথা নেই। কান্নায় ভেঙে পড়ে। দীর্ঘক্ষণ কেঁদে কেঁদে বুকের বরফ গলতে শুরু করলে তারপর সে স্বপ্নবৃত্তান্তের ঝাঁপি খোলে। শুরুতেই সে জানায় লিজার গণধর্ষণের কথা। বেশ ক’জন নরপশু কলেজ ছাত্রী লিজাকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যায় পার্শ্ববর্তী এক আখ খেতে। প্রথমে মুখের ভেতরে ওড়না গুঁজে দিয়ে তার বাক রোধ করে। তারপর বিবস্ত্র করে পালাক্রমে চলে গণধর্ষণ। ছোট মেয়ে লিজা হাত-পা ছুঁড়ে বহু চেষ্টা করেও নিজেকে মোটেই বাঁচাতে পারে না।
স্বপ্নবৃত্তান্তের এ পর্যন্ত এক রকম ঠিকই আছে।
রাজিয়ার ছাত্রী লিজা সত্যি সত্যি এমন করুণ বাস্তবতার মুখোমুখি যদি নাও হয়, বাংলাদেশের আরো অসংখ্য লিজা প্রতিদিন এ রকম পৈশাচিক নিষ্ঠুরতার শিকার হচ্ছে, অতঃপর সমস্ত লোকলজ্জা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছে; এ ঘটনা নতুন কিছু নয়। খবরের কাগজ খুললেই চোখে পড়ে এই চিত্র। আবার কাগজের আড়ালে অমুদ্রিতই থেকে যায় এমন অনেক মর্মন্তুদ ঘটনাও ঘটে চলেছে প্রতিদিন প্রতিনিয়তই। কাজেই অপহৃত লিজাকে নিয়ে এই ভয়াবহ স্বপ্ন দেখা অস্বভাবিক কিছু নয়। লিজার জন্য রাজিয়ার স্নেহ এবং উৎকণ্ঠা কোনোটি তো কম নয়! তাই বলে নিজেকে লিজা ভেবে কষ্ট পাবার মানে হয়!
রাজিয়ার স্বপ্ন এই জায়গায় এসে অদ্ভুত ভঙ্গিতে বাঁক বদল করে, এমনকি সকল কল্পনাকে হার মানায়। লিজাকে নিয়ে এই দুঃসহ দুঃস্বপ্ন দেখতে দেখতে এক সময় নাকি রাজিয়ার মনে হয়- লিজা নয়, জানোয়ারগুলো একে একে তাকেই ধর্ষণ করে চলেছে। সে প্রবলভাবে হাত-পা ছুড়ছে, থুতু ছুড়ে দিচ্ছে, এমনকি বিশেষ কৌশলে বমি ছুড়ে দিচ্ছে নরপশুদের মুখে; কিন্তু কিছুতেই নিজেকে রক্ষা করতে পারছে না। এক সময় রক্তের বন্যা বয়ে যায় তার যৌনাঙ্গ দিয়ে, তবু মুক্তি নেই, সেই রক্ত বন্যার ভেতরেই তারা চালিয়ে দেয় রণতরী। উহ্্! সে কী নিষ্ঠুরতা!
রাজিয়ার স্বপ্নবৃত্তান্তের এই অধ্যায় যে কারো কাছে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। তার স্বামী রায়হান কবিরের চোখেমুখেও দুলে ওঠে অবিশ্বাসের ছায়া। তার জানা বা শোনা কোনো কল্পকাহিনীর সাথেই যেন মেলাতে পারে না সে। তার সংশয় জাগে, তার স্ত্রী পাগল-টাগল হয়ে যাচ্ছে না তো! এ সংশয় ধরতে পারে রাজিয়া। স্বামীর হাত এনে বিছানায় ছুঁয়ে বলে- এই দ্যাখো, রক্তে ভেসে যাচ্ছে বিছানা।
এগার.
খবর পেয়ে ডা. মিজান ছুটে আসে ভোর হতে না হতে।
রাজিয়া তখন শান্ত হয়ে শুয়ে আছে। বিরামহীন রক্তক্ষরণে সারা শরীর নেতিয়ে পড়েছে নিস্তেজ হয়ে। সারা মুখ ফ্যাকাসে। চোখ দুটো খোলা, তবে ভাবলেশহীন। তার দৃষ্টি যে কোথায় আটকে আছে বলা মুশকিল। অফ হোয়াইট দেয়ালের গায়ে এক জোড়া টিকটিকি তার চোখের সামনে দাপাদাপি করে, তবু কিছু যায় আসে না তার। সে শুয়ে আছে নির্বিকার।
রোগীর চেহারা দেখেই চমকে ওঠে মিজান। হাতের কব্জি ধরে পাল্্স দ্যাখে, চোখের পাতা উল্টিয়ে রক্তশূন্যতা দ্যাখে; তারপর কপালে হাত রেখে মমতায় উদ্বেগে ডেকে ওঠে,
ভাবী! ভাবী!
কোনো সাড়া নেই রাজিয়ার। মিজান তবু ডাকে,
আমার দিকে তাকাও তো ভাবী!
রাজিয়া নির্দিষ্ট কোনোদিকেই তাকায় না। মিজানের কথা সে শুনতে পায় কি না সেটাও বুঝা যায় না। এবার রায়হানকে জিগ্যেস করে মিজান,
ব্লিডিং শুরু হবার আগে ভাবী কি তলপেটে যন্ত্রণার কথা বলেছিল?
না, কোনো যন্ত্রণা তো ছিল না!
ব্লিডিংও ছিল না, তাই না?
হ্যাঁ, সে তো আগেই বন্ধ হয়েছিল!
তাহলে যা ভেবেছিলাম, তাই হলো!
কী হলো মিজান?
ও কিছু না। ভাবীকে এক্ষুনি হসপিটালে নিতে হবে। খুব জরুরি। নাও দেখি ভাই, সেই ব্যবস্থা আগে করো।
এরপর আর কথা চলে না। অতি দ্রুত রাজিয়াকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। রক্ত দেওয়া, অক্সিজেন দেওয়া, গাইনীর ডাক্তারকে ডেকে আনা- ডা. মিজানের দৌড়ঝাঁপের অন্ত নেই। সদর হাসপাতালের ওয়ার্ডবয় থেকে শুরু করে অনেক ডাক্তার সিস্টারই ইতোমধ্যে জেনে গেছে, এই ভদ্রমহিলা ডা. মিজানের রিলেটিভ, মানে একেবারে নিজস্ব রোগী। কনসাল্ট্যান্ট পর্যায়ের ডাক্তারদের কথা আলাদা, জুনিয়র ডাক্তারেরা সবাই বিশেষভাবে খোঁজখবর নেন, সব রকমের সুযোগ-সুবিধার দেখভাল করেন। এদিক থেকে ক্লিনিকে নেওয়ার চেয়ে সরকারি হাসপাতালই রাজিয়ার জন্য অনেক ভালো।
ইনকমপ্লিট এবরশন নিয়ে কত রকম ঝামেলা যে একজন নারীর জীবনে ঘটতে পারে তার কি ইয়ত্তা আছে! অনিয়মিত এবং অস্বাভাবিক রক্তক্ষরণের মতো শারীরিক প্রতিক্রিয়া যে কোনো সময়ে দেখা দিতে পারে, পুনর্বার ঘটতে পারে; তাই বলে এমন তীব্র সংবেদন কাতর মানসিক প্রতিক্রিয়াও কি ঘটতে পারে ওই একই উৎস থেকে! চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও মিজানের জানা শোনার দৌড় এতদূর পৌঁছুতে পারেনি। বড় ভাই হয়েও রায়হান নিজে মুখে তার স্ত্রীর স্বপ্নবৃত্তান্তের যে রকম ভীতিপ্রদ এবং উদ্বেগজনক বিবরণ শোনায়, তাতে ডা. মিজানের দু’চোখ কপালে ওঠার জোগাড়। বিস্ময়ে হতবাক সে। ব্যাখ্যা মেলাতে পারে না- একজন ছাত্রীর সম্ভাব্য শারীরিক নির্যাতন, শ্লীলতাহানি, গণধর্ষণের যন্ত্রণাকে এভাবে কেউ নিজের শরীরে তুলে নিতে পারে? স্বপ্ন বললেই হবে! মিজানের ধারণা, রাজিয়া ভাবী মনে মনে গবেষণা করে বিশেষ প্রক্রিয়ায় এ স্বপ্ন রচনা করে নিয়েছে। দুঃস্বপ্নের এই বোঝা নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে সে কি পেরেছে লিজাকে বাঁচাতে! হায়, স্নেহ বুঝি এমনই অন্ধ এবং অপরিণামদর্শী হয়। কিন্তু মানসিক এই পীড়নের সঙ্গে শারীরিক পরিবর্তনের কারণ কী? এই যে আকস্মিক রক্ত নিঃসরণ, এ কি শুধুই অসম্পূর্ণ অ্যাবরশনের কারণেই ঘটেছে? গাইনী বিশেষজ্ঞের পাশাপাশি কোনো সাইকিয়াট্রিস্টেরও শরণাপন্ন হতে হবে কিনা, তাই নিয়ে খুব ভাবনায় পড়ে ডা. মিজান। সারাদিন অসংখ্য প্রশ্নে জেরবার করে রায়হান, ভাইয়ের উদ্বেগের এই জায়গাটা বেশ বুঝতে পারে মিজান; এলোমেলো উত্তরে ভাইকে যতই সান্ত¡না দিক, ভাবীকে নিয়ে তার উৎকণ্ঠাও কম কিছু নয়। কিন্তু সে কথা সে বলবে কাকে!
বারো.
অবশেষে সপ্তাহখানেক হাসপাতাল বাসের পর রাজিয়া অনেকটা সুস্থ হয়ে ওঠে। আবারও তার মুখে হাসি ফোটে। দুচোখের কোণে জমে থাকা বিষণ্নতার মেঘ কেটে যায়। হাসি-তামাশায় আবার তার গ-দেশে ছলকে ওঠে ঈষৎ রক্তাভা। রায়হানকে সামনে রেখেই মিজানের সঙ্গে রঙ্গ করে ওঠে,
শোনো ডাক্তার, তোমাদের ডাক্তারি শাস্ত্র দিয়ে শেষরক্ষা হবে না সে আমি বেশ বুঝে গেছি।
ডা. মিজান অবাক হয়,
শেষরক্ষা মানে!
নারী জীবনে শেষরক্ষা বলে একটা অধ্যায় আছে, তুমি জানো?
নাহ্্! জানব কী করে!
তাই তো! সে জানার এখনো বয়স হয়নি তোমার। তুমি আমাকে একটা টিয়াপাখি কিনে দিয়ো।
মিজান এবং রায়হান দুজনেই এক সঙ্গে বলে ওঠে,
টিয়া পাখি!
হ্যাঁ, টিয়া হলেই চলবে।
রায়হান ডিটেইলসে যেতে চায়, জিগ্যেস করে,
তার মানে?
মানে আবার কী! ময়না-টিয়া-কাকাতুয়া একটা কোনো বোল ফোটা পাখি হলেই চলবে।
কী হবে পাখি দিয়ে?
রায়হানের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রাজিয়া ঘোষণা করে,
তাকে আমি মা ডাকতে শেখাব।
রাজিয়ার এই অভিনব অভিলাষের কথায় সহসা থমথমে হয়ে যায় পরিবেশ। কী জবাব দেবে, কেউ যেন বলার মতো কথা খুঁজে পায় না। রায়হান মুখ ঘুরিয়ে উদাস চোখে তাকিয়ে থাকে জানালার দিকে। মিজান সামনে এসে মুখোমুখি দাঁড়ায়,
এ তুমি কী বলছ ভাবী!
কেন দুধের স্বাদ ঘোলে মিটবে না ভেবেছ?
না না, তা হবে কেন? তুমি দুধের স্বাদ দুধেই মেটাবে। চিকিৎসা বিজ্ঞান এখন অনেক দূর এগিয়েছে। নিশ্চয় তুমি মা হবে। তোমার কোলে....
বাক্য শেষ করতে দেয় না রাজিয়া। দুম্্ করে বলে ওঠে,
মিথ্যে সান্ত¡না আর কত শোনাবে ডাক্তার! টিয়া পাখি কিনে দেবে কিনা তাই বলো।
এরই মাঝে হঠাৎ হন্তদন্ত হয়ে কেবিনের দরজা ঠেলে প্রবেশ করেন ড. আনোয়ারুল আবেদীন। তার হাতে যথারীতি রজনীগন্ধার তোড়া। নতুন কিছু নয়। হাসপাতালে এলে তিনি অবশ্যই এক গোছা রজনীগন্ধা হাতে নিয়ে আসবেন।
ফুলের সৌরভে ভরিয়ে দেবেন ঘর। হয়তো রজনীগন্ধাই তাঁর প্রিয় ফুল। অন্য কোনো ফুল তার হাতে বিশেষ দেখা যায় না। ঢাকা থেকে ফিরে তিনি প্রতিদিনই হাসপাতালে আসেন। হাতে ওই নির্দিষ্ট ফুলের তোড়া, মুখে সেই ফুলের মতো শুভ্র হাসি। এ দিনও ফুলের সৌরভমাখা হাসি ছড়িয়ে কেবিনে ঢুকেই বলেন,
গুডমর্নিং রাজিয়া। আজকের সকালটা কেমন নির্মল দেখেছ?
চোখ তুলে তাকায় রাজিয়া। বালিশে হেলান দিয়ে একটুখানি উঠে বসে। কিন্তু মুখে কিছুই বলে না। কেবল মিজান হাত তুলে সালাম জানিয়ে একপাশে সরে দাঁড়ায়। আবেদীন স্যার প্রথমে রায়হান, পরে মিজানের মুখের উপরে চোখ বুলিয়ে রাজিয়াকে জিগ্যেস করেন,
কী খবর, কেমন আছ আজ?
রাজিয়া সংক্ষেপে জবাব দেয়,
ভালো আছি স্যার।
কী ব্যাপার বলো তো! আকাশে মেঘ নেই। ঘরের মধ্যে এমন থম্্থমে কেন? কী হয়েছে তোমাদের?
রাজিয়া তবুও নীরব।
ডা. মিজান নীরবতা ভেঙে তার ভাবীর বিচিত্র অভিলাষের কথা সবিস্তারে জানায়। নিজের গর্ভে সন্তান আসবে না এই অমূলক আশংকায় এক অবুঝ রমণীর বাসনা হয়েছে, পাখির কণ্ঠে মা ডাক শুনবে। তাকে টিয়া-ময়না একটা কিছু কিনে দিতে হবে। বায়না ধরেছে এই সাত সকালে। এমন অভিনব বাসনায় কথা শুনে আবেদীন স্যার হা হা করে উচ্চস্বরে হেসে ওঠেন। হাসি থামলে বলেন, পাখির কণ্ঠে কেন মা, আমিই তোমাকে মা বলে ডাকব, হবে না? সরাসরি উত্তর না দিয়ে রাজিয়া এক চিলতে হেসে ফ্যালে। ড. আনোয়ারুল আবেদীনের বুঝি তাতে প্রাণ ভরে না। তিনি তীর্যক অনুযোগ করেন, অ বুঝেছি। বুড়ো খোকার ডাক শুনে কি প্রাণ জুড়ায়?
রাজিয়া মুখ খোলে,
আপনি এভাবে বলবেন না তো স্যার।
কেন বলব না! তুমি মিছেমিছি আকাশ পাতাল এ সব কী ভাবছ বলো দেখি! আমি জানি স্যার, আমার ছেলেপুলে হবে না।
বাজে কথা বলো না তো মা। কে বলেছে তোমাকে এ সব?
রাজিয়া নীরব।
ড. আনোয়ারুল আবেদীন গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেন,
এখানকার ডাক্তাররা যা-ই বলুক, আমি তোমাকে ইন্ডিয়ায় নিয়ে যাব। তখন দেখো সব জল্পনা কল্পনা উল্টেপাল্টে যাবে, হ্যাঁ।
এতক্ষণে রায়হান এগিয়ে এসে জিগ্যেস করে,
সত্যি আপনি ইন্ডিয়ায় যাবেন স্যার?
এই তো সামনের মাসেই যাব। তুমিও চলো আমাদের সঙ্গে।
প্রস্তাব শুনে খুব খুশি হয় রায়হান।
ড. আনোয়ারুল আবেদীন যাবেন ইন্ডিয়ান ফোকলোর ইনস্টিটিউটের আমন্ত্রণে, আগামী মাসের সাতাশ তারিখে তিনি সেখানকার এক সেমিনারে প্রবন্ধ পড়বেন। তারপর একদিন গেস্ট-লেকচারার হিসেবে বক্তৃতা করবেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। এ সময়ে রাজিয়া রায়হানের সঙ্গ পেলে তিনি অত্যন্ত খুশি হবেন এ কথা অকপটে জানান এবং সোজাসুজি বলেন,
হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে তাড়াতাড়ি তোমাদের বাড়ি চলো দেখি। বাড়িতে বসেই আমরা পনেরো দিনের ভ্রমণ-পরিকল্পনা ফাইনাল করে ফেলব বুঝেছ! কোথায় কোথায় ঘুরতে চাও তোমরা ঠিক করে ফ্যালো। বাকি দায়িত্ব আমার।
স্যারের প্রস্তাব শুনে রাজিয়া এবং রায়হান দুজনেরই মন ভরে ওঠে আনন্দে। এ যেন হঠাৎ পাওয়া এক দুর্লভ সুযোগ। ভারতে এর আগেও স্বামী-স্ত্রী দু’জনে মিলে বেশ ক’বার বেড়াতে গেছে। পশ্চিম বাংলার দর্শনীয় স্থানগুলো তো বটেই একবার তারা দিল্লি হয়ে আজমিরও ঘুরে এসেছে। কিন্তু শিশুর সারল্য মাখা এই বয়স্ক অভিভাবকটি তো তখন সঙ্গে ছিলেন না। দু’জনেই একমত- এবারের সম্ভাব্য ভ্রমণটি নিশ্চয়ই যথেষ্ট আনন্দদায়ক হবে। রাজিয়া হঠাৎ বায়না ধরে, আমাকে তাহলে কাশ্মিরী ময়না কিনে দিতে হবে কিন্তু স্যার।
টিয়া-ময়না প্রসঙ্গ এরই মাঝে একেবারে ভুলে বসে আছেন আবেদীন স্যার।
তাই তিনি চম্কে ওঠেন,
কেন, বিদেশ-বিভূঁইয়ে ময়না কী হবে?
রাজিয়া ঢোক গিয়ে দুঃখ হজম করে ফ্যালে। দীর্ঘশ্বাস ঝেড়ে সে বলে, ভ্রমণের পাশাপাশি আমি কিন্তু একটু চিকিৎসাও করিয়ে আসতে চাই।
হঠ্যাৎ যেন মনে পড়ে যায়,
অ, চিকিৎসা! আচ্ছা, সে নিশ্চয় করা যাবে। কিন্তু ময়না দিয়ে কী হবে মা? আবার এ প্রশ্ন শুনে রাজিয়া হাসবে নাকি কাঁদবে ভেবে পায় না। স্যারের ডান হাতটা নিজের মাথায় তুলে নিয়ে সে বলে,
আপনি কাছে থাকলে ময়না-টিয়া কিছুই লাগবে না আমার।
অ। তাই বুঝি!
রায়হান মিজান দুই ভাই-ই অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে আবেদীন স্যারের মুখের দিকে। কিন্তু সেদিকে মোটেই ভ্রুক্ষেপ নেই তাঁর। রাজিয়ার কপালে হাত রেখে তিনি বলেন,
ইন্ডিয়া যাবার আগে আমাদের যে আরো অনেক কাজ আছে মা।
কী কাজ স্যার?
আমাদের এ মাসের সংশপ্তক সাহিত্য বাসরে কবি নির্মলেন্দু গুণ আসতে রাজি হয়েছেন, তোমাকে বলেছি সে কথা?
না তো! গুণদা আসবেন?
বলিনি বুঝি! আজকাল এই রকমই হচ্ছে, অনেক কিছুই মনে থাকছে না। আর মনে থাকলেই বা কী! হাসপাতাল তো হাসপাতালই। সব কথা এখানে বলা যায়!
আগে তোমার বাড়ি চলো।
জি¦ স্যার। আপনি জানেন আমাদের বাড়ির নাম সংশপ্তক।
হ্যাঁ জানি তো! খুব চমৎকার নাম। শব্দটির গায়ে লড়াইয়ের ঘ্রাণ আছে।
বাড়ি গেলেই আমি নতুন করে যুদ্ধজয়ের সাহস পাব, শক্তি পাব।
ভেরি গুড। আমি দেখছি রিলিজের কী করা যায়!
রায়হান জানায়,
মিজান গেছে স্যার। সে-ই সব ব্যবস্থা করে ফেলবে।
ছোট্ট এই শহরে দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করার সুবাদে ড. আনোয়ারুল আবেদীন অসংখ্য ছাত্রছাত্রী পেয়েছেন। তাদের অনেকেই এখন এ শহরের স্কুল-কলেজ অফিস-আদালতে নানাভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই হাসপাতালের ডাক্তারদের মধ্যেও অনেকেই তাঁর ক্লাসরুমের ছাত্র বা ছাত্রী। তারা শিক্ষককে সম্মান করে। ডা. মিজান তো আছেই, সেই সাথে আবেদীন স্যারের কারণেও রোগী হিসেবে রাজিয়া হাসপাতালে কর্তব্যরত ডাক্তারদের বিশেষ মনোযোগ পেয়েছে। এক সপ্তাহের হাসপাতালবাস শেষে আবেদীন স্যারের উপস্থিতিতে হাসপাতাল থেকে বিদায় নিতে রাজিয়ার ভেতরে অন্যরকম অনুভূতি জেগে ওঠে। তার মনে হয় দুঃসহ এক সংকট পাড়ি দিয়ে সে দায়িত্বশীল পিতার স্নেহার্দ্র হাতে হাত রেখে বাড়ি ফিরছে, বাড়ির নাম সংশপ্তক।
রাজিয়া বাড়ি ফিরবে বলে গেটের মুখে রাধাচূড়া এবং কৃষ্ণচূড়া কী অপরূপ সাজে সেজেছে। একজন লাল আগুনের দ্রোহ ছড়াতে চায় আকাশময়, অন্যজন প্রগাঢ় বাসন্তী রঙের প্রেমার্ত আঁচলে বাঁধতে চায়। এরই মাঝে স¤্রাজ্ঞীর মতো প্রবেশ করে রাজিয়া সুলতানা। কিন্তু এ কী! একেবারে শুরুতেই জোড়া শালিক যে! কী গভীর প্রণয় দ্যাখো। হলুদ ঠোঁটের ফাঁকে ঝগড়–টে হাসি। আবার কেমন মাথা ঝাঁকিয়ে কুর্নিশ করার ঢং! তবে কি ওরাও তাকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে! ওই যে গোলাপেরা হাসছে দুলে দুলে! কেন, এত হাসির কী হলো! ফুটেছ, বেশ করেছ। কই, আমার সেই রাণী-গোলাপ কই? বহু দূর থেকে আনিয়ে নেয়া প্রিয় গোলাপ খোঁজে রাজিয়া- কোথায় লুকালে রাণী মা! প্রশ্নের ধারা বুঝতে পারে রায়হান। স্ত্রীর পিঠে হাত রেখে আশ্বস্ত করে, আছে, রাণীও আছে; সবে কুঁড়ি এসেছে। রক্তমুকুট পরিয়ে দেবার জন্য অপেক্ষা করছে জবা ফুলের ঝাড়। দুই সারি রজনীগন্ধা কেমন সুশৃঙ্খল ভঙ্গিমায় মৃত্তিকালগ্ন হয়ে সৌরভ ছড়িয়ে চলেছে। এত প্রাণ, এত ঘ্রাণ, তবু কত বিন¤্র বিনয়! রাজিয়ার ইচ্ছে করে উবু হয়ে বসে দুহাতের দশ আঙুলে ছুঁয়ে ওদের আদর জানায়, কানে কানে বলে দেয়- এই যে আমি এসেছি।
কী নেই সংশপ্তকের বাগানে! ফুলগাছ তো আছেই, পাতাবাহারই আছে দশ প্রজাতির। বাব্বা! কী তাদের রূপের বাহার! প্রকৃতি এত যে নিপুণ হাতে রঙের খেলা খেলেছে, এরচেয়ে বড় শিল্পকর্ম আর কী হতে পারে! শৈশব থেকেই কেন যে সাদা রঙের প্রতি রাজিয়ার বিশেষ পক্ষপাত, সে কথা নিজেও খুব ভালো জানে না। জুঁই, চামেলি, শেফালি, কামিনি, হাস্নাহেনা, চন্দ্রমল্লিকা- কত না শ্বেত শুভ্র আয়োজন। তবু আশ মেটে না রাজিয়ার, রাস্তার পাশ থেকে একঝাড় ধুতুরা ফুলের গাছ তুলে এনে নিজে হাতে তাকে বাগানবাসের সম্মান দিয়েছে। কী যে কৃতজ্ঞতাবোধ, এরই মাঝে রসুনসফেদ ফুল ফুটিয়ে সে অপেক্ষা করছে, রাজিয়ার মুখেও সে যেন বা শুচিশুভ্র হাসি ফোটাতে চায়।
ঘরের দরজায় পা বাড়াতেই আবেদীন স্যার ব্রেক করে দাঁড়িয়ে পড়েন। সোজা জানিয়ে দেন- এখন আর নয় মা, রাতে আসছি। সাহিত্য বাসরের আগামী অনুষ্ঠান নিয়ে অনেক পরিকল্পনা আছে। কথা আছে। তুমি রেস্ট নাও। আমরা আসছি।
আনোয়ারুল আবেদীন ঘুরে দাঁড়াতেই রায়হান বলে ওঠে,
টিয়া-ময়নার ব্যপারটা তাহলে কী সমাধান হলো স্যার!
স্যার হা হা করে হাসেন। সে হাসিতে বাগানের সব ফুল যোগ দেয়, নেচে ওঠে, দুলে ওঠে, গড়িয়ে পড়ে, লুটিয়ে পড়ে গায়ে গায়ে। স্যারের মাথার উপর দিয়ে একঝাঁক অচেনা পাখি উড়ে যায় নিরুদ্দেশের পথে। কী জানি তাদের কুজন তাঁর কানে এসে পৌঁছে কিনা। তিনি ঘাড় তুলে একবার আকাশের দিকে তাকান। তারপর রায়হানের দিকে তাকিয়ে বলেন,
ওই দ্যাখো পাখির সারি আকাশে উড়ে উড়ে তোমাদের কথা বলছে। আমি বলছি, তোমাদের এই সংশপ্তকে ময়না-টিয়ার কোনো অভাব হবে না। ওরা নিজে থেকেই আসবে।
বারান্দায় দাঁড়িয়ে রাজিয়া যোগ করে,
নইলে আমার বুড়ো ছেলে তো আছেই, তাই না স্যার!
আবার হেসে ওঠেন আনোয়ারুল আবেদীন,
ঠিক বলেছ মা। আমি এখন আসছি।
বাগানের পথ ধরে ধীর পায়ে চলে যান আবেদীন স্যার। বারান্দায় দাঁড়িয়ে রাজিয়া এবং রায়হান তাঁর চলে যাওয়াটা চেয়ে দ্যাখে। কী অবাক কাণ্ড! দৃষ্টির আড়াল হবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে দুষ্টু বালকের মতো একবার পিছু ফিরে তাকাতে গিয়েই স্যার ধরা পড়ে যান এবং শিশুর সারল্যমাখা ঠোঁটে ফিক করে হেসে নিজেকে সরিয়ে নেন।
কাঁধে ব্যাগ ঝুলানো স্কুলগামী পুত্রকে রাস্তায় উঠিয়ে বিদায় জানাবার সময় মা যেমন করে দূর থেকে হাত নাড়ায়, রাজিয়া সেইভাবে দুহাত নেড়ে বিদায় জানায় পিতৃপ্রতিম প্রিয় শিক্ষক আবেদীন স্যারকে। দৃষ্টির সীমানা থেকে স্যারের ছবি একেবারে আড়াল হয়ে যাবার পরও যেন তার পা ওঠে না, নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকে আরো অনেকক্ষণ। খানিক পরে রায়হান হাত বাড়িয়ে স্ত্রীর ডান হাত তুলে নেয় নিজের হাতের মুঠোয়, তারপর চোখে চোখ রেখে আহ্বান জানায়,
এসো, তোমার জন্য অপেক্ষা করছে সংশপ্তক।
রাজিয়ার চোখের পাতা কেঁপে ওঠে তিরতিরিয়ে। এতদিনের চেনা মানুষটিকেই যেন নতুন করে দ্যাখে। তার চোখের তারায় যেনবা হাজার বছরের আশ্রয় খোঁজে, আকাশ জোড়া ছায়া খোঁজে। দিনের শেষে আকাশ ছেড়ে নেমে আসা পাখিরা খড়কুটোর নীড়ে কী যে খুঁজে ফেরে কে জানে, গৃহে প্রবেশের পূর্বেই রাজিয়া আশ্রয় নেয় স্বামীর বক্ষ মন্দিরে। তখন বাগানের সব ফুল হেসে ওঠে একযোগে, প্রজাপতি দুই পাখা যুক্ত করে বাজায় আনন্দ করতালি, পাখিরা গেয়ে ওঠে গান।
তখনই দেখা যায় ঢাকা রোডের বাম পাশ দিয়ে একাকী হেঁটে চলেছে ছেঁউড়িয়াগামী এক বাউল ফকির। তার হাতের এক তারায় আঙুলের জাদুকরী ছোঁয়া লেগে বোল ধরেছে চেনা গানের-
চাতকপ্রায় অহর্নিশি
চেয়ে আছে...