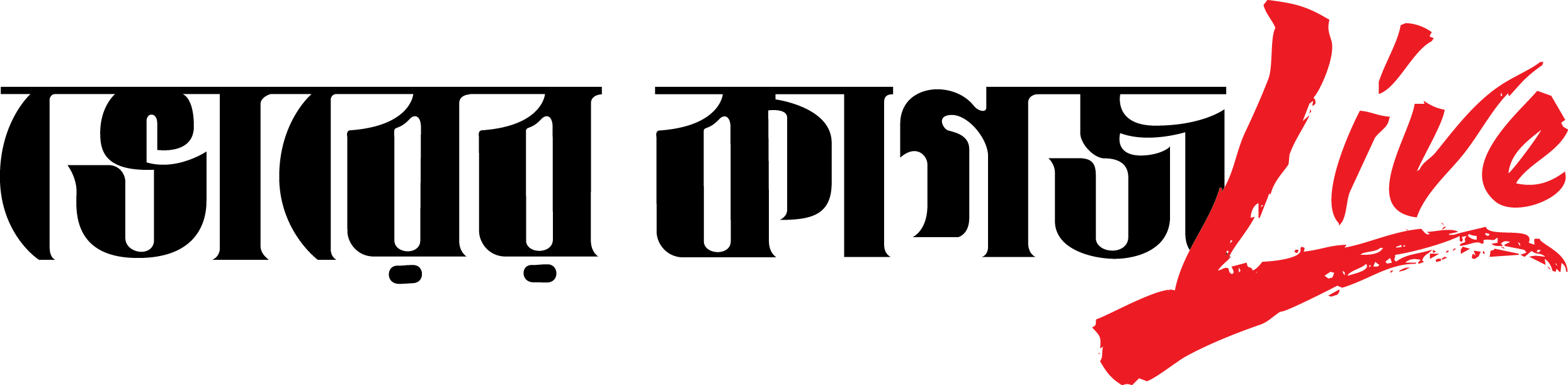দায়
কাগজ প্রতিবেদক
প্রকাশ: ৩১ মে ২০১৯, ০৭:৩৫ পিএম

এ গল্পটা আমার লেখা নয়। রুদ্র সুধাকরের। একটা ডাইরিতে লেখা ছিল এটি। গল্পটা আমার নয়, অথচ আমার বলে ছাপতে দিলাম কেন? এই রুদ্র সুধাকরই বা কে? ডাইরিটাও আমি পেলাম কোত্থেকে? প্রথম তিন লাইন পড়ে পাঠকের মনে এ রকম প্রশ্নগুলো জাগছে, জানি আমি।
গল্পবৃত্তান্তে যাওয়ার আগে এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর দেয়া জরুরি। উত্তর দেব শেষ প্রশ্ন থেকে। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থেমে যাব আমি। তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর দেব না। গল্প পড়া শেষে পাঠকরা নিজেরাই বুঝে যাবেন কেন নিজের না হয়েও গল্পটি ছাপতে দিলাম। বলে রাখা ভালো- এ কিন্তু নিছক গল্প নয়, জীবনের নানা সময়ের নানা টুকরো টুকরো কথা। সত্যকথা। গল্পকথার মতো কল্পকথা নয়। আর আমি যদি ছাপতেও দেয়ার দায়িত্ব না নিতাম, একটা সময়ে তা ছেঁড়াফাটা কাগজের জঞ্জালে নিক্ষেপিত হতো। আমরা বঞ্চিত হতাম একজন অনেক পাওয়া অথচ কিছু না পাওয়া মানুষের আত্মকথা থেকে।
একদা সিদ্দিক সাহেবের সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল। সিদ্দিক সাহেব কে? সিদ্দিক সাহেব মানে সিদ্দিক আহমেদ। স্থানীয় একটা দৈনিক পত্রিকায় অনুবাদ সেকশনে কাজ করতেন। ইংরেজিটা মাতৃভাষার মতো জানতেন তিনি। খুব বেশি যে বেতন পেতেন, এমন নয়। পরিবার থাকতো গ্রামে। রাউজানের দিকে কোনো এক গ্রামে তার বাড়ি। জমিজমা নেই, ভিটেটা সম্বল। বাম রাজনীতি করতেন। ও কারণে আখের গোছানোর চিন্তা মাথায় ছিল না। বেতনেই সংসার চলত। দুই ছেলে, এক মেয়ে। ওই বেতনেই ওদের লেখাপড়া, হোস্টেলে থাকা। নিজে থাকতেন শহরে। ছোট্ট একটা ঘরে। খাওয়া হোটেলে। দৈনন্দিন কৃত্য সমাপন করতেন অন্যজনের টয়লেটে। পড়তেন তিনি খুব, পড়াতেও জানতেন। কোনো ভালো বইয়ের সন্ধান পেলে অন্যদের না জানিয়ে, না পড়িয়ে ক্ষান্ত হতেন না। গোটাটা জীবন বই-ই কিনে গেছেন শুধু। তক্তপোশে আগে চিত হয়ে শুতেন। সংগৃহীত বই একদিন মেঝে ছাড়িয়ে তক্তপোশে উঠে এল। প্রথমে এক সারি। তারপর দুই, তিন। চিত হয়ে শোয়ার জায়গা হারালেন সিদ্দিক সাহেব। কাত হয়ে শুতে শুরু করলেন। সব সময় নতুন বই কিনতে পারতেন না। পুরনো বই-ই কিনতেন বেশি। বলতেন- যত পুরনো, তত রেয়ার। পছন্দের নতুন কোনো বই হাতে এলে প্রথমে দাম দেখতেন- কেনার সাধ্য আছে কিনা। ডান হাতটা প্যান্টের পকেটে বুলিয়ে নিতেন। ব্যাটেবলে হয়ে গেলে মুখে হাসি ফুটত। সিদ্দিক সাহেব সম্পর্কে এত কথা লেখার প্রয়োজন নেই। তিনি এই গল্পের নায়ক নন, সামান্য একটা পার্শ্ব চরিত্র। তারপরও তার কথা কলমে এসে যাচ্ছে বলে লিখলাম। সিদ্দিক আহমেদ পুরনো বইদোকান থেকে বই সংগ্রহ করতেন। ঢাকায় যেমন নীলক্ষেত, চট্টগ্রামে তেমনি নূপুর মার্কেট। নূপুর মার্কেটের দোতলায় সারি সারি বই দোকান। সবগুলো পুরনো বইয়ের।
এক সন্ধ্যায় তিনি আমাকে সেখানে নিয়ে গেলেন। দেখলাম- এদোকান ওদোকান তাকে ডাকছে- সিদ্দিক ভাই, সিদ্দিকদা আমার দোকানে আসেন। ভালো কালেকশন এসেছে। ইংরেজিও অনেক। সিদ্দিক সাহেব বেছে বেছে বই কেনেন, নিজের দামে। দোকানদারদের হাসিমুখ যা দেবেন, তাতেই সই। দোকানদারদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন। পরে পরে আমিও যাওয়া শুরু করলাম পুরনো বইদোকানে। কখনো সিদ্দিকদার সঙ্গে, হ্যাঁ, সিদ্দিক সাহেব তখন আমার কাছে সিদ্দিকদা হয়ে গেছেন, কখনো একা। গোবিন্দের সঙ্গে আমার খাতির হয়ে গেল খুব। গোবিন্দের দোকানটা যেন বাংলা বইয়ের আড়ত, বিশেষ করে বাংলা উপন্যাসের। বাংলা উপন্যাস আমার ভীষণ পছন্দ। শহরের অলিগলি ঘুরে ঘুরে সে এসব বই কিনে আনে। নারীরাই এসব বই বিক্রি করে বেশি। স্বামী চাকরিতে চলে গেলে বউরা বইকে সতীন মনে করে বিদেয় করে। এ্যাডিক্টের ছেলেমেয়েরাও গোবিন্দের কাছে বই নিয়ে আসে। তাদের কাছ থেকে বই কিনতে খুব বেশি বেগ পেতে হয় না গোবিন্দকে। আমার পছন্দের হদিস পেয়ে গেছে গোবিন্দ। বেছে বেছে আমার জন্য গল্প উপন্যাসের বই রেখে দেয় সে।
তো সেই সন্ধ্যায় বইটই কেনার পর একটা জরাজীর্ণ ডাইরি এগিয়ে ধরল গোবিন্দ।
আমি বললাম, ‘এটা কী?’
গোবিন্দ বলল, ‘একটা ডাইরি স্যার।’
‘এ রকম ছেঁড়াখোঁড়া ডাইরি দিয়ে আমি কী করব?’
‘ভিতরের অনেকগুলো পাতাজুড়ে লেখা স্যার। সতীশ লেনের এক ফ্ল্যাটে থেকে কিছু বই কিনেছি স্যার। যুবতি। ওঘরের পুতের বউটউ হবে। ডাইরিটা আমার দিকে ছুড়ে দিয়ে বলল, এটাও নিয়ে যাও। স্যার এসব করতে করতে চুলতো পেকে গেল আমার। ফেলতে শিখিনি। নিয়ে এলাম সঙ্গে করে। দুচার পাতা পড়ে কিছু বুঝলাম না। ভাবলাম- ফেলে দেয়ার আগে আপনাকে বা সিদ্দিকদাকে দেখাব। আপনি আগে এলেন।’ বলে গেল গোবিন্দ।
হাত বাড়িয়ে ডাইরিটা নিলাম। বহু বছরের পুরনো। চৌকো সাইজের খয়েরি মলাট। ধূলঝুল লেগে মলাটটি তার খয়েরিত্ব হারিয়েছে। বেশ পুরু। ভেতরটা খুলে দেখার লোভ লকলকিয়ে উঠল। খুলতে যাব ওই সময় গোবিন্দ বলে উঠল, ‘আসেন, আসেন সিদ্দিকদা। এবারের কালেকশন বেশ ভালো। কাল এনেছি। একটা ফ্যামেলি ধুয়েমুছে সব বই বিক্রি করে দিয়েছে।’
চট করে ঘাড় ঘোরালাম। বললাম, ‘আরে সিদ্দিকদা, আপনি না বললেন আসবেন না! কাজের অনেক চাপ।’
‘আর বলবেন না, কাজ ছিল ঠিকই, সন্ধ্যে হলে যে পুরনো বই আমাকে টানতে থাকে। নাকমুখ ডুবিয়ে কাজটা শেষ করে দে দৌড়। বলেছিলাম- আজ যাব না, এই দেখুন এসে পড়েছি।’ মৃদু একটা হাসলেন সিদ্দিকদা। ‘আর আপনার জন্যও এসেছি। জানি- আপনি আসবেন, গোবিন্দের দোকানে পাওয়া যাবে আপনাকে।’ গোাবিন্দের দিকে মুখ ফেরালেন সিদ্দিক আহমেদ, ‘তা গোবিন্দ কী কী বই এনেছো দেখাও দেখি।’
গোবিন্দ বলল, ‘এই দিকে, ওই যে ওপরের তাক দুটোতে গুছিয়ে রেখেছি।’
সিদ্দিক আহমেদ সেদিকে এগিয়ে গেলেন। কোনোদিন যা করিনি, তাই করলাম আজ, ডাইরিটা একটা প্যাকেটের মধ্যে লুকিয়ে ফেললাম। কেন লুকালাম, তার কোনো ব্যাখ্যা নেই আমার কাছে। ভাবলাম কি ডাইরিটা যদি সিদ্দিক আহমেদ পেতে চান? এমনিতে পুরনো, জরাজীর্ণ বইপত্রিকার প্রতি সিদ্দিকদার অমোঘ আকর্ষণ। বলেন- ‘পুরনো চালের মতো পুরনো বইপত্রের মূল্য বেশি। অনেক রেয়ার বইয়ের প্রথম এডিশন পাওয়া যায়, কখনো কখনো লেখকের স্বাক্ষরসহ।’ পুরনো বলে, রেয়ার কিছু মিলবে বলে হয়তো তিনি ডাইরিটা পেতে চাইবেন, এই ভয়ে লুকিয়ে ফেললাম।
এমনিতে আমি যা কিনি, ওকে দেখাই। নানা মন্তব্য করেন তিনি। কোন বইটা কী অর্থে মূল্যবান, বলেন তিনি। তবে নিজের বেলায় ব্যতিক্রম। কোনো বই পছন্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বগলদাবা করেন। করেন উল্টোভাবে। বইটার নাম যাতে দেখা না যায়। জিজ্ঞেস করলে বলেন, ‘আরে তেমন ভালো বই না, সামান্য একটা বই, আপনার দরকারে লাগবে না।’ বলতে বলতে বগলের চাপ বাড়ান তিনি। আবার কখনো ভীষণ প্রয়োজনীয় একটা বই আমার দিকে বাড়িয়ে ধরে বলেন, ‘ধরেন, এটা আপনার কাজে লাগবে।’
যাক, অনেক আগডুম বাকডুম বলা হলো। মোদ্দাকথা এই- সেই সন্ধ্যায় কেনা বইয়ের আড়ালে ডাইরিটা বাসায় নিয়ে আসতে পেরেছিলাম আমি, সিদ্দিক আহমেদের চোখ এড়িয়ে।
খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকাতে চুকাতে বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল। কন্যা এসেছে নাতনিকে নিয়ে। গিন্নির আহ্লাদের সীমা নেই। ন’বছরের নাতনি প্রতীক্ষার জন্য নানা পদের রান্না করতে লেগে গেল গিন্নি। আমাকে বলল, ‘রাতের ভাত দেরি হবে। প্রতীক্ষারা খেয়ে চলে যাবে। হেঁশেলে একটু সময় লাগবে আজ।’
নাতনি ও কন্যা বিদেয় হওয়ার পর খাওয়ার পাট চুকিয়ে গিন্নি শোয়ার ঘরে চলে গেল। আমি গিয়ে বসলাম পড়ার টেবিলে। প্যাকেট থেকে ডাইরিটা বের করলাম। গোবিন্দের দোকানে যাও একটু চকমক করেছিল, আমার টেবিলে ডাইরিটাকে চুরাশি বছরের চামড়া তোবড়ানো বুড়োর মুখম-লের মতো লাগছে। কী থাকতে পারে এই ডাইরিতে? কারো রোজনামচা? কোনো বৃদ্ধার বহু বছরের বাজার হিসাব? আলু-পটোল-চাল-ডাল-নুনের দাম? নাকি কোনো ব্যর্থ প্রেমিকার না পাওয়া মনের কথকতা? অথবা...। অথবা ’৭১-এর কোনো লাঞ্ছিতা নারীর আত্মকথন? বুকটা দুরু দুরু। ভেতরটায় যেন লাঙ্গলের ফলা চলছে। চট করে মলাটটা উল্টালাম। ওরেব্বাস! এ যে রুদ্র সুধাকরের ডাইরি। প্রথম পৃষ্ঠার মাঝামাঝিতে লেখা- রুদ্র সুধাকর। জন্ম : ১৯৪৭, মৃত্যু সাল জানা নেই। মাথাটা চক্কর খেল- কোন রুদ্র সুধাকর? সেই বিখ্যাত অধ্যাপক নন তো! যার লেকচার শোনার জন্য আশপাশের ক্লাসগুলো হুমড়ি খেয়ে পড়ত! শুধু তাই কেন? ধর্মসভাও তো কাঁপাতেন রুদ্র সুধাকর। যুক্তি ও ধর্মকে, সংস্কার ও বিজ্ঞানকে ভাব ও বাস্তবতাকে অতিশয় বিশ্বস্ত করে উপস্থাপন করতেন রুদ্র সুধাকর। এই চট্টগ্রাম শহরের খ্যাতিমান অধ্যাপক, যুক্তিবাদী ধর্মবিশ্লেষক হিসেবে রুদ্র সুধাকর কিংবদন্তিতুল্য। তারই ডাইরি কি এটা? বুকের কাঁপন বেড়ে গেল আমার। চোখ বন্ধ করে ঝিম মেরে থাকলাম কিছুক্ষণ। বড় একটা শ্বাস টানলাম। তারপর পড়তে শুরু করলাম। রাত তিনটে যখন, পড়া শেষ হলো। বড় ঘুম পাচ্ছিল তখন। ঘুমাতে যাওয়ার আগে শুধু এইটুকু লিখতে ইচ্ছে করছে- হ্যাঁ এটি সেই কীর্তিধারী ব্যক্তি রুদ্র সুধাকরের ডাইরি, যিনি পাঁচ বছর সাত মাস আগে নিজের বেডরুমে গলায় দড়ি দিয়েছিলেন। সেই সময় বেশ হইচই পড়ে গিয়েছিল শহরে- এ রকম সুখী, জ্ঞানী, জনপ্রিয় একজন মানুষ সত্তর বছর বয়সে আত্মহত্যা করলেন কেন? ডাইরিতে ‘কেন’র উত্তর আকারে-ইঙ্গিতে আছে। পুলিশ হয়তো সে সময় ডাইরিটির সন্ধান পায়নি। পেলে আত্মহত্যার কারণ খুঁজে পেতো।
পরদিন গিন্নি স্কুলে চলে গেল ডাইরিটা নিয়ে বসলাম। গিন্নি প্রাইমারি স্কুলের হেডমিস্ট্রেস। আর আমি বেকার। উপজেলা পর্যায়ের একটা ডাকঘরের পোস্টমাস্টার ছিলাম আমি। অবসরে এসেছি বেশ ক’বছর হয়ে গেল। যাক ব্যক্তিগত রোজনামচা বাদ দিয়ে রুদ্র সুধাকরের রোজনামচায় আসি। ডাইরির প্রথম তারিখটা ৭ মে ১৯৬৪। সুধাকর লিখেছেন- সতেরো ছাড়িয়ে আঠারোতে পা দিলাম আমি। আগে কখনো লিখিনি। আমার মেজমামা ডাইরিটা উপহার দিল বলে লিখলাম।
পরের প্যারায় লিখেছেন- বরিশালের মেহেন্দিগঞ্জে জন্ম আমার। এ বছর মেট্রিক পরীক্ষা দেব। বাবা কুমোর। তাই আমরা রুদ্র লিখি। আমাদের বাড়ির পাশ ঘেঁষে খাল। একটু দূরে সন্ধ্যানদী। এই খাল গিয়ে সন্ধ্যার সঙ্গে মিশেছে। আমাদের খালে এঁটেল মাটি। পাড়াটা কুমোরদের পাড়া। কুমোরেরা মাটি দিয়ে হাঁড়ি পাতিল বাসন কোসন গেলাস তৈরি করে। গ্রামে গ্রামে এগুলোর বেশ কদর। বাড়ি বাড়ি মাটির চাকা ঘোরে। আমাদের উঠান জুড়ে কাঁচা মাটির কলসি হাঁড়ি পাতিল। একটু দূরে বিশাল বড় চুলা। হাঁড়ি পাতিল রোদে টানটান হলে চুলায় দেয়া। তারপর পুড়ে পুড়ে লালচে।
ওই তারিখে আর লিখেননি সুধাকর। পরের তারিখে লিখলেন-
মা এসে পিঠের ধারে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল- কী লিখছিস খোকা? ঝুপ করে ডাইরিটা বন্ধ করে বলেছিলাম- কই কিছু নাতো মা! লিখেছিলাম- পুড়ে পুড়ে মাটির হাঁড়ি পাতিল লালচে হওয়ার কথা। খালে বড় বড় নৌকা। মাচাং বাঁধা। বাবা, কাকা আর আশু জেঠা মিলে ওই হাঁড়ি-ডেকচি নৌকায় তুলত। তারপর সন্ধ্যা নদী, তারপর...। তারপর যে কোথায় ভেসে যেত বাবা-কাকারা! জানতাম না। বাবাকে শুধালে শুধু বলত, ‘ওসব জেনে তোর কাজ নেইরে বাবা! ও বড় কষ্টের কাজ, বড় অপমানের কাজ। তোরা দুই ভাই পড়াশোনা কর বাপ। মুক্তি নে।’ ‘কিসের মুক্তি বাবা?’ জিজ্ঞেস করলে বাবা কোনো উত্তর দিত না। শুধু বলত, ‘পড়ালেখা কর।’
এখানে বলে রাখা ভালো- ডাইরির সমতারিখের ব্যাপারটা আমি এড়িয়ে যাচ্ছি। সমতারিখের জটলায় মূল কাহিনীটায় ঘোঁট লেগে যাবে। তারপর বেশ কিছু পৃষ্ঠা জুড়ে সুধাকর বাবুর ব্যক্তি জীবনের ছুটকা-ছাটকা কিছু কথা। তার গাঁ-গেরামের কিছু স্মৃতি।
লিখেছেন- আমার দুই মাসিকে এক গ্রামে বিয়ে দেয়া হয়েছে। বড় মাসি মারা গেছে। ছেলে আছে একটা। বড় মেসো ধনী ধরনের। মেসো নাকি ভটকাদাকে বিয়ে করিয়ে দিয়েছেন। মেজ মাসি বেঁচে আছেন, মেসোও। মেজ মাসি মেসোর সঙ্গে নাকি ভটকাদার সম্পর্ক ভালো না। বড় যেতে ইচ্ছে করে মাসিদের বাড়ি। আগে খুব যেতাম। মা মারা যাওয়ার পর যাওয়া কমে গেছে।
আরেক জায়গায় লিখেছেন- সন্ধ্যানদীর পাড় ধরে বাঁধ। বাঁধের ওপর দিয়ে রাস্তা। বাঁধ থেকে নামলেই গ্রাম্য পথ। মাটির। গরু গাড়ির ক্যাঁ-ৎ, কোঁক। নৌকার মতো দুলতে দুলতে চলে। একবার এদিকে কাত, আরবার ওই দিকে। একবার চড়েছি তো গরু গাড়িতে! গরুর লেজ মোচড়াতে মোচড়াতে ভন্তুদা বলেছে- আমার বউ এসেছে গরুর গাড়িতে। তোর বউ আনব কিন্তু পালকিতে। বলেছি- পালকিতে! ভন্তুদা বলেছে- হ্যাঁ পালকিতে। বউ থাকবে ভেতরে। আর টোপরপরা তুই পালকির পাশে পাশে। ঘোমটা টানা বউয়ের পাশে পাশে রুমালমুখো সুধাকর! কী, কেমন মজা! না?
কয়েক পৃষ্ঠা পর আছে-
আজ হাবিজাবি কত কথা যে মনে পড়ছে। অলকার কথা বেশি করে মনে পড়ছে। ছোট বেলায় কত না বন্ধুত্ব ছিল অলকার সঙ্গে! প্রতিদিন কোথাও না কোথাও নিয়ে যেত অলকা। সারাদিন টইটই, হইচই। একবার সন্ধ্যানদীর ধার তো, পরের বার মা ওলাওঠার থান। অন্যবার মদন হাটের চালা। সেই অলকার একদিন বিয়ে হয়ে গেল। দু’তিনটে গ্রামের পরে। বড় অভিমান হয়েছিল আমার। বিয়ে করলি ঠিক আছে, তাই বলে শ্বশুরবাড়িতে এ রকম করে ঢ্যাং ঢ্যাং করে চলে যাওয়া! শুনেছি অলকার বর চাষবাস করে। সম্পন্ন চাষি পরিবার। অলকা তার বরকে নিয়ে একবার এসেছিল গ্রামে, আমাদের বাড়িতেও। কি হাসিখুশি তখন সে। গা কেটে সোনা গড়াচ্ছিল যেন। বরকে বলেছিল- ‘এ আমার সুধাকরদা। সুধা আমার।’ নির্লজ্জ অলকা! ফট ফট করে বলে দিল- সুধা আমার! এই অলকা মারা গেল একদিন।
আরেক তারিখে লেখা আছে-
বাবা মারা গেল। কাকা জেঠাদের জিভ লকলকিয়ে উঠল। আজ রাতের আঁধারে দুই ভাই পালিয়ে যাব।
এরপর পরপর অনেকগুলো পৃষ্ঠা খালি। এককালের সাদা পৃষ্ঠাগুলো হলদেটে হয়ে গেছে। একটা পৃষ্ঠাজুড়ে তো চায়ের দাগ। কোনো একদিন লিখতে বসেছিলেন বুঝি। পাশে কাপভর্তি চা। অন্যমনস্কতায় হয়তো কাপটি উলটে গিয়েছিল। বিরক্ত হয়েছিলেন নিশ্চয়। না হলে ওইদিন কিছু লিখলেন না। কেননা লেখার অন্য একটা কারণও থাকতে পারে। চায়ে ভিজে যাওয়া পৃষ্ঠায় লিখবেন কি করে?
বহু পৃষ্ঠা পরে এক জায়গায় দেখছি- ‘রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের দ্বিতীয় মহাভারত’ লিখেছেন।
পরের একটা পৃষ্ঠায় জানালেন- অনেকটা বছর লিখিনি। সময়টা গেছে যুদ্ধে। সেই যুদ্ধের বিবরণ এখানে বাহ্য। কত ঘাটের জল খাওয়া, শ্যাওলার মতো ভেসে চলা। কতজনের লাথিগুঁতা যে খেলাম। সুদিন এল। ভাইটি ইন্টারমিডিয়েট পাস করে মেডিকেলে ঢুকল। আমি চাকরি পেলাম, সরকারি কলেজে। ঠিকানা লেখা ৪৭ ব্রিকফিল্ড রোড, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম।
কোথায় বরিশালের মেহেন্দিগঞ্জ, কোথায় চট্টগ্রামের ব্রিকফিল্ড রোড! কোথাকার রুদ্র সুধাকর, কোথায় এসে ঠাঁই নিয়েছেন। কীভাবে এলেন, কীভাবেই বা থিতু হলেন, তার কোনো বর্ণনা নেই ডাইরিতে। শুধু অন্য একটি পৃষ্ঠায় লিখেছেন- এতদিন পরে পৃথিবীর দিকে তাকাতে ইচ্ছে করছে। লাইনটির শেষে বি. দ্র. দিয়ে লেখা- আজ প্রথম মাসের বেতন পেলাম। বছর দেড়েক পরে একটা পৃষ্ঠায় লিখেছেন- সুনন্দার সঙ্গে আমার বিয়ে হলো। সুধাকর-সুনন্দা- শুনতে বেশ ভালো না?
একদিনের পৃষ্ঠায় পাচ্ছি- বাপের পদবি রুদ্র, শৈলেশ রুদ্র। আমারও। লিখতাম সুধাকর রুদ্র। মেট্রিক সার্টিফিকেটেও তাই আছে। কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের কাছে বলে বেড়াতে লাগলাম- আমার নাম রুদ্র সুধাকর। গোটা চট্টগ্রাম শহরও জানল- আমার ওই নাম। হঠাৎ একদিন আমাকে চন্দনাইশের নিগমানন্দ আশ্রমে নিয়ে যওয়া হলো, বক্তৃতা দেয়ার জন্য। ধর্মসভায় বক্তৃতা। খুব বেশি জানাশোনা ছিল না আমার। যা জানি-বুঝি, বললাম। আমার মতো করেই বললাম। বাস্তব জীবনের উদাহরণ টানলাম বারবার। শ্রোতারা মুগ্ধ হলো। আমার বাজার খুলে গেল, ধর্মসভায় বক্তৃতা দেওয়ার বাজার। বাজার বলার একটা কারণ আছে। পরে পরে বক্তৃতার আহ্বান এলে আমি টাকা চেয়ে বসলাম- পাঁচ হাজার। সঙ্গে কখনো দামি চাদর, কখনো পাজামা-পাঞ্জাবি। চাইব না! ধর্মগুরুদের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে দক্ষিণা দেয় শিষ্যরা, কখনো টাকা ভর্তি হলুদ খাম। বক্তৃতা দিয়ে আমি গলা ফাটাই, ধর্মগুরুটি মঞ্চে সেগুন কাঠের চেয়ারটিতে বসে ডানহাতটা উঁচিয়ে চোখ মুদে বিড় বিড় করেন। পরে চোখ খুলে বলেন- কল্যাণ হোক তোমাদের। ওই একটা লাইনেই হলুদ খাম, রাশি রাশি টাকা! আমি বোকা থাকব কেন? চেয়ে বসলাম টাকা। আয়োজকরা টাকা দিতে কার্পণ্য করলেন না। টাকা তো আর তাদের যাবে না। দেবে তো বোকা ভক্তরা। ভালোই চলছে আমার জীবন। একদিকে অধ্যাপনা, অন্যদিকে ধর্মসভায় বক্তৃতা। দুদিক থেকেই টাকা আসে।
অন্য একটা তারিখে সংক্ষিপ্ত লেখা- বিপিন হোস্টেলে থাকে। পড়ে চট্টগ্রাম মেডিকেলে। মেডিকেল থেকে ব্রিকফিল্ড রোড বেশি দূরে নয়। বলি- বাসা থেকেও তো কলেজ করতে পারিস তুই। বিপিন বলে- হোস্টেলে সুবিধা দাদা। বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করে পড়তে সুবিধা। বলি- ঠিক আছে।
কিন্তু ইদানীং বিপিনের আনাগোনা বেড়ে গেছে। বিশেষ করে আমার বিয়ের পর, সুনন্দা ঘরে আসার পর। জিজ্ঞেস করি, কিরে বিপিন, আজ বুঝি কলেজ বন্ধ! বিপিন মাথা চুলকে আমতা আমতা করে বলে, এ্যাঁ, হ্যাঁ দাদা। ছাত্রদের মধ্যে মারামারি লাগল, কলেজ বন্ধ হয়ে গেল। বলি, অঁ-! আমি সভাসমিতিতে চলে যাই বিপিন ঘরে থাকে।
প্রায় ছ’মাস কিছু লিখেননি রুদ্র সুধাকর। হঠাৎ একদিন একটা পৃষ্ঠায় লিখলেন-
জগতের অন্ধকার আর মনের অন্ধকারের ফারাক বিস্তর। জগতের অন্ধকার ছানাকাটা। চোরাগোপ্তা নষ্ট আলোর ছাঁট। মনের আঁধার তাজা। অন্ধকারের জন্যই যে অন্ধকার। এ অন্ধকার ওয়াট মাপা আলো নিভে যাওয়ার অন্ধকার নয়, সূর্যডোবা অন্ধকার। মনের অন্ধকার আলোর উচ্ছিষ্ট নয়। জগতের অন্ধকারের ভেতর রাতের গন্ধ থাকে। রাতের গন্ধ কেমন জানি না। কিন্তু আমার মনের আঁধার গহন। এই গহন অন্ধকারের ঘ্রাণ আছে, শব্দও আছে। এই অন্ধকার শিশিরের মতো টুপটাপ টুপটাপ করে ঝরে পড়ে। আমি আমের মতো অন্ধকার কুড়িয়ে যাচ্ছি। এই অন্ধকার কুড়োনো বড় কষ্টের। এই অন্ধকার হাতে তুলে নিলে জল হয়ে যায়। মুখের ভেতর রাখলে গলা উগলানো তেতো।
সুধাকর বাবুর কবিতার মতো করে লেখা এই অংশটি পড়ে আমি থমকে গেছি। অন্ধকার নিয়ে এ রকম করে ভাবা, লিখা! কার মনের অন্ধকার রাতের অন্ধকারকেও হার মানাচ্ছে! কী জন্য লিখলেন তিনি এ রকম করে? আরেকদিন ভীষণ একান্ত ব্যক্তিগত কিছু কথা লিখলেন। আগের দিনের মতো হেঁয়ালি করে নয়, পষ্টাপষ্টি। লিখেছেন- কোমরে প্রচ- ব্যথা। দাঁড়াতে পারি, বসতেও কোনো অসুবিধা নেই। হাঁটতে গিয়েও ব্যথা লাগে না, দৌড়ালেও তাই। কিন্তু যত ব্যথা কোমর দোলাতে গিয়ে। কনকনে ব্যথা। যেন হাজারে হাজারে পিন ফুটছে কোমরে। ব্যথাটা এমনি এমনি হয়নি। ধর্মসভায় যাচ্ছিলাম পটিয়ায়। মাইক্রোবাসে ড্রাইভারের পাশে বসেছিলাম। পেছনে অন্যরা সামনে দিয়ে হঠাৎ একটা বলদ দৌড় দিল। ড্রাইভার ব্রেক কষল জোরসে। আচমকা কোমরে চাপ পড়ল আমার। তখন তখন বুঝতে পারিনি। বাসায় ফিরলে সামান্য ব্যথা। বিপিন বড় ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল। পরীক্ষা নিরীক্ষার পর ডাক্তার বললেন, মেরুদ-ের একটি মালাতে আরেকটি মালা বসে গেছে। অপারেশন করলে সারতে পারে, তবে নিশ্চয়তা নেই, বিপদের সম্ভাবনা। আমার তো তেমন অসুবিধা হচ্ছে না! অপারেশনের চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেললাম।
রাতে শরীর গরম হয়। মনটা আঁকুপাঁকু। আমি সুনন্দার শরীরে হাত রাখি। আমরা লীলায় মাতি। গন্তব্যে পৌঁছাতে তো কোমর দোলাতে হয়। এক দুলুনিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত। আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে মারে...। সুনন্দা পাশ ফিরে শোয়। আমি বারান্দায় যাই। আমার চোখে কি জল? এভাবে কাটে দীর্ঘদিন, অনেকগুলো রাত। সপ্তাহ, মাস, বছর।
আরেকদিন রুদ্র সুধাকর লিখেছেন- দাম্পত্যজীবনের সবচাইতে বড় শক্তির নাম ভালোবাসা, সবচাইতে বড় শত্রুর নাম সন্দেহ।
বছর দেড়েক পর একদিন লিখলেন- আজ রাতে সুনন্দা জানালো তার বাচ্চা হবে। অন্তঃসত্ত্বা সে। কিন্তু আমি, আমি যে অক্ষম! গত দেড়-পৌনে দুই বছর ধরে যে সুনন্দার সঙ্গে আমার দেহগত সম্পর্ক নেই। এ বাচ্চা কার?
পরের পৃষ্ঠাগুলো জুড়ে লেখার পর লেখা। নানা লেখা। কলেজের কথা। ছাত্রছাত্রীদের কথা। ধর্মসভার কথা। তার নিজের পদোন্নতির কথা। যেদিন যা লিখতে ইচ্ছে করেছে, লিখে গেছেন। কিন্তু একবারের জন্যও স্ত্রী বা সন্তান অথবা ভাই বিপিনের কথা লিখেননি।
বহু বছর পর এক স্থানে লিখলেন- এখন আমার দুজন পুত্র। সুলাল আর দুলাল। সুলাল মেডিকেলে, দুলাল স্কুলে, নাইনে। বিপিনকে বিয়ে করিয়েছি। একই ফ্ল্যাটে থাকি। তার ঘরে একটা মেয়ে।
একই পৃষ্ঠায় আবার লিখেছেন- সুলাল-দুলালের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি। দুজনের চেহারা কাছাকাছি। দেখতে একেবারে বিপিনের মতো।
বছর চারেক পরে লিখলেন- রিটায়ারমেন্টে এলাম। সুনন্দা সুলালকে বিয়ে করানোর জন্য তোড়জোড় করছে। ইদানীং তিলকের ফোঁটা কাটে সুনন্দা, কপাল থেকে নাকের আগা পর্যন্ত। মন্দিরে বসে চোখ বুজে ওঁ ওঁ করে।
বেশ কিছুদিন পর একদিন লিখলেন- সুলালের বাচ্চা হয়েছে। ছেলে। বিপিনের মতো দুলালেরও অধিকাংশ সময় কাটে ঘরে। আমি থাকি আমার রুমে, সুনন্দা রান্নাঘর অথবা মন্দিরে।
ডাইরির শেষ পাতাটা এ-ই লিখেই শেষ করেছেন রুদ্র সুধাকর। শান্তনুপুত্র চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য, সত্যবতীর ঘরে। ওরা ছিল শান্তনুর আসলপুত্র, মানে শান্তনুর ঔরসে জন্ম তাদের। চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্যের বউয়ের নাম যথাক্রমে অম্বিকা আর অম্বালিকা। সন্তান জন্মদানের আগেই চিত্রাঙ্গদ গন্ধর্বরাজের হাতে নিহত হয়। শান্তনুর মৃত্যুর পর চিত্রাঙ্গদ রাজা হয়েছিল। চিত্রাঙ্গদের পরে রাজা হলো বিচিত্রবীর্য। বিচিত্রবীর্য যক্ষ্মা রোগী ছিল। সন্তান জন্ম দেওয়ার আগে তারও মৃত্যু হয়। মা সত্যবতী দিশেহারা। ঘরে যুবতি পুত্রবধূরা। বংশধারা বিলুপ্তপ্রায়। সত্যবতী আগের স্বামীর সন্তান ব্যাসকে ডেকে আনল। ভ্রাতৃবধূদের গর্ভে সন্তান উৎপাদন করতে বলল। বধূরা অসহায়। ব্যাসের বীভৎস দেহের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হলো অম্বিকা-অম্বালিকাকে। অম্বিকা আর অম্বালিকার ঘরে জন্ম নিল ধৃতরাষ্ট্র এবং পা-ু। সন্তান বটে, অবৈধ।
একটু গ্যাপ দিয়ে অন্য প্যারায় রুদ্র সুধাকর লিখেছেন- সুনন্দারও দুই পুত্র- সুলাল-দুলাল। কার ঔরসে? বিপিন নামের ব্যাসের ঔরসে?
সুলালের ছেলে হয়েছে। দুলাল ঘরে থাকে, সুলাল চাকরিতে। সন্তানটি কার? দুলালের নয় তো?
শেষ প্যারায় লিখেছেন- বেঁচে থাকার দায় বড়। এ রকম করে দেখে যাওয়ার চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়।
পাঠকবৃন্দ, প্রথম প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল কি?