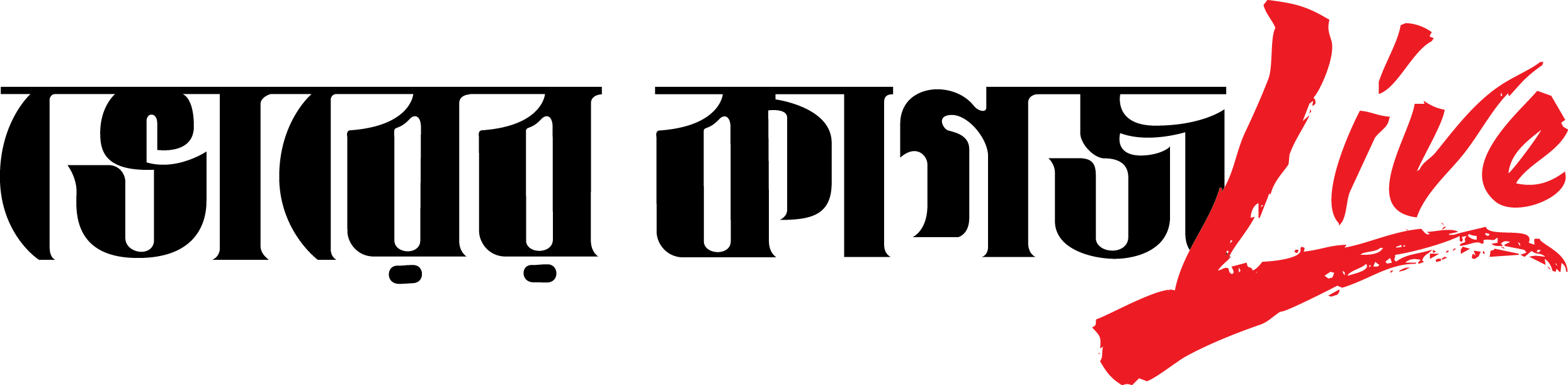আলোতে অন্ধকার এবং অন্ধকারে আলো
কাগজ প্রতিবেদক
প্রকাশ: ০৮ মে ২০১৯, ০৮:৪৪ পিএম
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা আর যা করল সেটা হলো বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি। শিক্ষিত লোকেরা আলাদা হয়ে গেল অশিক্ষিত লোকদের কাছ থেকে। এর প্রধান কারণ যে শিক্ষা তাও নয়, প্রধান কারণ ভাষা। ইংরেজি-শিক্ষিতদের মধ্যে ইংরেজির জ্ঞান নিয়ে জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে একটি দাম্ভিক অহমিকা গড়ে উঠল, যার ফলে তারা আর আপনজনদের আপন রইল না, পর হয়ে গেল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কায়েম করা হয়েছিল ১৭৯৩ সালে; কৃষকের জন্য অত্যন্ত নিষ্ঠুর, জোয়ালের মতো হিংস্র এই ব্যবস্থা সম্পর্কে শিক্ষিতরা অধিকাংশই রইল উদাসীন, কেউ কেউ হয়ে পড়ল এর সমর্থক।
একই বছরের ঘটনা, ১৮৫৭-এর। কলকাতায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং কলকাতার অনতিদূরে, ব্যারাকপুরে, সিপাহি অভ্যুত্থান। প্রথমটি ঘটল জানুয়ারি মাসে, দ্বিতীয়টি মার্চে। দুই মাসের ব্যবধান। স্থানের দিক থেকেও দূরে নয় ব্যারাকপুর, কলকাতা থেকে। কাছেই। কিন্তু স্বভাবে ও চরিত্রে ঘটনা দুটি খুবই দূরবর্তী, পরস্পর থেকে। বিশ্ববিদ্যালয় কেমন প্রতিষ্ঠান, কী তার কাজ সে আমরা জানি। তাকে চিহ্নিত করা সহজ। কিন্তু সিপাহি অভ্যুত্থান? না, তার চরিত্র ততটা স্পষ্ট চিহ্নিত করতে গেলে দ্বিধার সৃষ্টি হয়। সিপাহিরা শিক্ষা-দীক্ষার সঙ্গে যুক্ত ছিল না, তাদের অধিকাংশই ছিল অশিক্ষিত কৃষকের সন্তান; উর্দি পরে সিপাহি হয়েছে। পশ্চাৎপদ ছিল তারা ধ্যান-ধারণায়। মোটেই আলোকিত নয়। ওদিকে বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু, উজ্জ্বল এবং আলোকিত। তার মুখ বিশ্বের দিকে, সিপাহিরা আত্মমুখী।
এ পর্যন্ত কথাগুলো বলা গেল এক নিঃশ্বাসে। তবে তারপরই প্রশ্ন দেখা দেয়। আলো যাকে বলছি তার নিচে কি অন্ধকার ছিল না? অন্ধকার যাকে মনে হচ্ছে তার অন্তরালেও কি ছিল না আলো? ঘটনা দুটো বেশ জটিল- ওই কারণেই।
বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোর দিকগুলো তালিকাভুক্ত হতে বিলম্ব করে না, একের পর এক তারা এসে যায়। প্রথম কথা, বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে শিক্ষার অতি উচ্চ প্রতিষ্ঠান। দ্বিতীয় কথা, সে বিশ্বমুখী, বিশ্বের যেখানে যা পায় যতটা পায় দ্রুত সে সংগ্রহ করে, সৃষ্টি করে নতুন জ্ঞান, বিতরণ করে তা অকাতরে। তৃতীয়ত, পরাধীন ভারতে সে এসেছিল বুর্জোয়া বিকাশের প্রতিশ্রুতি নিয়ে। চতুর্থত, সামন্তবাদ-কবলিত বঙ্গদেশে যে নবজাগরণ ঘটেছিল কলকাতাকে কেন্দ্র করে তার ঠিক কেন্দ্রে না হলেও আশপাশেই ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। সব মিলিয়ে যেন সকালের স্নিগ্ধ আলো।
এর বিপরীতে সিপাহি অভ্যুত্থানকে মনে হবে যেন মধ্যরাতের দুঃস্বপ্ন। মূর্তি সে অন্ধকারের, মুখ তার সামন্তবাদের দিকে ঘোরানো, যাত্রা তার পশ্চাৎমুখী। রেনেসাঁসের পক্ষে নয়, বিপক্ষে সে।
তবে একটু সতর্ক চোখে দেখার যা অপেক্ষা, দেখলে সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়বে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ প্রশংসিত আলোর নিচে হতভাগ্য বাঙালির জন্য অন্ধকার ছিল কেমন ভয়ঙ্কর। শুরুতেই লক্ষ করা যাবে যে, বিশ্ববিদ্যালয় এ দেশে আলো বিতরণের জন্য আসেনি, এসেছে তাঁবেদার সৃষ্টির জন্য। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমে পড়ানোর কোনো ব্যবস্থা ছিল না, তার একমাত্র কাজ ছিল পরীক্ষা নেয়া। এবং এখনো কেবল কলকাতায় নয়, উভয় বাংলার সব ক’টি বিশ্ববিদ্যালয়েরই প্রধান মাথাব্যথা শিক্ষা দান নয়, পরীক্ষা গ্রহণ করা। আর ওই যে তাঁবেদার শ্রেণি তৈরি করা সেই অভিপ্রায়টি পরাধীনতার যুগে যতটা পরিষ্কার ছিল এখন ততটা নয় বটে, তবে এখনো রাষ্ট্র চায় বিশ্ববিদ্যালয় স্বাধীনচেতা মানুষ নয়, বরঞ্চ অনুগত নাগরিকই সৃষ্টি করুক।
সিপাহি অভ্যুত্থানের লক্ষ্য ছিল একেবারেই উল্টো। সিপাহিরা তাঁবেদার হয়ে থাকবে এটাই ছিল তাদের চাকরির প্রথম শর্ত; কেনা গেলাম তারা; গোলামি করতে এসেছে। কিন্তু তারা তা করল না, করে বসল উল্টো কাজ, করল বিদ্রোহ। সিপাহিদের অভ্যুত্থানকে যতই পেছনমুখো বলে গাল পাড়ি না কেন তার অভিপ্রায়টা ছিল অত্যন্ত আধুনিক। সে চেয়েছে ইংরেজ শাসনের অবসান। চেয়েছে স্বাধীনতা। সিপাহিরা চাইল স্বাধীনতা, শিক্ষিত মানুষেরা চাইল পরাধীনতা। কোনটা ভালো কোনটা মন্দ বিচার করব কি করে? আলোর দরকার আছে; জ্ঞান চাই, বিকাশ চাই বুর্জোয়া ধরনের, ছিন্ন করা চাই সামন্তবাদের শীতল বন্ধন। সবই সত্য। কিন্তু এই আলো, এই বিকাশ, এই মুক্তি এরা যদি পরাধীনতাকে পোক্ত করে তাহলে তাদের কি করে বলি অবিমিশ্র আশীর্বাদ? বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদানকে খাটো করার কোনো অবকাশ নেই। সে আলো দিয়েছে, এমনকি বিদ্রোহ করতেও শিখিয়েছে, কিন্তু তার ভেতরে যে অন্ধকারটা ছিল তাকে যেন না ভুলি। সেই অন্ধকার সে বহন করেছে, এখনো যে মুক্ত হয়েছে তা নয়।
সিপাহি বিদ্রোহের ঠিক পরের বছর, ১৮৫৮-তে কোম্পানির শাসন শেষ হয়, শুরু হয় মহারানী ভিক্টোরিয়ার কর্তৃত্ব। সেই নতুন ব্যবস্থার একটা সামরিক ভিত ছিল, ছিল তার অত্যন্ত শক্ত একটি আমলাতান্ত্রিক কাঠামো; সঙ্গে এবং ভেতরে ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাও। এই শিক্ষার ক্ষতিকর দিকগুলোকে আমরা যেন অবজ্ঞা না করি। কেননা মোটেই তারা সামান্য নয়। প্রথম ব্যাপার তো এটাই যে, এ শিক্ষা আমাদের স্বাধীনচেতা হতে উদ্বুদ্ধ করেনি। বরঞ্চ নত করে দিয়েছে ভেতর থেকে। আমরা পরাধীন জাতি, ইংরেজরা অতিউচ্চ স্তরের মানুষ, দেখছ না কেমন উজ্জ্বল তারা গায়ে-গতরে, শিক্ষা-দীক্ষায়, তারা আমাদের অনন্তকাল শাসন করবে- এই কথাটা অজস্র ধারায় প্রবেশ করেছে আমাদের চেতনায়। আমরা নত হয়েছি, হীনমন্যতায়। সাধারণ শিক্ষার্থী কোন ছাড়, বড় বড় ঐতিহাসিকরা (বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক) যা যা করছেন সেটা স্মরণ করলে এখনো হৃদকম্প উপস্থিত হয়, শিক্ষিত সমাজের হীনতার কথা স্মরণ করে। স্যার যদুনাথ সরকারকে ছোট ঐতিহাসিক বলবে কোনো দুঃসাহসী? খুব বড় ঐতিহাসিক ছিলেন, ছিলেন শিক্ষক, উপাচার্য ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত History of Bengal-এর দ্বিতীয় খণ্ড তিনি সম্পাদনা করেন; এর শেষ প্রবন্ধটি তাঁরই লেখা। এতে তিনি ইংরেজের বঙ্গদেশ অধিকারের অঘটনঘটনপটিয়সী মুহূর্তটির কথা উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, প্রায় দার্শনিক হেগেলের ভাষা ও ভঙ্গিতে, বঙ্গভূমি যেন নিজের অজ্ঞাতে যুগ-যুগান্তর ধরে এই পরিণতির লক্ষ্যেই অগ্রসর হচ্ছিল। তাঁর চমৎকার ইংরেজি বক্তব্যের বাংলা করলে এই রকম দাঁড়ায় : ইংরেজ আগমনের ফলে ‘একটি স্থবির প্রাচ্য সমাজের শুকনো হাড়গুলো যেন নতুন জীবন পেল, ঈশ্বর-প্রেরিত এক জাদুকরের ঐন্দ্রজালিক কাঠির স্পর্শ পেয়ে।’ দখলকারী নয়, জাদুকর; লুণ্ঠনকারী নয়, ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ- এই হলো ইংরেজের পরিচয়। অশিক্ষিত সিপাহিরা যাদের দস্যু বলে চিনে ফেলেছে, স্যার যদুনাথরা তাদের বলেছেন রেনেসাঁস সৃষ্টির জন্য প্রেরিত-পুরুষ। তথাকথিত ওই রেনেসাঁসের মূল্যায়ন করতে গিয়ে যদুনাথ সরকার বলেছে, ‘এ ছিল ইউরোপীয় রেনেসাঁসের চেয়েও বিস্তৃত, গভীর এবং বিপ্লবী।’ এই প্রবন্ধ তিনি ইংরেজ শাসনের মধ্যাহ্ন আলোতে লেখেননি, লিখেছেন তার অস্তমিত হওয়ার সন্ধ্যায়, ১৯৪৭-এ, আগস্ট মাসের পর অক্টোবর। অর্থনৈতিক নিঃশেষকরণ দেখলেন না, পরাধীনতার দগদগে ঘাগুলো দেখলেন না, দেখলেন কথাকথিত রেনেসাঁস, যা আদৌ কোনো রেনেসাঁস ছিল না। রেনেসাঁসের প্রধান কথা মুক্তি, পরাধীন দেশে যে মুক্তি কোনোভাবেই সম্ভবপর নয়।
যদুনাথ সরকার ব্যতিক্রম নন। তাদের যা বক্তব্য অধিকাংশ শিক্ষক ও শিক্ষিত ব্যক্তিরও বক্তব্য সেটাই। এরা মনে করেন, আমাদের দেশের যত যত উন্নতি সব বিদেশিদের কারণেই- আর্য, মোগল-পাঠান, ইংরেজ, আমেরিকান, এরা সবাই এসে আমাদের ধন্য করেছে এবং স্থায়ী ও প্রভূত উপকার করে রেখে গেছে। সিপাহিরা এবং সচেতন ছাত্ররাও এসব শিক্ষকের পরামর্শ শোনেনি। তারা আন্দোলন করেছে স্বাধীনতার জন্য। তাদের আন্দোলনেই দেশ স্বাধীন হয়েছে। যদুনাথ সরকারদের পরামর্শ শুনলে আমাদের যুগ যুগ ধরে পরাধীন থাকতে হতো।
আত্মসমর্পণের পরামর্শ দেয়ার দৃষ্টান্ত স্থাপনের কোনো অবধি ছিল না। ধরা যাক, রমেশচন্দ্র মজুমদারের কথা। ইনিও একজন বড়মাপের ঐতিহাসিক, History of Bengal-এ প্রথম খণ্ড তিনি সম্পাদনা করেন এবং এক সময়ে উপাচার্য ছিলেন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের। তার সম্পর্কে তারই এক সময়ের ছাত্র বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির প্রয়াত নেতা খোকা রায় উল্লেখ করেছেন ‘সংগ্রামের তিন দশক’ বইতে। ১৯৩০ সালের ২৬ মার্চকে কংগ্রেস স্বাধীনতা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। সেদিন খোকা রায় ও অন্য কয়েকজন ছাত্র একটি ছাত্রাবাসে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করেন। ছাত্রাবাসের প্রভোস্ট ছিলেন রমেশচন্দ্র মজুমদার। তিনি বাধা দিলেন এবং সেখানেই থামলেন না, খোকা রায় ও তার এক বন্ধুকে হল থেকে বহিষ্কার করে দিলেন। খোকা রায় লিখেছেন, ‘আমাদের এই প্রভোস্ট ব্রিটিশের ধামাধরা ও স্বাধীনতা আন্দোলনের ঘোরতর বিরোধী বলে সুপরিচিত ছিলেন। সরকারের গোয়েন্দা বিভাগের সঙ্গেও তার যোগাযোগ ছিল বলে একটা কথা তখন ঢাকার বামপন্থি রাজনৈতিক মহলে চালু ছিল। তাই আমাদের ওপর তার স্বেচ্ছাচারী আদেশে আমরা বিক্ষুব্ধ হলেও বিস্মিত হই নাই। কিন্তু খুব অবাক হয়েছিলাম, যখন আট বছর পরে জেল থেকে বের হয়ে দেখেছিলাম যে আমাদের সেই হলের ব্রিটিশভক্ত, স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধী প্রভোস্ট ভদ্রলোক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের একজন অথরিটি হিসেবে কংগ্রেসের উচ্চ মহলে সমাদর লাভ করেছিলেন।’
ক্ষুব্ধ খোকা রায় মন্তব্য করেছেন, ‘এটাই বোধ হয় বুর্জোয়া সমাজের নিয়ম।’ তার মন্তব্যের সঙ্গে যোগ করতে হয় যে, না, ঠিক বুর্জোয়া সমাজের নয়, এটা হচ্ছে পরাধীন দেশের বুর্জোয়া সমাজের নিয়ম। এসবই মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াদের কীর্তি, জাতীয় বুর্জোয়াদের নয়। মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ারা দালালি করে এবং দালালদের পছন্দ করে। ইংরেজের বিশ্ববিদ্যালয় ছিল আসলে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। তার সমগ্র অভিপ্রায়টিই ছিল রাষ্ট্রনৈতিক- রাষ্ট্রের স্বার্থে সজ্জিত ও বিন্যস্ত। সেই স্বার্থ যে উদ্ধার হয়নি সেটাইবা কেমন করে বলি।
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা আর যা করল সেটা হলো বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি। শিক্ষিত লোকেরা আলাদা হয়ে গেল অশিক্ষিত লোকদের কাছ থেকে। এর প্রধান কারণ যে শিক্ষা তাও নয়, প্রধান কারণ ভাষা। ইংরেজি-শিক্ষিতদের মধ্যে ইংরেজির জ্ঞান নিয়ে জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে একটি দাম্ভিক অহমিকা গড়ে উঠল, যার ফলে তারা আর আপনজনদের আপন রইল না, পর হয়ে গেল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কায়েম করা হয়েছিল ১৭৯৩ সালে; কৃষকের জন্য অত্যন্ত নিষ্ঠুর, জোয়ালের মতো হিংস্র এই ব্যবস্থা সম্পর্কে শিক্ষিতরা অধিকাংশই রইল উদাসীন, কেউ কেউ হয়ে পড়ল এর সমর্থক।
জাতীয়তাবাদের শিক্ষাও বিশ্ববিদ্যালয়ই দিয়েছে। এর ফল শুভ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু হলো না; কেননা এর মধ্যে প্রবেশ করল সাম্প্রদায়িকতা। শিক্ষিত-অশিক্ষিতের যে বিভাজন তার চেয়েও মারাত্মক হয়ে প্রকাশ পেল সাম্প্রদায়িক ভেদরেখা। জাতীয়তাবাদ শেষ পর্যন্ত রূপ নিল সাম্প্রদায়িকতার। দূর থেকে দেখলে মনে হবে ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য, কিন্তু ঘটনা তো সত্য। সাম্প্রদায়িকতা অশিক্ষিত লোকদের পীড়া নয়, এ হচ্ছে শিক্ষিত লোকদের সংক্রামক ব্যাধি, তারাই তৈরি করেছে, তারাই সংক্রমিত করেছে দেশব্যাপী। জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে নয়, সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে ভাগ হয়েছে ভারতবর্ষ; তবু আজো সেই সাম্প্রদায়িক সমস্যার নিরসন হয়নি।
উল্টো দিকে, অর্থাৎ সিপাহি অভ্যুত্থানের ক্ষেত্রে আমরা কি দেখি? দেখি আপাততের অন্ধকার ভেদ করে ঠিকরে পড়েছে আলো, সে আলো সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার।
(প্রবন্ধের বাকি অংশ পড়ুন আগামী বৃহস্পতিবার)
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।