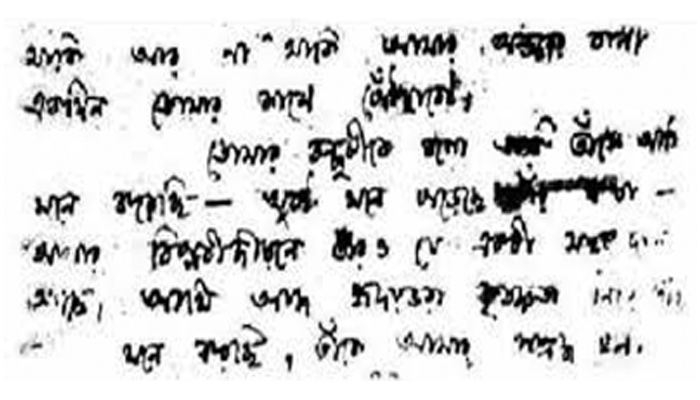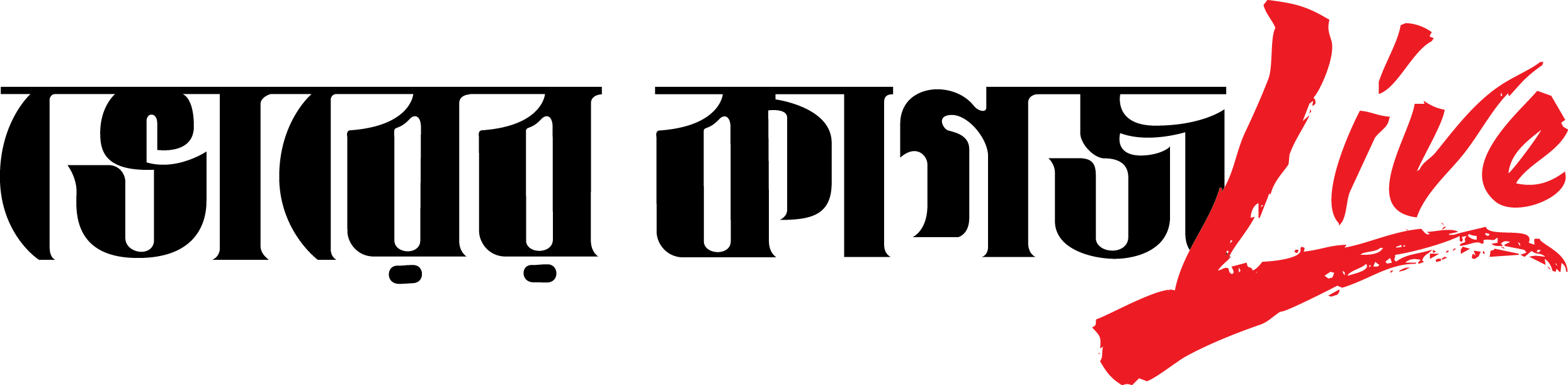পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাবে আনন্দ উৎসবে মত্ত ইংরেজদের ওপর সশস্ত্র আক্রমণ করার প্রথম নির্ধারিত তারিখ ছিল ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল। কিন্তু সেদিন ‘গুড ফ্রাইডে’র ছুটি থাকায় ক্লাব বন্ধ ছিল। কর্মসূচিটি বাতিল হয়ে যায়। এরপর পুনরায় এই কর্মসূচির তারিখ ও সময় নির্ধারণ করা হয়েছিল ১৯৩২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর রাত ১০টায়। নেতৃত্বের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল প্রীতিলতাকে। কাট্টলীর সমুদ্রতীরে প্রীতিলতা ও অন্যান্য বিপ্লবী আক্রমণকারীকে যথাযথ অস্ত্রশিক্ষা দেয়া হয়েছিল। নির্বাচিত অন্য আর যেসব বিপ্লবী সদস্য তাঁর সঙ্গে ছিলেন, তাঁরা হলেন শান্তি চক্রবর্তী, কালী দে, প্রফুল্ল দাস, সুশীল দে, মহেন্দ্র চৌধুরী, বীরেশ্বর রায় ও পান্না সেন। অভিযানের সামরিক পোশাক পরা তো ছিলই, উপরন্তু প্রীতিলতার কোমরে ছিল চামড়ার কটিবন্ধে গুলিভরা রিভলবার, খাপে ভরা গোর্খাদের ভোজালি, পায়ে মোজা ও বাদামিরঙা রাবার সোলের জুতা। মাথার দীর্ঘ কেশরাশিকে সুবিন্যস্ত করে তার ওপরে বাঁধা সামরিক কায়দার পাগড়ি। অন্যান্য অভিযাত্রীর হাতে ছিল রাইফেল, রিভলবার, ভোজালি ও বোমা। ক্লাবের একজন বাবুর্চির সহায়তায় এই অভিযাত্রীরা সব খবর আগেভাগেই জেনে গিয়েছিলেন। সফলভাবে অভিযান শেষ করে দলের নেতা হিসেবে প্রীতিলতা সবাইকে বের করে নিজে বের হলেন শেষে। সবাই নির্বিঘ্নে চলে গেলেন। কিন্তু হঠাৎ একটি গুলি এসে প্রীতিলতার বুকে লাগে। তিনি রক্তাক্ত অবস্থায় শত্রু র হাতে বন্দি এড়াতে সায়ানাইড (বিষ) খেয়ে আত্মাহুতি দিলেন।
সেই যুগের প্রথম নারী-বিপ্লবী শহীদের প্রাণহীন দেহ অনেকক্ষণ ধরে রাস্তায় পড়ে ছিল। পুলিশ, মিলিটারি ও গোয়েন্দা কর্মচারীরা পোস্টমর্টেম রিপোর্ট দেয়ার সময়। দেখেন সামরিক পোশাক পরিহিত মৃতদেহটি একজন নারীর। মৃতদেহের সঙ্গে পাওয়া গিয়েছিল : ১. মাথার পাগড়ি, ২. পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাবের প্ল্যানচার্ট ১টি, ৩. একটি হুটসিন, ৪. প্রীতিলতার ফটোসহ ভারতীয় রিপাবলিকান আর্মির চট্টগ্রাম শাখার সভাপতি সূর্য সেন স্বাক্ষরিত লাল রংয়ের ১টি ইশতেহার, ৫. প্রীতিলতার নিজ হাতে লেখা বিবৃতি। প্রথম নারী শহীদ প্রীতিলতার আদর্শ আজো উদ্দীপ্ত করে চলেছে বাংলাদেশের গণতন্ত্রী, সমভাবে বিপ্লবী ভাবধারার নারী-পুরুষকে।
পরদিন ২৫ সেপ্টেম্বর ভোরবেলা ঘুম থেকে বাড়ির সবাই জেগে উঠে দেখেন বাইরের উঠানে প্রীতিলতার বাবা পাগলের মতো ছোটাছুটি করছেন আর কেঁদে কেঁদে আর্তনাদ করে বলছিলেন, ‘তোমরা সকলে শোনো, কাল রানী পুলিশের সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রাণ হারিয়েছে।’ রানী, রানী বলে বাবা কাঁদছিলেন। মা মূর্ছা যেতে যেতে আছাড় খেয়ে পড়লেন।
পুলিশ এসে প্রীতিলতার বাবাকে কোতোয়ালি থানায় নিয়ে যায়। প্রীতিলতার বুকে বুলেটের রক্তাক্ত জখম ছিল, নিজ হাতে লেখা ছোট একটা বই, শ্রীকৃষ্ণের ছবির সঙ্গে একটা লেখাও ছিল তাঁর মৃতদেহের সঙ্গে।
সুন্দর ইংরেজিতে লেখা তাঁর একটি বিবৃতি ছিল। বিবৃতির শেষের দিকে লেখা ছিল, I sacrifice myself in the name of God whom I have adored for years.
রক্তাক্ত কাপড় সরিয়ে বাবা খুবই সাবধানে একটি নতুন শাড়ি এনে পরিয়ে দিলেন প্রীতিলতার দেহে।
‘...পুলিশের হাতে ধরা পড়ে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে হবে এটাই ছিল প্রীতিলতার আতঙ্ক। এ নিয়ে মাস্টারদার সঙ্গে তার নাকি তর্কও হয়েছিল বেশ কয়েক দিন। কিছুতেই পুলিশের হাতে ধরা দেবেন না তিনি। তাই সব সময় পটাশিয়াম নিয়ে চলাফেরা করতেন। তিনি বলতেন, ‘নরপশু ওরা, ওদের হাতে ধরা পড়লে থাকবে না আমার সম্মান।’ মৃত্যুকে ভয় করতেন না।
তিনি, ভয় করতেন অপমানকে, অসম্মানকে। সামান্য আহত হতেই তাই তিনি বিষ খেয়েছিলেন।
‘তা ছাড়া তাঁর ইচ্ছা ছিল, তাঁর আত্মদানে বাংলার নারীসমাজ সচেতন হয়ে উঠবে, মেয়েদের প্রাণে এনে দেবে উৎসাহ ও আত্মবিশ্বাস। ...প্রায় সপ্তাহখানেক পরে... পুলিশ এসে ঘিরে ফেলল আমাদের বাড়ি। চলল অনুসন্ধান প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে। পুলিশের নিত্য আগমন ও অত্যাচার। ...অগ্নিযুগের আগুনের ছোঁয়া একটু পেয়েছিলাম কৈশোরে এটাই আমার গর্ব। ...হাসপাতালের শব ব্যবচ্ছেদের পর বাবা চুক্তিপত্রে সই করে মৃতদেহ সৎকারের জন্য নিয়ে আসেন। চুক্তিপত্রে ছিল কোনো শোভাযাত্রা চলবে না, পনেরো জনের অধিক লোক শ্মশানে যেতে পারবে না।...দিদির শবযাত্রা! তাতে কোনো স্লোগান ছিল না। শুধু গুটিকয়েক লোক চোরের মতো চুপি চুপি দিদিকে নিয়ে গেছে শ্মশানের দিকে। দিদির মৃত্যুর পর আমাদের পিতা-মাতা, ভাই-বোন সবাইকে পরিত্যাগ করেছিল। কারো ছিল পুলিশের ভয়, কারো ছিল চাকরির মায়া।’ প্রীতিলতার ছোট বোন শান্তি চৌধুরীর বক্তব্য থেকে প্রীতির মৃত্যু-পরবর্তীকালের এই ছিল চালচিত্র।

স্মৃতিকথায় প্রীতিলতা
কল্পনা দত্ত
পাহাড়তলী স্টেশনের কাছে পাহাড়তলী রেলওয়ে ক্লাব। প্রতি শনিবার সাহেব-মেমরা জমায়েত হয় সেখানে। চলে খানাপিনা, নাচ-বাজনা। এভাবে কিছুক্ষণ ফুর্তি করার পর যে যার আপন নিবাসে চলে যায়। ১৯৩২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর ছিল এমনই এক শনিবার। রাত ৯টায় আটজন ছেলে হানা দেন প্রীতি ওয়াদ্দেদারের নেতৃত্বে, নির্বিঘ্নে সবাই পালিয়ে যায়, কিন্তু প্রীতি ফিরে গেলেন না, খেয়ে নিলেন পটাশিয়াম সায়ানাইড।
ক্লাব-ঘরের দশ গজ দূরে গিয়ে সে পড়ে গেল। একটি বোমার টুকরোয় তার বুকের জামাটাও রক্তাক্ত হয়ে আছে। হঠাৎ ক্লাবের ভেতরে সব ফুর্তি কোলাহল থেমে গেল, সঙ্গে সঙ্গে উঠল আর্তনাদ এবং বোমা ও গোলাগুলির শব্দ। সাহেব-মেম ইতস্তত ছোটাছুটি করে দরজা-জানালা দিয়ে বেরিয়ে পড়ার চেষ্টা করছে, আবার বাধা পেয়ে ছুটে আসছে ভিতরে।
মিনিট পনেরো পর দেখা গেল সব চুপচাপ কেবল আহতদের গোঙানি আর নিহত ও আহতদের রক্তে ঘরের গোটা মেঝেতে রক্তস্রোত বইছে।
এসবই প্রকাশিত হলো পরের দিন সংবাদপত্রে।
সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে অনেক ছেলের ফাঁসি হয়েছে, পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে ছেলেদের মৃত্যুর কথাও শোনা গেছে। অনেক। কিন্তু এই আন্দোলনে মেয়েদের স্থান ছিল না এতদিন, নেতারা তাদের দলে নিতে দ্বিধা করতেন। ১৯০৩ সালে মেয়েরা কিছু কিছু দলের গোপনীয় কাজে যুক্ত হলেও প্রত্যক্ষ কাজে মেয়েদের যুক্ত করা হয়েছে অনেক পরে। সংখ্যায় খুব কম নারী প্রত্যক্ষ বিপ্লবে অংশ নিয়েছিলেন।
প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের মৃত্যুতে জনসাধারণ দেখল, মেয়েরাও এসব কাজে পিছিয়ে থাকে না। আত্মদানে ছেলেদের থেকে তারাও কিছু কম নয়। কাজের পন্থা নিয়ে সমালোচনা কেউ কেউ করলেও প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারকে তাদের বীরকন্যা বলে চট্টগ্রামের জনসাধারণ স্মরণ করে। তার আত্মদানকে তারা শ্রদ্ধাঞ্জলি দেয়, বলে, পুলিশের হাতে ধরা দেয়নি সে।
আমি তখন জেলে প্রীতি তার কাজে লিপ্ত হওয়ার এক সপ্তাহ আগেই আমি ধরা পড়ে গেছি।
২৫ সেপ্টেম্বর জেলার গোয়েন্দা বিভাগের ইন্সপেক্টর সকালে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেই বললেন, ‘কাল প্রীতি মারা গেছে, বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে পাহাড়তলী ক্লাব আক্রমণ করার পর।’
...আমার অত কথা শোনার মন ছিল না, শুনতে পারছিলাম না।
ঘরে চলে এলাম। প্রীতির সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ছিল। যে চারজন মেয়ে আমরা এই দলে যোগ দিয়েছিলাম, তার মধ্যে দুজন শেষ পর্যন্ত চলে গেছে, ছিলাম শুধু আমি ও প্রীতি। মাস্টারদার মুখে শুনি প্রীতির আত্মহত্যার পেছনে উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণের কাছে প্রমাণ করা যে মেয়েরাও দেশের জন্য প্রাণ দিতে পারে, দেশের জন্য তারাও লড়তে পারে।
কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল, বেঁচে থেকে আরো অনেক বেশি কাজ সে করতে পারত।
প্রীতিকে জানি খুব ছোটবেলা থেকে, একই স্কুলে পড়ি দুজনে। ও পড়ে এক ক্লাস উপরে, আমি পড়ি এক ক্লাস নিচে। পরিচয় হয় প্রথমে ব্যাডমিন্টন খেলার সাথী হিসেবে।
স্কুলের নিয়ম অনুসারে আমাদের ক্লাস ফাইভে উঠলেই ব্যাডমিন্টন খেলা ও লাইব্রেরির বই ব্যবহার করা ইত্যাদির অধিকার জন্মাত। কিন্তু অধিকার জন্মালেই হয় না। কোর্ট ছেড়ে দিতে হবে বড় মেয়েদের জন্য, সেই জন্য টিফিনের সময় দুপুর রোদে আমি খেলতে চাইতাম। অসময়ে খেলার সাথী হিসেবে পেতাম ওকে। ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা এমনি করেই জমে উঠেছিল।
বড় ক্লাসে উঠে দুজনেই ‘গার্ল গাইড’-এ যোগ দিয়েছিলাম। আমরা বলতাম আমাদের উচিত ওই ওদের অর্থাৎ ব্রিটিশদের ভালো জিনিস সব শিখে নেয়া, আমাদের কাজে লাগবে। দুজনে জল্পনা-কল্পনা করতাম, আর ভাবতাম গাইডদের প্রতিজ্ঞাগুলো বদলে দিলে কেমন হয়! To be loyal to God and the King Emperor না বলে To be loyal to God and the Country হলে কেমন হয়!
‘গল্প প্রসঙ্গে ওর মুখে শুনতাম, ওদের বাড়িতে কেউ বিলিতি জিনিস ব্যবহার করে না, ওরা সবাই স্বদেশি জিনিস ব্যবহার করে। ওর কাছে মনে মনে ছোট হয়ে যেতাম। আমাদের বাড়িতে কাপড়চোপড় থেকে আরম্ভ করে সবই বিলিতি।
গল্প করতাম আমরা অনেক কিছুই, কিন্তু আমাদের আদর্শ কী, কী করব না করব সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা আমাদের গড়ে ওঠেনি তখনো। কোনো সময় আমরা বড় বিজ্ঞানবিদ হয়ে যাব মনস্থ করেছি বা মনে করেছি ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাঈ হবো, কোনো সময় বা হয়ে উঠেছি ঘোরতর বিপ্লবী! বিশ্ববিদ্যালয়ে ভালো স্কলার হয়ে রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ বৃত্তি নেয়ার পরিকল্পনা বহুবার হয়ে গেছে।’
[...] একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে। ১৯২৯ সালে গোয়েন্দা বিভাগের একটি সার্কুলার বেরোয়। তার প্রতিবাদে সব স্কুল-কলেজ করবে ধর্মঘট।
‘আমরা ছুটিতে বাড়ি এসেছি, খাস্তগীর স্কুলে পিকেট করলাম আমরা চারজন। এরপর থেকে স্কুলে বেড়াতে যাওয়া আমাদের বন্ধ হয়ে গেল। আমরা যেতে পারিনি, অন্য দুজন ঠিক স্কুলে গিয়ে আবার পূর্ব প্রতিষ্ঠা ফিরিয়ে নিল। প্রীতি আমাকে বলেছিল, নিশ্চয় ওরা সুরমাদি মিনিদির কাছে ক্ষমা চেয়েছে। আমরা দোষ করিনি, মরলেও ক্ষমা চাইতে পারব না।
এর পরে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন হয়ে গেছে। প্রীতি ঢাকা ইডেন কলেজ থেকে আইএ পাস করে বৃত্তি নিয়ে কলকাতায় বেথুন কলেজে চলে এলো। আমি বেথুন কলেজ থেকে ‘ট্রান্সফার’ নিয়ে চাটগাঁয় এসে পড়ার জন্য চেষ্টা করতে লাগলাম এবং চাটগাঁতেই রয়ে গেলাম, ফলে প্রীতির আগেই মাস্টারদার সঙ্গে আমার দেখা ও যোগাযোগ হয়েছিল।
প্রীতির ছিল অসম্ভব আত্মবিশ্বাস, তাই সে ভাবতেও পারত না কেউ ওকে অবিশ্বাস করতে পারে।
[...] ১৯৩২ সালে প্রীতির সঙ্গে মাস্টারদার প্রথম দেখা হয় ও তখন বিএ পরীক্ষা দিয়ে চাটগাঁয়ে চলে এসেছে। প্রীতির কথা বলতে গিয়ে মাস্টারদা এক কথায় বলেছিলেন, ‘অমন মেয়ে আর আমি দেখিনি। দুটো জিনিসের এত সুন্দর সামঞ্জস্য আর কোথাও মেলে না। ও যেমন ফুর্তিবাজ, তেমনি ধীরস্থির আবার চিন্তাশীল। কোমলে কঠিনে মিলে ও অনন্য।’
ওর জীবনেরই একটি ঘটনা। মাস্টারদাদের সঙ্গে ও দেখা করতে গেছে ১৯৩১ সালের মে মাসে ধলঘাটের এক গ্রামে। সন্ধ্যার সময় ক্যাপ্টেন ক্যামেরনের নেতৃত্বে সৈন্যদল বাড়ি ঘেরাও করে ফেলে। প্রস্তুত ছিল না একটুও, মেশিনগান চলল অপর পক্ষ থেকে, আমাদের পক্ষ থেকেও গুলি চলল। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে হতভম্ব ভাব কেটে গেলে প্রীতিও গুলি চালাতে লাগল। ক্যাপ্টেন ক্যামেরন নিহত, নির্মলদা গুরুতরভাবে আহত, বাঁচবে না। ক্যাপ্টেন ক্যামেরনের মৃত্যুতে সৈন্যরা যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ়, মাস্টারদার নির্দেশ এলো পালাবার চেষ্টা করতে হবে।
যে প্রীতি এতক্ষণ অন্যদের মতো প্রাণপণে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল, সে প্রীতি আহত নির্মলদার জন্য বিচলিত হয়ে পড়ল। আহত সাথী একজনকে কিছুতেই ছেড়ে যেতে সে পারবে না। অসম্ভব ভালোবাসত প্রীতি দলের প্রত্যেককে, নিজের প্রাণ ওর কাছে ছিল তুচ্ছ ব্যাপার। শেষকালে মাস্টারদা ওকে টেনে বের করে নিয়ে আসেন। ঘটনাটা শুনে মনে হয়েছিল মাস্টারদার উক্তির সত্যতা। মনে হয়েছিল হাতে আছে ওর আয়ুধ, আর বুকে আছে ওর অমৃত।
প্রীতি বিপদের সম্মুখীন হয়ে এতটুকুও ভয় পেত না। কিন্তু নিজের জন্য আর কাউকে অসুবিধায় ফেলতে সে সংকোচ বোধ করত।
এই ধলঘাটের ঘটনার পর সে পালিয়ে আসতে পারলেও সেই বাড়িতে তার কাপড়-চোপড় পাওয়া যায়। কিন্তু শহরে নিজের বাসায় ফিরে এলেও পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেনি, সন্দেহ করতে পারেনি।
মাস্টারদা খবর পাঠালেন শহরে ওকে লুকিয়ে রাখতে হবে। বাসা থেকে ওর চলে আসার পর পুলিশের দৃষ্টি আমার ওপর বেড়ে গেল। আমাদের বাড়িতে শাসনও আরো একটু কড়া হয়ে উঠল। তাই ও মনস্থ করল নিজের বাসায় চলে যাবে এবং বলল, ‘কল্পনা, আমি চাই না আমার জন্য তুমিও গ্রেপ্তার হও, আমি অন্য ব্যবস্থা করব, এখন বাসায় চলে যাই।’ মাস্টারদা ওর জন্য পরে অন্য ব্যবস্থা করে তাকে নিয়ে যান।
...কলকাতায় দিনের পর দিন মিথ্যা নামে ফাঁসির আসামি রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে প্রীতি দেখা করে এসেছে। কেউ তাকে চিনতেও পারেনি, ধরতেও পারেনি, বুঝতেও পারেনি। রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ছিলেন চাটগাঁয়ের ছেলে, অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পলাতক আসামি, চাঁদপুরে তারিণী মুখার্জির হত্যার মামলায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। কলকাতা সেন্ট্রাল জেলে তিনি থাকতেন। প্রীতি ‘আরতি’ নাম নিয়ে বোন পরিচয়ে ৪০ বার ইন্টারভিউ দিয়েছে। তার সঙ্গে, পুলিশের বিন্দুমাত্র সন্দেহের উদ্রেক হয়নি। শুধু পুলিশ নয়, কলেজের বোর্ডিংয়ের সুপারিন্টেডেন্টও সন্দেহ করেনি কোনোদিন। ধলঘাটে রামকদা সম্বন্ধে ওর লেখা একটি প্রবন্ধ পাওয়ার পরে পুলিশ জানতে পারে। ‘রামকৃষ্ণদার ফাঁসি হওয়ার পর প্রীতি প্রত্যক্ষ কাজে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তারপরে হয় ওর মাস্টারদার সঙ্গে দেখা। ধলঘাটে চোখের সামনে নির্মলদার মৃত্যু ওকে আরো বিচলিত করে তোলে। মাস্টারদা বলেছিলেন, হয়তো আত্মহত্যা করবার সপক্ষে এত যুক্তি সে সেজন্যই দিয়েছিল। অত্যন্ত প্রিয় দুজনের মৃত্যু ওকে আঘাত করেছিল খুব বেশি। মাস্টারদা বলতেন, ‘আত্মহত্যা আমি একেবারেই সমর্থন করি না, কিন্তু যাওয়ার আগের মুহূর্তে তার যুক্তি দিয়ে সে আমার সমর্থন আদায় করে পটাশিয়াম সায়ানাইড চেয়ে নিয়ে গেল। প্রীতির আগ্রহের কাছে আমার যুক্তি টিকল না।’
ছোট্ট একটি কথা, কিন্তু তাতেই প্রীতির স্নেহপ্রবণ ও দয়ালু মনের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯৩০-এর পূজার বন্ধে ওদের বাড়িতে গিয়েছি। কথা হচ্ছিল পাঁঠা কাটা নিয়ে। প্রীতি উত্তর দিয়েছিল, ‘ভয়ের প্রশ্ন না, কিন্তু আমি পারব না নিরীহ একটি জীবকে হত্যা করতে।’ একজন তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করল, ‘কী, দেশের স্বাধীনতার জন্যও তুমি অহিংস উপায়ে সংগ্রাম করতে চাও?’ আমার মনে পড়ে প্রীতির স্পষ্ট জবাব, ‘স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিতেও পারব, প্রাণ নিতেও মোটেই মায়া হবে না। কিন্তু নিরীহ জীব হত্যা করতে সত্যিই মায়া হয়, পারব না।’
দুবছরের মধ্যেই এর প্রমাণ অক্ষরে অক্ষরে সে দিয়ে গিয়েছে। পাহাড়তলী আক্রমণের নেতৃত্ব প্রীতিই নিয়েছিল, পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করে প্রমাণও করে দিয়েছিল দেশের জন্য আত্মদান সে কত সহজেই করতে পারে!
‘অস্ত্রাগার লুণ্ঠন থেকে শুরু করে চাটগাঁয়ে সব আন্দোলনের সমস্ত খরচই দলের ছেলেমেয়েদের কাছ থেকেই নেয়া হতো। প্রত্যেক কর্মীই সাধ্যমতো টাকা বাড়ি থেকে এনে দলের কাজে দিয়েছে। প্রীতির বাড়ির অবস্থা বরাবরই খারাপ ছিল। বাবা মিউনিসিপ্যালিটির কেরানি ছিলেন, সামান্য মাইনে যা পেতেন তাতে সংসার চালানোই কষ্টকর ছিল। প্রীতির ওপরই সংসারের সব ভার ছিল। বাবা মাইনে পেয়েই ওর কাছে দিতেন। একদিন দুপুরে ওদের বাড়িতে বসেই টাকার সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছিল। ৫০০ টাকা সেদিনই মাস্টারদার কাছে পাঠাতে হবে। ৪৫০ টাকা জোগাড় হয়েছে, আরো ৫০ টাকা চাই। ওকে টাকার কথা বলা হয়নি ওদের বাড়ির আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ বলে।’
আলোচনাকালে কাউকে কিছু না বলে সে উঠে গেল, পর মুহূর্তেই ৫০ টাকা এনে হাতে দিল। টাকা কোথায় পেল জিজ্ঞেস করাতে অম্লান বদনে সে বলল, ‘কাল বাবা মাইনে পেয়েছেন, টাকা তো আমার কাছেই থাকে, সমস্ত টাকাটাই দিলাম।’ প্রতিবাদ করা হলো দুটো কারণে। প্রথমত, সংসারে খরচ চালানোর আর কিছু রইল না আর বাসায় বাবা যখন ফিরবেন, তখন এই নিয়ে হৈচৈ হবে, ওর ওপর বাড়ির সবাই বিশ্বাস হারাবে। প্রীতি উত্তর দিল, ‘সংসার চালানোর ভার আমার ওপর। আমি বুঝব, তা নিয়ে আপনাদের মাথা ঘামাতে হবে না। আর বাড়িতে এই নিয়ে গোলমাল হওয়ার কোনো আশঙ্কাই নেই। আমার ওপর বাবার বিশ্বাস কোনোদিনই ভাঙবে না, তা ছাড়া আমি তো নিজেই বলব বাবাকে যে আমিই টাকাটা খরচ করেছি। আপনাদের ভয় নেই বাবা জিজ্ঞাসাও করবেন না কিসে খরচ হলো। আমি টাকা খরচ করেছি শুনলেই বুঝবেন কোনো ভালো কাজেই খরচ হয়েছে এবং সে কাজ সংসার চালানোর চেয়েও মহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ।’ তবু টাকা গ্রহণ করায় আপত্তি দেখে ও প্রায় কেঁদে ফেলে বলল, ‘গরিব দেখে আমাদের টাকা নিতে চান না। আমি যে নিষ্ঠাবান কর্মী হতে পারব তা প্রমাণ করার সুযোগও কি আমায় দেবেন না?’ এই কথার পর টাকা নিতে হয়েছিল বাধ্য হয়ে।
‘প্রীতি শুধু স্কুল-কলেজে ভালো মেয়েই ছিল না, সে লিখতে পারত খুব ভালো, ভালো সাহিত্যিক ছিল সে। ইন্টারমিডিয়েটে ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে মেয়েদের মধ্যে সে প্রথম হয়। পলাতক জীবনে সে যা লিখত, সবাই তা আওড়াতো কথায় কথায়।
ছোটবেলা থেকে তার অদ্ভুত মেধাশক্তি দেখে ওর বাবা অবস্থাপন্ন না হলেও ওকে পড়িয়েছেন। প্রীতিও বলত, ওর বাবা বলেন, ‘তোকে ঘিরেই রয়েছে আমার ভবিষ্যৎ আশা-ভরসা।’ বাবার কথা বলতে গিয়ে প্রীতির চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠত। ওর বাবাকে ও খুবই ভালোবাসত।। প্রীতির বিএ পরীক্ষা দেয়ার কিছু আগে ওর বাবার চাকরি যায় বলে প্রীতির আয়ের ওপরই নির্ভর করে চলতে হতো সকলের। মা-বাবা, আর চারটি ভাই বোন। সে নন্দনকানন হাই স্কুলে মাস্টারি করত, আর করত একটা টিউশনি।। ‘কিন্তু দেশের কাজের জন্য ও সব তুচ্ছ করে চলে গিয়েছিল। একান্ত আপন যারা ছিল তাদের দুঃখ-কষ্ট, তাদের চোখের জলও তাকে পিছু টানতে পারেনি। দেশের হাজার হাজার মা-বাবার চোখের জল দূর করার আদর্শকে সে গ্রহণ করেছে।। প্রীতির বাবা শোকে-দুঃখে পাগলের মতো হয়ে গেলেন, কিন্তু প্রীতির মা গর্ব করে বলতেন, আমার মেয়ে দেশের কাজে প্রাণ দিয়েছে। তাদের দুঃখের পরিসীমা ছিল না, তবু তিনি সে দুঃখকে দুঃখ মনে করেননি। ধাত্রীর কাজ নিয়ে তিনি সংসার চালিয়ে নিয়েছেন, আজো তাদের সেভাবে চলছে। প্রীতির বাবা প্রীতির দুঃখ ভুলতে পারেননি। আমাকে দেখলেই তাঁর প্রীতির কথা মনে পড়ে যায়, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন। দুর্ভিক্ষের সময় মেয়েদের কাজ দেখতেন আর ভাবতেন, প্রীতি থাকলে এর চেয়ে বেশি কাজ হতো।
দেশের লোকও প্রীতিকে ভোলেনি, প্রীতির আত্মদানকে ভোলেনি। তাই জগদ্বন্ধু বাবু যখন রাস্তা দিয়ে যান, অপরিচিতের কাছে তাকে সবাই পরিচয় করিয়ে দেয়, ‘প্রথমে যে মেয়ে দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছিল, উনি তারই বাবা।’ (চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণকারীদের স্মৃতিকথা)।
প্রতিভা সেন
বেথুন কলেজে প্রীতিলতার সহপাঠী ছিলেন প্রতিভা সেন। ওই কলেজের শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ ১৮৭৯-১৯৭৯ বইতে প্রীতিলতা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, ঢাকা থেকে আইএ পাস করে আমরা তিনজন মেয়ে কলকাতায় পড়তে এসেছিলাম আমি, প্রীতি ওয়াদ্দেদার, বকুল দত্ত। প্রীতি ওয়াদ্দেদার ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষায় পঞ্চম স্থান ও আমি সপ্তম স্থান অধিকার করে ২০ টাকা স্কলারশিপ নিয়ে দুজনেই ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে বেথুন কলেজে ভর্তি হই। পরে রাজনীতিতে বেশি ব্যস্ত থাকায় প্রীতি অনার্স ছেড়ে দিয়েছিল।
বিএ পাস করে চট্টগ্রামে ফিরে গিয়ে একটা স্কুলে কিছুদিন শিক্ষকতা করে ও পরে চট্টগ্রামের ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ করতে গিয়ে ধরা পড়ার আগে পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করে এসব কথা সবারই জানা।
‘ঢাকায় দুবছর ও কলকাতায় দুবছর প্রীতির সঙ্গে পড়েছিলাম। ও চট্টলার মেয়ে বলে খুব গর্ব করত। পড়াশুনায় খুব ভালো ছিল। আন্তরিক আগ্রহ নিয়ে পড়াশুনা করত। ঢাকায় ওকে সিরিয়াস, ভালো ছাত্রী বলেই জানতাম। কলকাতায় যখন এলো তখন ও যে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে জড়িত তা ঠিক বুঝতে পারিনি। দেখা যেত খদ্দর ছাড়া ও অন্য কিছু পরত না। তবে শৌখিন ছিল সব সময় শাড়ির রং কিংবা পাড়ের সঙ্গে ম্যাচ করে ব্লাউজ পরত। খুব চটপটে, ফিটফাট, কর্মব্যস্ত মনে হতো। প্রীতির চেহারা ও কথাবার্তা আমার প্রায়ই মনে পড়ে। রং কালো, মাঝারি গড়ন, জোড়াভুরু। হাসিটা সুন্দর ছিল হাসলে মুখটা জ্বলজ্বল করত।’ (বেথুন কলেজ শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ ১৮৭৯-১৯৭৯)।
সতী ঘোষ
আলাপ হলো প্রীতির সঙ্গে। প্রীতি ওয়াদ্দোদার-গায়ের রংটি কালো আর ভুরুজোড়া ছিল ঘন। খুব শান্ত মেজাজ, কথা কম বলত, কিন্তু রসিকতা ছিল যথেষ্ট। আমাকে ভালোবাসত; তার কারণ খুব জোর গলায় তাকে স্বদেশি গান গেয়ে শোনাতে হতো। আমার সঙ্গে দেখা হলেই বলত, ‘চল চল একটা গান শোনাবি, আমার হস্টেলেই চল।’
আমরা জানতাম প্রীতিদি চাটগাঁর খাস্তগীর কলেজ থেকে স্কলারশিপ পেয়ে এসেছে; বিএতে নিশ্চয়ই ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট হবে। বেথুন সাহেবের মূর্তি বসানো বড় লাইব্রেরি হলটার চারপাশে ঘুরে ঘুরে বই দেখত। অধ্যাপকরা জিজ্ঞেস করতেন, ‘প্রীতি পড়াশোনা করছ তো?’ প্রীতিদি খুব নিস্পৃহ গলায় জবাব দিত, ‘ভালো লাগে না স্যার।’
‘কেন যে প্রীতিদির পড়াশোনা ভালো লাগত না, তার কারণ পরে বুঝেছিলাম।’ (বেথুন কলেজ শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ ১৮৭৯-১৯৭৯)।
প্রবন্ধটি প্রথমা প্রকাশন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার বই থেকে সংগৃহীত