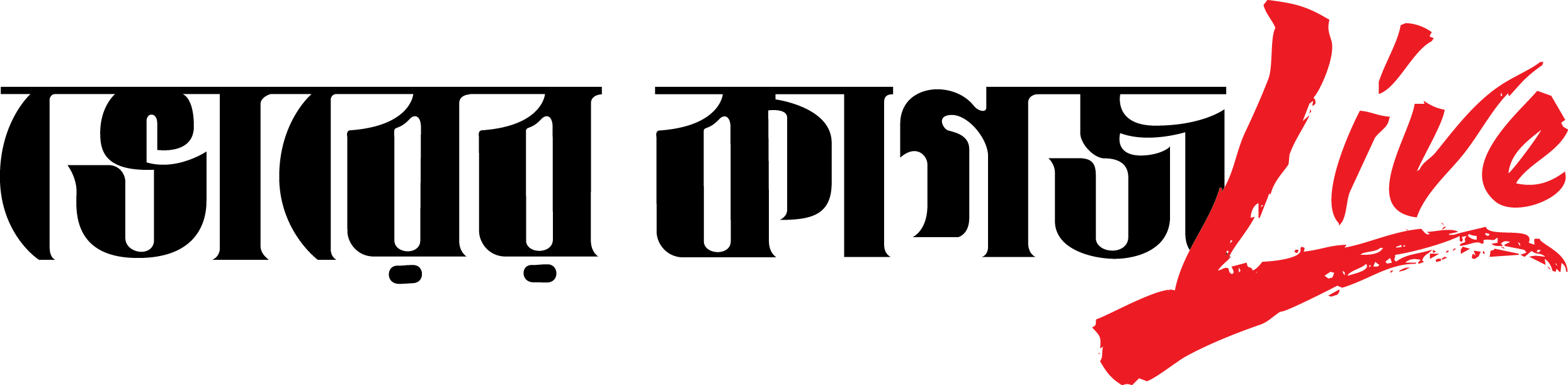মুক্তিযুদ্ধে এপ্রিলের দুই ঐতিহাসিক দিবসের তাৎপর্য
কাগজ প্রতিবেদক
প্রকাশ: ১৫ এপ্রিল ২০১৯, ০৮:৫৬ পিএম
মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনায় ১০ এবং ১৭ এপ্রিলের গৃহীত সিদ্ধান্ত ঘোষণাপত্র সরকারের শপথ অনুষ্ঠান বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল এবং অংশ। এটি ছাড়া মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস একেবারেই কল্পনার বিষয় হতে পারবে না। সুতরাং আমরা যখন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পঠন-পাঠনের কথা বলব তখন এপ্রিলে দুই দিবসের মহত্তম তাৎপর্যকে একীভূত করে এর যথার্থ অর্থ বুঝতে হবে। তা হলেই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সঠিকভাবে বুঝা ও ধারণ করা সম্ভব হবে।
মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার তাৎপর্যে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে হয়। এর কিছু কিছু ঘটনা মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রাক্কালের, আবার গোটা ৯ মাসের শুরু থেকে বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন ঘটনার বিশেষত্ব রয়েছে। যেমন- ২৫ মার্চের আগে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর রেসকোর্সের ঐতিহাসিক ভাষণ। এটি একটি মাইলফলক ঘটনা। তবে এর আগেও অনেকগুলো ঘটনা ৭ মার্চ এসে যুক্ত হয়। আবার ৭ মার্চ থেকে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনা অনুযায়ী মানুষের অংশগ্রহণ সক্রিয় হয়ে ওঠে, মুক্তিযুদ্ধের জন্য মানসিক প্রস্তুতি ও অস্ত্রশস্ত্রের প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর্ব চলতে থাকে, বঙ্গবন্ধু এবং ইয়াহিয়া-ভুট্টোসহ রাজনৈতিক নেতাদের বৈঠকের পর্ব এবং সর্বশেষ ২৫ মার্চ পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বর আক্রমণ ও গণহত্যার শুরু থেকে ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার পর্বটি মুক্তিযুদ্ধ পূর্ববর্তী ছোট ছোট পর্বের অথচ খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য বহনকারী ইতিহাসের অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়। একইভাবে ২৬ মার্চ পরবর্তী সময়ে যে প্রতিরোধ জনগণের পক্ষ থেকে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে শুরু হয় সেটি এপ্রিল মাসের ১০ তারিখ সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে একটি নতুন পর্বে উন্নীত হয়। আবার এই সরকারের শপথ নেয়ার মাধ্যমে ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী সরকারের গ্রহণযোগ্যতা, বিশ্বাসযোগ্যতা এবং নেতৃত্বদানের অঙ্গীকারের বিষয়টি একটি নতুন তাৎপর্য সৃষ্টি করেছিল- যা ২৬ মার্চ পরবর্তী সময়ে অসংগঠিত প্রতিরোধ ও যুদ্ধকে একটি বৈধ সরকারের নেতৃত্বে সুসংগঠিতভাবে পরিচালিত হওয়ার যাত্রা শুরু করে। সে কারণে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধকে পরিপূর্ণতা দানের ক্ষেত্রে এপ্রিল মাসের ১০ ও ১৭ এপ্রিলের দুটি ঐতিহাসিক ঘটনা বিশেষ তাৎপর্যের অধিকারী ছিল। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনায় এই দুটি ঘটনাকে যথাযথ মর্যাদা ও গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরতে হবে। তা হলেই ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পরিপূর্ণতা লাভের বিষয়গুলো নতুন প্রজন্মের কাছে স্পষ্ট হবে।
আমরা জানি ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার একটি তারবার্তা প্রেরণের মাধ্যমে দেশবাসীকে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা লাভের আগ পর্যন্ত যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান। এটি তাঁর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে যুদ্ধ শুরুর দিকনির্দেশনার ধারাবাহিকতা হিসেবে বিবেচিত হয়। তবে পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুকে ওই রাতে বাসভবন থেকে গ্রেপ্তার করে পাকিস্তানে নিয়ে যায়। তাদের ধারণা ছিল বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করার পর পূর্ব বাংলায় যেটুকু বিদ্রোহ বা প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে তা তারা সেটি নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হবে। বিশেষত অপারেশন সার্চলাইট পরিচালিত হওয়ার পর যে গণহত্যার ভীতি পাকিস্তান সরকার ঢাকাসহ দেশব্যাপী সৃষ্টি করেছিল তার ফলে পূর্ব বাংলার জনগণের প্রতিরোধ ক্ষমতা সহজেই স্তিমিত হয়ে যাবে- এমনটাই তাদের ধারণা ছিল। কিন্তু তাদের এই হিসাবটি সঠিক হয়নি। পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যে নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর অনুসারীদের প্রতি যে আস্থা তৈরি হয়েছিল তার ভিত্তি ছিল অনেক গভীরে প্রথিত। সে কারণে বঙ্গবন্ধুর একটি নির্দেশের পর তাঁর উপস্থিতি বা সরাসরি নেতৃত্ব দেয়া না দেয়ার বিষয়টি মানুষের কাছে আলাদা করে দেখার কোনো সুযোগ ছিল না। তিনি ছিলেন সেই সময়ের মানুষের কাছে এক কিংবদন্তির মহানায়ক। সুতরাং তাঁর ঘোষিত স্বাধীনতা তখন প্রতিটি নেতা, কর্মী এবং জনগণকে একই সুতায় গেঁথে ফেলেছিল। সে কারণে ২৬ মার্চ থেকে দেশব্যাপী একদিকে প্রতিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল, অন্যদিকে একটি দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধের জন্য মানুষ প্রতিবেশী ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। এই আশ্রয়টি শরণার্থী শিবিরে দিন কাটানোর জন্য নয়। বরং সশস্ত্র পন্থায় যুদ্ধ করার প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশের অভ্যন্তরে মানুষকে সঙ্গে নিয়ে পাকিস্তানি বাহিনীকে পরাজিত করার মাধ্যমে মুক্ত স্বদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য। ভারতমুখী হওয়ার জন্য মানুষকে তখন কোনো বেতার টিভিতে ঘোষণার জন্য অপেক্ষা করতে হয়নি। আওয়ামী লীগের নেতারা সেই রাতেই ঢাকা ছেড়ে পূর্ব, উত্তর ও পশ্চিমে যে যার মতো করে সীমান্ত অতিক্রম করছিলেন। সাধারণ মানুষ নেতাদের অনুসরণ করতে থাকে। এটি যেন সবার কাছে মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। একদিকে নেতারা বসে না থেকে সীমান্ত অতিক্রম করলেন, অন্যদিকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে বাঙালি সেনা, পুলিশ, বিডিআর, ছাত্র-জনতা, পেশাজীবী, আমলাসহ সব স্তরের মানুষ সীমান্তের ওপারে চলে গেলেন। বিষয়টি পাকিন্তানি সেনাবাহিনীরা মোটেও বুঝতে পেরেছিল বলে মনে হয় না। তারা সীমান্তে মানুষের ঢল নামার প্রবাহকে বন্ধ করতে পারেনি। সীমান্তের ওপারে গিয়েই রাজনৈতিক নেতারা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে একটি সরকার গঠনের প্রস্তুতি নিতে থাকেন। বিশেষত ১৯৭০-এর নির্বাচনে যারা জাতীয় প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত হয়েছিলেন তাদের নিয়ে সরকার গঠনটি ছিল একটি বৈধ উপায়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সংগঠিত রূপ দেয়া। কেননা তখন পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার অভ্যন্তরে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একটি সশস্ত্র যুদ্ধ ও কূটনৈতিক লড়াই পরিচালনা করার জন্য একটি বৈধ সরকারে প্রয়োজনীয়তা ছিল- যারা লড়াইরত পূর্ব বাংলার মানুষের সমর্থন একচেটিয়াভাবে পাওয়ার অবস্থানে ছিলেন।
জনগণের মধ্যে তখন বঙ্গবন্ধুর নামে সরকারের যে কোনো কর্মকান্ডের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন ছিল। এই সরকারটি গঠন করা না গেলে ২৫ মার্চ-পরবর্তী সময়ের রাজনৈতিক উত্তেজনা কোনো দিকনির্দেশনা পেত না। তেমনটি ঘটলে স্বাধীনতার আকাক্সক্ষা বাস্তবায়নের সুযোগ ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে যেত। বিষয়টি বঙ্গবন্ধু আগে থেকে উপলব্ধি করতে পেরেই ২৫ মার্চ রাতে তাজউদ্দীনসহ অন্য নেতাদের তার অনুপস্থিতিতে একটি সংগঠিত রূপ দেয়ার একটি নির্দেশ দিয়েছিলন। নেতারা ভারতে প্রবেশ করার পরই নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা এবং একটি সরকার গঠনের আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নিতে থাকেন। তারা বিদ্যমান রাজনৈতিক বাস্তবতায় বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি, তাঁর অনুপস্থিতিতে সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব প্রদান করে একটি সরকার গঠন করার সিদ্ধান্ত নেন। এটি ১০ এপ্রিল চূড়ান্ত হয় এবং পাকিস্তান রাষ্ট্র ব্যবস্থা থেকে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ঘোষিত স্বাধীনতা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত এই সরকার পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে সৃষ্ট পূর্ব বাংলার জনগণের প্রতিরোধকে সশস্ত্র যুদ্ধে নেতৃত্ব দেয়া এবং একইভাবে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এই যুদ্ধের পক্ষে জনমত সৃষ্টি, নৈতিক ও সশস্ত্র যুদ্ধের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রশস্ত্রের জোগানদান, কূটনৈতিক সমর্থন আদায় করাসহ যাবতীয় দায়িত্ব পালনের জন্য সব ধরনের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও আর্থিক দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিলেন। ১০ এপ্রিল এবং তার অব্যবহিত পরপরই পূর্ব বাংলার যুদ্ধরত মুক্তিকামী সব মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। এক অভূতপূর্ব সাড়া তখন পাকিস্তানি দখলকৃত পূর্ব বাংলায় প্রবাহিত হয়, যার কম্পনে পাকিস্তান সরকার সেই দিন অনেকটাই পরাজয়ের প্রস্তুতি গ্রহণ করার অপেক্ষায় দিন গুনতে থাকে। বাংলাদেশব্যাপী এই সরকারের প্রতি সমর্থন দৃঢ়তর হতে থাকে, মানুষ দলে দলে যুদ্ধের জন্য সীমান্ত পাড়ি দিতে থাকে। গ্রামগঞ্জে সংগ্রাম কমিটি গঠিত হতে থাকে। এসব কমিটি তরুণদের প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য নির্দেশ অনুযায়ী বিভিন্ন জায়গায় প্রেরণ করতে থাকে এবং জনগণের কাছ থেকে খাদ্য ও অর্থ সংগ্রহ করে মুক্তিযোদ্ধাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে থাকে। সাধারণ মানুষ নির্ভয়ে এসব যুদ্ধকে আশ্রয় দিতে থাকে এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতির সঙ্গে সরকারের মেলবন্ধন তৈরি হতে থাকে। সুতরাং ১০ এপ্রিল গঠিত সরকার মুক্তিযুদ্ধের ২৫ মার্চ-উত্তর স্বতঃস্ফূর্ত অসংগঠিত রূপকে একটি যৌক্তিক পরিণতিতে নিয়ে যাওয়ার বৈধ সরকারের অংশে পরিণত করে। এখান থেকে মুক্তিযুদ্ধ সুসংগঠিতভাবে পরিচালিত হওয়ার সব নির্দেশনা লাভ করে। একটি মুক্তিযুদ্ধকে সফল করার ক্ষেত্রে ১০ এপ্রিলের যুগান্তকারী ঘটনা কতটা তাৎপর্য বহন করেছিল সেটি এর অন্তর্নিহিত আয়োজন ও পরবর্তী কার্যক্রমের মাধ্যমেই নির্ধারিত হয়েছিল।
দ্বিতীয় যে দিবসটি এই এপ্রিল মাসেই নবগঠিত সরকারের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ছিল তা হলো ১৭ এপ্রিল তৎকালীন কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার বৈধ্যনাথ তলায় মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী সরকারের শপথ গ্রহণের আনুষ্ঠানিকতা। ১০ তারিখ সরকার গঠিত হওয়ার পর সরকারের শপথ নেয়ার বিষয়টি কোথায় কীভাবে হবে তা কারো কাছেই জানা ছিল না। সেই সময়ের বাস্তবতায় নতুন সরকারের পক্ষে সব কিছু আগে নয় পরে দৃশ্যমান করা যথাযথ ছিল। সরকার সেই কাজটি করেছিল। মুক্তাঞ্চলে সরকার শপথ নেয়ার বিষয়টি ১৭ তারিখ সংগঠিত করেছিল। সেখানে সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রিপরিষদ শপথগ্রহণ করেছিলেন। সেখানে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী সংক্ষিপ্ত ভাষণের মাধ্যমে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। সেখানেই পঠিত হয়েছিল স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি। যা স্পিকার হিসেবে অধ্যাপক ইউসুফ আলী পাঠ করেছিলেন। এর মাধ্যমে নতুন সরকারের শপথ ও ঘোষণার ভিডিও সারা বিশ্বের মানুষ দেখতে পায়। একই সঙ্গে সেখানে উচ্চারিত মুহুর্মুহু স্লোগানের ধ্বনি আকাশ-বাতাস যেন প্রকম্পিত করেছিল। উচ্চারিত হয়েছিল ‘তোমার নেতা আমার নেতা- শেখ মুজিব, শেখ মুজিব’ স্লোগানটি, যা ধরেছিলেন শত শত মুক্তিযোদ্ধা। যাদের হাতে লড়াইয়ের অস্ত্র ছিল, মাথায় গামছা বাঁধা ছিল। সেই উচ্চারণের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল সাড়ে সাত কোটি মানুষের যুদ্ধরত আকাক্সক্ষার মনোবৃত্তি। ১৭ এপ্রিল বৈদ্যনাথ তলায় নতুন সরকারের শপথ অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিকতা স্বল্প সময়ের জন্য হলেও এর তাৎপর্য অসীম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এখান থেকে মানুষ নতুনভাবে শপথ নেয়ার সুযোগ খুঁজে পেল। সরকার শপথের জায়গাটির নাম মুক্তিযুদ্ধের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে তথা মুজিবনগর নামে পরিচিত করেছিল। সেই দিন থেকেই মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী সরকারের নাম গণমাধ্যমে মুজিবনগর সরকার নামে হতে থাকে। ১০ এপ্রিল এই মুজিবনগর সরকার গঠন, স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র রচনা, ১৭ এপ্রিল ওই ঘোষণাপত্র পাঠ, শপথগ্রহণ ইত্যাদি হয়ে উঠেছিল মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এই দলিলটি ১৯৭২ সালে রচিত বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানের চতুর্থ (১৯৭৫) এবং পঞ্চম (১৯৭৯) সংশোধনীতে অন্তর্ভুক্ত হয়। যা আমাদের সংবিধানে অলঙ্ঘনীয় অংশ হিসেবে পরিচিত হয়। সুতরাং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনায় ১০ এবং ১৭ এপ্রিলের গৃহীত সিদ্ধান্ত ঘোষণাপত্র সরকারের শপথ অনুষ্ঠান বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল এবং অংশ। এটি ছাড়া মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস একেবারেই কল্পনার বিষয় হতে পারবে না। সুতরাং আমরা যখন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পঠন-পাঠনের কথা বলব তখন এপ্রিলে দুই দিবসের মহত্তম তাৎপর্যকে একীভূত করে এর যথার্থ অর্থ বুঝতে হবে। তা হলেই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সঠিকভাবে বুঝা ও ধারণ করা সম্ভব হবে।
মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী : অধ্যাপক (অবসরপ্রাপ্ত), ইতিহাসবিদ ও কলাম লেখক।