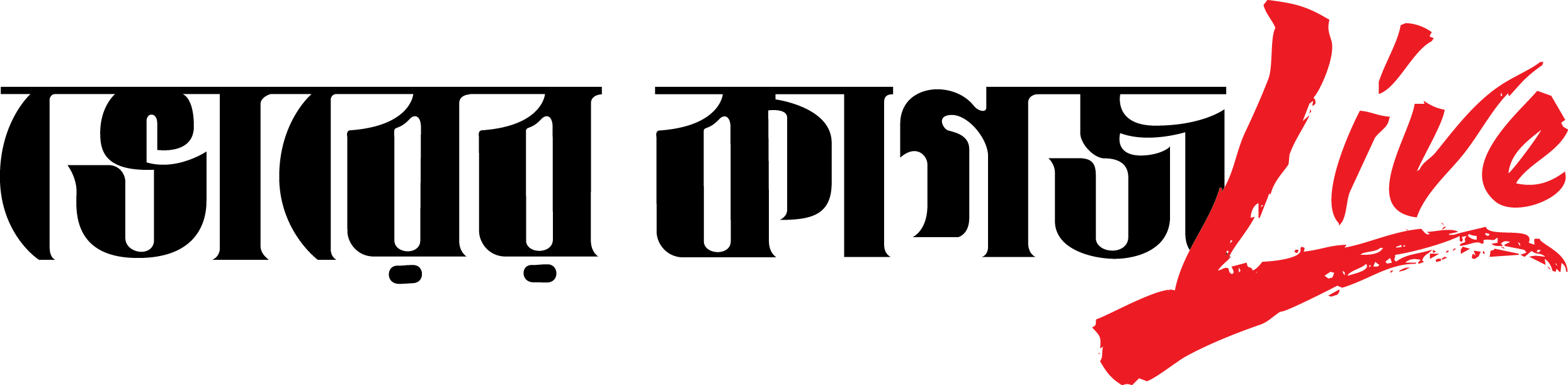উচ্চশিক্ষার সংকটের আয়তন এবং চেহারা
কাগজ প্রতিবেদক
প্রকাশ: ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯, ০৭:১৮ পিএম

বস্তুত বাংলাদেশের শিক্ষার্থী প্রজন্মের জনসংখ্যা চিন্তা করলে বাংলাদেশে আসলে ৫০০টি বিশ্ববিদ্যালয় থাকা দরকার। আজকেই (৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯) পত্রিকায় দেখলাম বান্দরবানের দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তরের উদ্বোধনের ছবি। বাংলাদেশের মতো জনবহুল কিন্তু সংকুচিত ভূমির দেশে উচ্চশিক্ষার আনুভূমিক বা সমতল সম্প্রসারণ ঠেকানো যাবে না। সেজন্য বেসরকারি খাতে উচ্চ শিক্ষাব্যবস্থাকে যেতেই হবে। এবং ফলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়বেই। কাজেই একটা খাত বৃদ্ধি পাওয়া যদি অবশ্যম্ভাবি হয়ে পড়ে, সে খাতটি যাতে ভালোভাবে উপযুক্ততা লাভ করে তার দিকেও লক্ষ রাখতে হবে। এখানে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের উচ্চতর ডিগ্রি লাভের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি কল্পে এবং সাধারণভাবে উচ্চতর ডিগ্রি গ্রহণের ইচ্ছা পোষণকারী শিক্ষার্থীর তৃষ্ণা মেটাতে একটি কথা প্রস্তাবনার আকারে দিতে চাই। সেটি হলো যোগ্যতার নিরিখে ক্রমান্বয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েও মাস্টার্স-পরবর্তী এমফিল এবং পিএইচডি ডিগ্রি প্রদানের সক্ষমতার অনুমতি দেওয়া। বাস্তবতার নিরিখে বলছি, বর্ষীয়ান অনেক শিক্ষক স্বায়ত্তশাসিত ও সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর নিয়ে বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন পদে নিয়োজিত আছেন পূর্ণকালীন সময়ে। তাদের দ্বারা এমফিল, পিইচডি প্রোগ্রাম চালু করা যায়। বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ মানের পাঠাগার এবং অনলাইন সুযোগ পাকাপোক্তভাবে আছে।
প্রাতঃভ্রমণের সময় নিত্য দেখি এলাকার মসজিদের সামনে ভ্যানগাড়িতে করে সবজিওয়ালারা সবজি বিক্রি করছে। একদিন দেখলাম একটিতে চালকের আসনে বসে আছে ৮/১০ বছরের এক বালক। পেছনে তার গাড়ি সবজিতে ভরা। কিন্তু বালকটি গাল হাঁ করে ঘুমোচ্ছে। বুঝলাম তার বাবা হয়তো আশপাশে কোথাও আছে, ছেলেকে রেখে গেছে চৌকিদারিতে।
আবার ভাবলাম, তা তো নাও হতে পারে, হয়তো সেই বিক্রেতা। মানুষের মনের চিন্তা এগোয় একটি দেখার অনুবর্তী দেখাগুলোর ক্রমানুসারে। তখন মনে পড়ল, এর একটু আগে একটি কিশোর বয়সী স্কুল ছাত্রকে দেখেছিলাম স্কুলে যাচ্ছে ধীর পায়ে হেঁটে হেঁটে- শেক্সপিয়ারের ভাষায়, শম্বুকগতিতে, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে।
এর সঙ্গে যোগ হলো আরো কতিপয় স্কুল শিশুর মা বা বাবার সঙ্গে হেঁটে এলাকাস্থ স্কুলে যাওয়ার ছবি। কোনো কোনো শিশুর নিজের পিঠের ওপর ব্যাগের ভারী বস্তা, আবার কোনো কোনো শিশুর ব্যাগ তার বাবা বা মা বহন করছে। একই সূত্রে আমার নাতি-নাতনিকে তাদের মায়ের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর সময় দেখাশোনা করার জন্য নিযুক্ত কাজের কিশোরী ‘বুয়া’র (আমার নাতি-নাতনিরা ডাকে ‘আপু’) কথা মনে পড়ল।
ওপরের ছবিগুলো থেকে বোঝা যাচ্ছে দেশে অনেক শিশুই দারিদ্র্যের জন্য স্কুলে যেতে পারছে না। অনেক শিশু স্কুলের লেখাপড়াকে পছন্দ করছে না এবং অনেক শিশুর মনস্তত্ত্বে স্কুলে গমনের সময় ব্যাগের ভারী এবং বড় হওয়াটাই শিক্ষার আসল উপকরণ হিসেবে ঢুকে গেছে। শিশুর মন সবসময় বড় কলাটা, বড় পিঠাটা চায়, সেই একই কারণে ব্যাগ বড় হওয়াটাই তাদের পছন্দ। তাদের মেরুদণ্ডে ক্ষতির কথা তো তারা আর জানবে না।
তবে আমার আজকের লেখাটা শিশু-কিশোর শিক্ষা নিয়ে নয়, আমি লিখতে চাই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কিছু অধ্যয়নিক বিষয় নিয়ে। বস্তুত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার্থী ভর্তি সংক্রান্ত সংকট নিয়ে। এ ছবিটা আরো বিভ্রান্তিজনক। আমি যেহেতু পেশাগতভাবে ইংরেজির শিক্ষক, কাজেই শিক্ষার্থীর ইংরেজির মানকে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার ওপর প্রতিফলন হিসেবে দেখাই আমার জন্য প্রামাণিকভাবে যৌক্তিক হবে, যদিও এটি অবশ্যই খণ্ডিত অভিমত হবে। তবে এ কথাটাও স্বীকার করতে হবে সাধারণত প্রথাগতভাবে আমাদের সমাজে ইংরেজি জানা বা না-জানা নিয়ে সাধারণ শিক্ষার মান যাচাই করার রেওয়াজ আছে। যদিও এটি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি নয়।
উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে আসা শিক্ষার্থীদের আমরা ভর্তি করাই। ভর্তি পরীক্ষার সময় লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের বেশিরভাগের অক্ষমতা দেখে আমরা ফাঁপড়ে পড়ি। শিক্ষার্থীর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে ইংরজির নম্বর মার্কশিটে দেখাচ্ছে ‘এ প্লাস’, কিন্তু সে ‘গরু ঘাস খায়’ বাক্যটার ইংরেজি লিখতে পারছে না।
যদি একজন দু’জনের ক্ষেত্রে এটা হতো কথা ছিল না, কিন্তু অধিকাংশ শিক্ষার্থীর বেলায় একই ব্যর্থতা দেখে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হই, স্কুল-কলেজগুলোতে আমরা ঠিকমতো লেখাপড়া করাচ্ছি না। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হবার আগে যখন ডিগ্রি পরীক্ষা ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত হতো তখন একটা কথা প্রায় প্রমাণিত ছিল যে ডিগ্রি পরীক্ষায় পাস করা যতোটা না কঠিন ছিল ঠিক সেরকম সহজ ছিল যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে (তখন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম হয়নি।) যে কোনো বিষয়ে ভর্তি হয়ে অনার্স, মাস্টার্স করে বের হয়ে আসা। ডিগ্রি সিলেবাস দু’বছরের থাকলেও, এটার পরীক্ষা পদ্ধতি ছিল পাবলিক পরীক্ষার আদতে। এখনো তাই। অন্যদিকে অনার্স, এমএ ছিল বিভাগের অন্তর্গত শিক্ষাব্যবস্থাধীন। এখনো তাই।
এ কথাটা তুলে আনলাম এ জন্য যে, যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের (এখন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাও ধরে বলছি।) অধীনস্ত কোনো বিভাগে অনার্স, মাস্টার্স করার জন্য ভর্তি হওয়ার অর্থ হলো শিক্ষার্থী নিশ্চিত ভালো বা খারাপ একটা সার্টিফিকেট নিয়ে বের হবেই। শিক্ষার্থী নিজে থেকে ড্রপ আউট না হলে শেষ পর্যন্ত সে রি-টেক টি-টেক দিয়ে একদিন বের হবেই।
বিশ্ববিদ্যালগুলোর সমস্যাটা এখানে বুঝতে হবে, তারা শিক্ষার্থী ভর্তি করাচ্ছে তাদেরই যারা মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার যোগ্যতা কাগজে-কলমে অর্জন করেছে।
‘বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার যোগ্যতা কাগজে-কলমে অর্জন করেছে’- এ কথাটা আবার সরলার্থে বলা যাবে না। এখানে স্বায়ত্তশাসিত এবং সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এক ধরনের সমস্যা আর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আরেক ধরনের সমস্যা বিরাজ করছে।
স্বায়ত্তশাসিত এবং সরকারি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সমস্যাটা হচ্ছে এত বিপুল পরিমাণে শিক্ষার্থী স্নাতক সম্মানে ভর্তি হবার জন্য আবেদন করে যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ইউনিটভিত্তিক পরীক্ষা নেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না এবং প্রশ্নপত্র হয় বহু নির্বাচনী বা মাল্টিপল চয়েস অনুযায়ী। শিক্ষার্থীর জনসংখ্যাধিক্যের কারণে এর বিকল্পও থাকে না।
ইউনিটভিত্তিক ভর্তি পরীক্ষা এখন সব ধরনের স্বায়ত্তশাসিত এবং সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু থাকলেও, কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে, আমার ধারণা, ইউনিটভিত্তিক পরীক্ষা অনুষদভিত্তিক ভর্তি পরীক্ষারই নামান্তর। দু’টোর মধ্যে সামান্য পার্থক্য আছে। অনুষদভিত্তিক ভর্তি পরীক্ষা নেওয়ার অর্থ হচ্ছে অনুষদের অন্তর্গত সকল বিভাগের ভর্তি পরীক্ষা ঐ অনুষদ দ্বারা পরিচালিত হবে।
আর ইউনিটভিত্তিক ভর্তি পরীক্ষায় ইউনিটের অধীনে বিভিন্ন অনুষদ থেকে ভেঙে বিভাগ অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। যেমন ধরুন, কোনো বিশ্ববিদ্যালয় ঠিক করল যে কলা অনুষদের নাম হবে ‘ক’ ইউনিট, বিজ্ঞান অনুষদ ‘খ’ ইউনিট, বাণিজ্য অনুষদ ‘গ’ ইউনিট, সমাজবিজ্ঞান ‘ঘ’ এবং এর বাইরে তারা একটা ‘ঙ’ নামে অতিরিক্ত ইউনিট খুলতে পারে যেখানে ‘চারুকলা’, ‘নাট্যকলা’, ‘সঙ্গীত’ ইত্যাদি সৃজনশীল বিভাগগুলো অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।
এ ছাড়াও অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা ইউনিট থাকে যেটার অধীনে শিক্ষার্থী তার অনুষদ বদলানোর জন্য পরীক্ষা দিতে পারে। এই ইউনিটের অধীনে একজন বিজ্ঞানের ছাত্র কলা অনুষদের অধীনে বা বাণিজ্য অনুষদের অধীনে কোনো বিভাগে ভর্তি হবার সুযোগ নিতে পারে। বা উল্টোটাও হতে পারে- কলার শিক্ষার্থী বিজ্ঞানে বা বাণিজ্যে যেতে পারে। এই ইউনিটটি ট্রানজিটের মতো কাজ করে।
আগেই বলেছি, ইউনিটভিত্তিক পরীক্ষাগুলো হয় বহু নির্বাচনী বা মাল্টিপল চয়েসের ভিত্তিতে। কিন্তু আমার বিবেচনায় এ ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি মৌলিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার চরিত্রের বিরোধী। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মূলত উচ্চশিক্ষার বিস্তারের কাজে নিয়োজিত। কিন্তু এটার কার্যকর ভিত্তি হলো উন্নত মানের শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে নতুন জ্ঞানের সৃষ্টি করা ও দেশ ও সমাজের প্রয়োজনে দক্ষ, সৎ, ভিশনারি ও দেশপ্রেমিক জনগোষ্ঠী তৈরি করা।
এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিচ্ছু যে কোনো শিক্ষার্থীর অভীষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে সে যে বিষয়ে পড়তে চায়, সে বিষয়ে ভর্তি হতে পারা। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ বিভাগগুলোরও লক্ষ্য হচ্ছে তাদের যার যার বিভাগে এমন শিক্ষার্থী ভর্তি হোক যাদের স্বকীয় প্রবণতা ঐ বিষয়গুলো পড়বার জন্য অস্তিত্বমান। কিন্তু অনুষদভিত্তিক কিংবা ইউনিট সিস্টেম প্রবর্তিত হবার পর থেকে বিভাগগুলোর আর নিজেদের বিষয়ানুযায়ী প্রবণতাসম্পন্ন শিক্ষার্থী ভর্তি করানোর সুযোগ বা স্বাধীনতা থাকে না। এটা বিভাগস্থ শিক্ষকেরা হাড়ে হাড়ে টের পান যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিকসংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য আবেদন করার প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিভাগ থেকে নির্বাচনী পরীক্ষা পরিচালনার অধিকার প্রত্যাহার করে অনুষদের ওপর দায়িত্ব দেয়।
এটা ছাড়া হয়তো উপায়ও ছিল না। এটা সম্ভবত আমি নব্বই দশকের শুরুর দিকের কথা বলছি। অনুষদভিত্তিক পরীক্ষা পরিচালনার আগে আগে দুই কি তিন বছর বিশ্ববিদ্যালয়গুলো চেষ্টা করেছিল বিভাগের অধীনেই নির্বাচনী পরীক্ষা চালু রাখা। তখন সমস্যাটা তৈরি হলো এ জন্য যে যাতে শিক্ষার্থীরা একাধিক বিভাগে ভর্তি হবার সুযোগ নিতে পারে সে জন্য আলাদা আলাদা দিনে বিভাগগুলোর অধীনে পরীক্ষা নেওয়া শুরু হলো। যেমন, তখন বাংলা এবং ইংরেজির পরীক্ষা, কিংবা পদার্থ বিজ্ঞান এবং রসায়ন বিজ্ঞানের পরীক্ষা একই সময়ে হতো না, পারস্পরিক সমানুগতার জন্য।
ফলে পরীক্ষা নেওয়া, ফলাফল বের করা ইত্যাদি প্রশাসনিক জটিলতায় দেখা গেল যে এক একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে দেড় থেকে দু’মাস শুধুমাত্র ভর্তি পরীক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক ক্লাস ও পরীক্ষাসহ বিভিন্ন নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রম চালানো গেল না। ফলে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হলো যে বিভাগগুলোর বদলে সংশ্লিষ্ট অনুষদই পরীক্ষা নেবে। তখন অনুষদভিত্তিক পরীক্ষা নেওয়া শুরু হলো। অর্থাৎ বিভাগ কর্তৃক পরীক্ষা নেওয়ার অধিকার প্রত্যাহার করে অনুষদের ওপর পরীক্ষা নেওয়ার দায়িত্ব বর্তায়। তখন থেকেই আসলে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার মৌলিক চরিত্রের বিপরীতে হাঁটা শুরু হলো।
কারণ আগে যেমন বিভাগগুলোর- বিস্তর সময়ক্ষেপণ হলেও বিষয়ভিত্তিক প্রবণতা অনুযায়ী ১০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা নিয়ে তারপর নির্বাচিতদের মৌখিক পরীক্ষায় ডেকে বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন করে যাচাই-বাছাই করে উপযুক্ত শিক্ষার্থী নির্বাচনের সুযোগ ছিল, সেটি আর রইলো না। তারপরও অনুষদভিত্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে বাংলা এবং ইংরেজিসহ অনুষদের অধীনস্থ বিভাগুলোর ওপর সামান্য প্রশ্ন থাকতো, যার উত্তর লিখিতভাবে পরীক্ষার্থীকে দিতে হতো এবং ফলে ভর্তি ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের কিছুটা হলেও যাচাইয়ের সুযোগ ছিল। তারপরও আমরা বিভাগের শিক্ষকরা ক্রমাগত শিউরে উঠতে থাকি যে এমন এমন শিক্ষার্থী বিভাগে ভর্তি হবার জন্য যোগ্যতা লাভ করেছে যাদের না আছে ইংরেজি ভাষায় সাধারণ দক্ষতা, না আছে সাহিত্যের প্রতি ভালোবাসা।
অন্যান্য বিভাগের শিক্ষক-সহকর্মীরাও তাদের নিজ নিজ বিষয়ের জন্য নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের মান সম্পর্কেও একই হতাশা ব্যক্ত করতে লাগলেন। কিন্তু তারপরও যখন ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া ও গ্রহণ করার প্রক্রিয়ায় সংখ্যা ও সময়ের মধ্যে দ্বান্দ্বিক সংকটটি আরো ঘনীভূত হলো, তখন একনাগাড়ে স্বায়ত্তশাসিত এবং সরকারি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনুষদভিত্তিক পরীক্ষা পদ্ধতির বদলে ইউনিট সিস্টেমের প্রবর্তন হলো এবং তখন থেকেই, আমার ধারণা, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির প্রক্রিয়াতে বড় ধরনের পতন হলো। উচ্চশিক্ষাব্যবস্থা কড়াই থেকে আগুনে পড়ল। পতনটি এমন যে এটাকে কোনো পরিসংখ্যান দিয়ে সমর্থন করা যাবে না, কারণ ক্ষতিটা হয়ে গেছে আরো গভীরে- শিক্ষার চরিত্র গঠনে।
কেমন করে এ পতনটা হলো একটু ব্যাখ্যা করি। ইউনিট সিস্টেমে পুরো ১০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা হয় বহু নির্বাচনী প্রশ্ন পদ্ধতিতে। বাংলা, ইংরেজি এবং সাধারণ জ্ঞান- এ তিন বিষয়ে সাধারণত নম্বর ভাগ করা হয়। সাধারণ জ্ঞান বিষয়টা হচ্ছে একটা আমব্রেল্লা কনসেপ্টের অধীনে প্রকারান্তরে সমাজবিজ্ঞানভিত্তিক বিষয়গুলোর ওপর জ্ঞান যাচাই করা হয়।
আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের চাহিদা অনুযায়ী কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে অংক শাস্ত্রের ওপরও প্রশ্ন থাকে। তবে এ নিয়মগুলোর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে হেরফেরও হতে পারে। তবে ইংরেজিতে যেহেতু অধিকাংশ শিক্ষার্থী খারাপ করে সে জন্য ইংরেজিতে পাস মার্ক অন্য দুই বিষয়ের চেয়ে কম থাকে।
আবার যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজিতে অনার্স, এমএ আছে সে সব বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজির ওপর বিশেষ কিছু প্রশ্ন থাকে এবং একটা পাস মার্কও ধার্য করা থাকে যেটাতে পাস করলে সে ইংরেজি অনার্সে ভর্তি হতে পারবে। পারবে, কিন্তু এখানেও একটা ফ্যাকড়া আছে। সেটা হলো শিক্ষার্থী শুধু ইংরেজি বিষয়ে পাস করলে হবে না, তাকে টোটাল ১০০ নম্বরের মধ্যে টিকে থাকতে হবে।
অর্থাৎ, ব্যাপারটা এরকম- ধরুন, একজন শিক্ষার্থী ১০০ নম্বরের মধ্যে পেয়েছে ৫১, কিন্তু বিশেষ ইংরেজিতে সে ৩০-এ পেয়েছে ২৫, এবং সাধারণ ইংরেজিতে পেয়েছে ২০-এ ১৮, আর বাকি ৫০ নম্বর বাংলা ও সাধারণ জ্ঞানে পেয়েছে মাত্র ৮। কিন্তু যারা ইংরেজিতে তার মতো মার্ক পায়নি কিন্তু সব বিষয় মিলিয়ে ৭০/৭৫ পেয়েছে, তারা সিরিয়ালি টিকে যাবে কিন্তু সে টিকবে না। অথচ সে ইংরেজি অনার্স পড়ার জন্য ছিল উপযুক্ত শিক্ষার্থী।
আবার একই কথা বাংলা বা সাধারণ জ্ঞানের বিষয়ে ভর্তি ইচ্ছুক শিক্ষার্থীর জন্যও প্রযোজ্য হতে পারে। কেউ হয়তো বাংলায় খুব ভালো করলো, বা সাধারণ জ্ঞানে খুব ভালো করলো, কিন্তু অন্য দুই বিষয়ে ভালো করল না বলে সে ভর্তি পরীক্ষায় টিকতে পারলো না। অথচ সে হয়তো বাংলা বা সমাজবিজ্ঞানের জন্য উপযুক্ত শিক্ষার্থী ছিল।
ফলে হতাশার সঙ্গে লক্ষ করা যায়, যে শিক্ষার্থীর ইংরেজি পড়ার কথা নয় সে ইংরেজিতে ঢুকে গেল, যার ভূগোল পড়ার কথা নয়, সে ভূগোলে এবং যার চারুকলা পড়ার কথা নয় সে চারুকলায় ঢুকে গেল। এবং এ ধরনের মিসফিট শিক্ষার্থীর জন্য পুরো অনার্স এবং মাস্টার্সের লেখাপড়া, যদি সে শেষ পর্যন্ত মানিয়ে নিতে না পারে, তা হলে তার বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনটা একরকম অপচয়িত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়। এবং এ ধরনের মিসফিট শিক্ষার্থীরা বিভাগীয় শিক্ষকদের জন্যও ডিমোটিভেশনাল ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে।
আরেকটি কারণে বহু নির্বাচনী প্রশ্নভিত্তিক ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মৌল-চরিত্রের বিপক্ষে। সেটি হচ্ছে, বহু নির্বাচনী পরীক্ষাটা হয় মূলত শিক্ষার্থীর চিন্তা শক্তির পরীক্ষা করার জন্য নয়, হয় কিছু প্রশ্নের বিপরীতে সে খুব দ্রুত ঠিক উত্তরটি দিতে পারে কিনা। এবং না জেনে আন্দাজে সঠিক উত্তর দেবার অবকাশও এখানে থাকে। যদিও ভুল উত্তরের জন্য তার মার্ক কাটা যেতে পারে। সে যা হোক, এ ধরনের পরীক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর প্রকৃত প্রবণতার কোনো পরীক্ষা হয় না। এ বহু নির্বাচনী পরীক্ষার ছকটা বিজ্ঞানভিত্তিক বিষয়গুলোর জন্য কিছুটা কার্যকর হলেও মানবিক এবং সমাজবিজ্ঞান কিংবা ব্যবসাবিজ্ঞানভিত্তিক বিষয়গুলোর জন্য কার্যকর নয়।
আমার বিবেচনায় ভুল শিক্ষার্থী ভুল বিভাগে ভর্তি হবার এ যে মহাযজ্ঞ চলছে এতে প্রকারান্তরে জাতীয় উচ্চশিক্ষার ক্ষতি হচ্ছে। এটা বন্ধ করে কোনো না কোনোভাবে বিভাগের কাছে নিজেদের বিষয় অনুযায়ী যোগ্য প্রবণতা প্রদর্শনকারী শিক্ষার্থীকে ভর্তি করানোর সুযোগ ও অধিকার বিভাগের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত। না হলে আমরা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিরাট ধরনের আত্মপ্রবঞ্চনার শিকার হয়ে যাচ্ছি। এটা কি পদ্ধতিতে করা যেতে পারে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কর্তৃপক্ষ ইউজিসি এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে ঠিক করে নিতে পারে।
তবে এ রিভার্স মোডে যেতে গেলে প্রধান প্রতিবন্ধকতা আসবে অর্থনৈতিক কারণে। ইউনিট সিস্টেমে আবেদন জমা পড়ার প্রক্রিয়ায় একটা বিরাট অর্থনৈতিক সাফল্য আসে, যার অর্থনৈতিক ফল ভোগ করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সকলেই- উচ্চপ্রশাসন থেকে শুরু করে সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও সকল শিক্ষক। সম্ভবত মোট আয়ের শতকরা হিসাবে একটি ধার্যকৃত অংশ সরকারের তহবিলে জমা দিতে হয়, কিংবা সরকার সেটা কেটে রাখেন বার্ষিক বাজেট অনুমোদনের বেলায়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য ভর্তি পরীক্ষার মৌসুমটা হচ্ছে দেবী লক্ষ্মীর বর। দেবী সরস্বতীর এখানে কিছু করার নেই।
এ জন্য ভর্তি সংক্রান্ত সংকট হ্রাস করার জন্য ভর্তি পরীক্ষা গুচ্ছ পদ্ধতিতে নেবার যে আহ্বান মহামান্য রাষ্ট্রপতি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে করে থাকেন, সেটি কখনো কার্যকর হয় না এই অর্থনৈতিক স্বার্থটার কারণে।
স্বায়ত্তশাসিত এবং সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যেমন মোটা অর্থে শিক্ষার্থী পাওয়া সমস্যা নয়, সেখানে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মূল সমস্যা হচ্ছে শিক্ষার্থী পাওয়া, বা আরো স্পষ্ট করে বললে উপযুক্ত শিক্ষার্থী পাওয়া। দেশে সম্ভবত এখন ৪টি স্বায়ত্তশাসিত, ৪৫টি সরকারি ও প্রায় শখানেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আছে।
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে হয়তো গোটা বিশেক বিশ্ববিদ্যালয় স্বয়ংসর্ম্পূণভাবে চলছে, কিন্তু বাকিগুলো নানা কারণে ধুঁকছে। কারো জায়গা নেই, কারো বিল্ডিং নেই, কারো শিক্ষক নেই, কারো হয়তো উপাচার্য বা উচ্চ প্রশাসনের কেউ নেই, এবং কারো কারো হয়তো শিক্ষার্থী নেই। ফলে অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে শিক্ষার্থী ভর্তির প্রক্রিয়ায় প্রচ্ছন্নভাবে নিশ্চিত কিছু আপসের মধ্য দিয়ে যেতে হয়।
এ আপসটা মেনে নিলেও এটার পেছনে একটি কার্যকর দর্শন আছে কিন্তু- সেটি হচ্ছে ছাইকে স্বর্ণে পরিণত করা। এবং এটাতো সত্য যে যদি ইংরেজিতে এসএসসি এবং এইচএসসিতে ‘এ প্লাস’ পাওয়া শিক্ষার্থী ‘গরু ঘাস খায়’ ট্রান্সলেশনটা করতে না পারে, তাতে শিক্ষার্থীর মেধার নয়, শিক্ষাপদ্ধতির প্রকৃতি নিয়েই প্রশ্নটা উঠবে। সে জায়গায় রবীন্দ্রনাথের ভাষায় “যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখিও তাই, পাইলেও পাইতে পারো অমূল্য রতন” (স্মৃতি থেকে লিখেছি, উদ্ধৃতি ভুলও হতে পারে।) পদ্ধতিতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শিক্ষা প্রদান করে থাকে বলে আমার ধারণা।
তবে একটি জঙ্গম সমাজ সবসময় বিকল্প ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল থাকে। যেমন গুড়ের অভাবের কারণে এক সময় সমাজে চিনির প্রচলন শুরু হয়ে গেল, তেমনি স্বায়ত্তশাসিত এবং সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো উচ্চশিক্ষার ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলন শুরু হয়। এর ফলে ছেলেমেয়েদের বিদেশে পাঠানোর প্রবণতা অনেকাংশে কমে। এ জন্য দেখা গেছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর খামতি নিয়ে বেশি ধরাধরি করলে নেতিবাচক প্রচারণার জন্য তাদের শিক্ষার্থী ভর্তি কমে গেলে আবার ছেলেমেয়েদের বিদেশে পাঠানোর প্রবণতার শুরু হয়। সব শৃঙ্খলাযুক্ত তরিকারই ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দিক আছে।
বস্তুত বাংলাদেশের শিক্ষার্থী প্রজন্মের জনসংখ্যা চিন্তা করলে বাংলাদেশে আসলে ৫০০টি বিশ্ববিদ্যালয় থাকা দরকার। আজকেই (৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯) পত্রিকায় দেখলাম বান্দরবানের দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তরের উদ্বোধনের ছবি। বাংলাদেশের মতো জনবহুল কিন্তু সংকুচিত ভূমির দেশে উচ্চশিক্ষার আনুভূমিক বা সমতল সম্প্রসারণ ঠেকানো যাবে না।
সেজন্য বেসরকারি খাতে উচ্চ শিক্ষাব্যবস্থাকে যেতেই হবে। এবং ফলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়বেই। কাজেই একটা খাত বৃদ্ধি পাওয়া যদি অবশ্যম্ভাবি হয়ে পড়ে, সে খাতটি যাতে ভালোভাবে উপযুক্ততা লাভ করে তার দিকেও লক্ষ রাখতে হবে। এখানে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের উচ্চতর ডিগ্রি লাভের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি কল্পে এবং সাধারণভাবে উচ্চতর ডিগ্রি গ্রহণের ইচ্ছা পোষণকারী শিক্ষার্থীর তৃষ্ণা মেটাতে একটি কথা প্রস্তাবনার আকারে দিতে চাই। সেটি হলো যোগ্যতার নিরিখে ক্রমান্বয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েও মাস্টার্স-পরবর্তী এমফিল এবং পিএইচডি ডিগ্রি প্রদানের সক্ষমতার অনুমতি দেওয়া।
বাস্তবতার নিরিখে বলছি, বর্ষীয়ান অনেক শিক্ষক স্বায়ত্তশাসিত ও সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর নিয়ে বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন পদে নিয়োজিত আছেন পূর্ণকালীন সময়ে। তাদের দ্বারা এমফিল, পিইচডি প্রোগ্রাম চালু করা যায়। বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ মানের পাঠাগার এবং অনলাইন সুযোগ পাকাপোক্তভাবে আছে। কাজেই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে যোগ্যতা পূরণ সাপেক্ষে এমফিল এবং পিইচডি ডিগ্রি প্রোগ্রাম খোলার অনুমোদন দেওয়া যায়। আমি নিশ্চিত এটাতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার চরিত্রও আমূল বদলে যাবে।
কারণ এই অনুমতি বিরাট একটা মোটিভেশনাল ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করবে। আরেকটা কথা, অর্থনীতিতে ‘ব্যাড মানি ড্রাইভস গুড মানি আউট অব সার্কুলেশন’ হলেও, সমাজ ক্রমশ সর্বত্র সুশৃঙ্খলিত হতে থাকলে এর উল্টোটাই ঘটবে। অর্থাৎ, ‘গুড মানি ড্রাইভস ব্যাড মানি আউট অব সার্কুলেশন’ হবে। সেদিনের অপেক্ষা বেশিদিন করতে হবে বলে মনে হয় না।