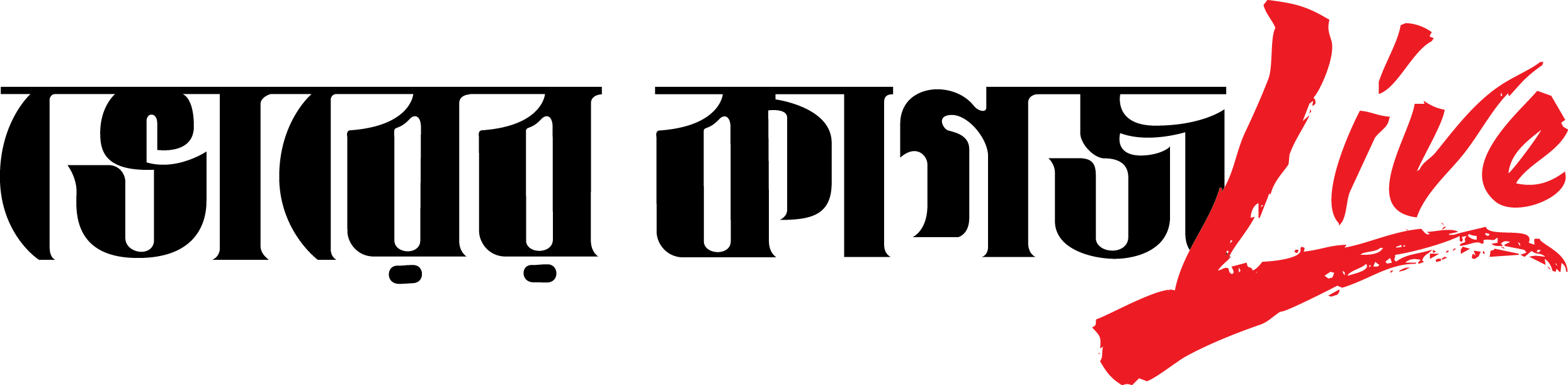লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির সেকাল একাল
কাগজ প্রতিবেদক
প্রকাশ: ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯, ০৭:০৭ পিএম
চট্টগ্রামে যখন থেকে জনবসতি শুরু হয়েছিল তখন থেকে আজ পর্যন্ত লোকসঙ্গীত চট্টগ্রামের লোকজীবনের ভূষণ হয়ে রয়েছে। লোকজীবনের গান সুপ্রাচীন কাল থেকেই এ দেশের গ্রামাঞ্চলের আকাশ-বাতাসকে মুখরিত করে রাখছে। রাজশাহী-রংপুর অঞ্চলের ভাওয়াইয়া, মালদহের গম্ভীরা, ভাটি অঞ্চলের ভাটিয়ালির মতো চট্টগ্রামের লোকসঙ্গীতও বাংলার লোকসঙ্গীতকে করেছে সমৃদ্ধ। গাজির গান, হালদাফাটা গান, হঁঅলা, হাইল্যা সাইর, পাইন্যা সাইর, পালাগান বা গীতিকা, মাইজভাণ্ডারি, শিব-গৌরীর গান, উল্টা বাউলের গান, কানুফকিরের গান, আসকর আলী পণ্ডিদের গান, ফুলপাট গান, ওলশা মাছের গান চট্টগ্রামের একান্ত নিজস্ব সম্পদ। অতি বর্ষীয়ান ব্যক্তিদের মুখ থেকে জানা যায়, প্রাচীন চট্টগ্রামের জনজীবনে আরও অনেক রকমের গান প্রচলিত ছিল। বিয়ে ইত্যাদি সামাজিক অনুষ্ঠানে এসব গাওয়া হতো। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সেগুলো ক্রমে লোপ পেতে থাকে।
উপমহাদেশের অন্যান্য জায়গার মতো চট্টগ্রামের জীবন ও সংস্কৃতি ছিল গ্রামীণ। চট্টগ্রাম ও আরাকান সুপ্রাচীন কাল থেকে খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতক পর্যন্ত একটি অখণ্ড রাজ্যরূপে শাসিত হতো। অর্থাৎ একদেশ বলে পরিগণিত হতো। সেজন্যে এই গ্রামীণ সংস্কৃতিতে ছিল বর্মী প্রভাব এবং তাতে এখানকার জনগোষ্ঠীর এক বিশেষ পরিচয় গড়ে ওঠে।
পরবর্তীকালে আরাকান রাজাদের কোন্দলের সুযোগ নিয়ে সমতট ও হরিকেল রাজ্যভুক্ত হয় চট্টগ্রাম। তখনও সমতট ও হরিকেলের রাজা-শাসকদের সঙ্গে আরাকানের রাজাদের প্রায়শ যুদ্ধবিগ্রহ লেগে থাকতো। এজন্য কারো শাসনই নিরঙ্কুশ হয়নি। তবে বিবদমান দুপক্ষই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হওয়ায় চট্টগ্রামে বৌদ্ধ সংস্কৃতি প্রসারে বিঘ্ন ঘটেনি এবং এর প্রভাব এখানকার শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিতেও পড়েছে।
চট্টগ্রামে পরিবেশন শিল্পের ইতিহাস পাওয়া যায় সামান্য। তবে অনুমান করা যায়, যেহেতু গান-নাচ-নাটক আদিম মানব সমাজেও ছিল সে জন্য চট্টগ্রামেও মানব বসতির কাল থেকে এসব পরিবেশনা শিল্প চলে আসছে।
সঙ্গীতের ক্ষেত্রে দেখা যায়, চট্টগ্রামে লোকসঙ্গীত মানব-বসতির সময় থেকে চলে এলেও রাগসঙ্গীত বা উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের ইতিহাস অপেক্ষাকৃত কম প্রাচীন। তবে তার বয়সও হাজার বছরের ওপর। বাংলার সবচেয়ে প্রাচীন গান চর্যাগীত। চর্যাকারদের মধ্যে কয়েকজন চট্টগ্রামের অধিবাসী বলে পণ্ডিতরা দাবি করেছেন।
তা ছাড়া, প্রাচীন বৌদ্ধ-তিব্বতি ভাষাসাহিত্য বিশারদ রায়বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাশ-এর এন্টিকুইটি অব চিটাগাং নিবন্ধে উল্লেখ আছে, দশম শতাব্দীতে চট্টগ্রামে ‘পণ্ডিত বিহার’ নামে একটি বৌদ্ধ বিহার ছিল। এতে ‘কানুপাদ’, ‘হাড়িপাদ’ ‘শবরীপাদ’ প্রমুখ চর্যাকাররা অধ্যাপনা করতেন বলে পণ্ডিতদের অনুমান। অতএব বলা যেতে পারে, হাজার বছর আগে চট্টগ্রামে রাগসঙ্গীতের চর্চা কমবেশি হতো।
লোকসঙ্গীতের প্রাচীন নিদর্শন : ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ‘চর্যাপদ’ নামে নিদর্শনটি নেপালের রাজদরবার থেকে আবিষ্কার করেন। বলাবাহুল্য, আবিষ্কারের প্রায় ৯ বছর পর তিনটি পুঁথির সাথে একত্রে প্রকাশ করেন ‘হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষার বৌদ্ধগান ও দোহা’ নামে।
এতে তিনি বলেন, ‘১৯০৭ সালে আবার নেপালে গিয়া আমি কয়েকটি পুঁথি দেখিতে পাইলাম। একখানির নাম ‘চর্য্যাচয্যাবিনিশ্চয়’, উহাতে কতগুলি কীর্তনের গান আছে ও তাহার সংস্কৃতি টীকা আছে। গানগুলো বৈষ্ণবদের কীর্তনের মতো, গানের নাম চর্যাপদ।
আর একখানি পুঁথি পাইলাম তাহাও দোহাকোষ, গ্রন্থকারের নাম সরোজবজ্র, টীকাটি সংস্কৃতে, টীকাকারের নাম অদ্বয়বজ্র। আরও একখানি পুস্তক পাইলাম তাহার নামও দোহাকোষ, গ্রন্থকারের নাম কৃষ্ণাচার্য্য, উহারও একটি সংস্কৃত টীকা আছে (পৃ-৪-৫, ২য় সংখ্যা)। গ্রন্থভুক্ত
‘ডাকার্ণব’ পুঁথির উল্লেখ এ উদ্ধৃতিতে নেই। না বললেই নয়, যদিও গ্রন্থের নাম হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা’ কিন্তু গ্রন্থভূক্ত চারটি পুঁথির মধ্যে কেবল চর্যার ভাষাই বাঙ্গালা। আলোচনার মাধ্যমে সর্বপ্রথম এ কথা প্রমাণ করেন ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় (The Origin and Development od the Bengali Language, 1916) চর্যাপদ পাঠে লক্ষণীয়, প্রতিটি চর্যাই গান এবং এগুলোর রচয়িতা বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যরা।
লুইপাদানং, কুক্কুরীপাদানং, বিরুবাপাদানং, গুণ্ডরীপাদানং, চাটিল্লপাদানং, ভুসুকুপাদানং, কাহ্নপাদানং, ঢেন্টণপাদানং প্রমুখ সিদ্ধাচার্যের নাম এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। এঁরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী নয়, বৌদ্ধ লোকধর্মের অনুসারী। চর্যাসমূহে এরা ‘লোক’ হিসেবে নিজেদের দুঃখ-বেদনা এবং এঁদের অনুসৃত লোকধর্মকে কেন্দ্র করে ধর্ম সাধনার কথা ব্যক্ত করেছেন। দু’টি চর্যা উপস্থাপন করা যাক (চর্যাগীতি পরিচয়/ ড. সত্যব্রত দে থেকে) :
রাগ পটমঞ্জরী, ঢেন্টণপাদানং টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী। হাড়িত ভাত নাহি নিতি আবেশী ॥ বেগ সংসার বড়হিল জাঅ। দুহিল দুধু কি বেন্টে যামাঅ ॥ ধ্রু। বলদ বিআএল গবিআ বাঝেঁ। পিটা দুহিএ এ তিনা সাঝোঁ ॥ ধ্রু। জো সো বুধী সৌধ নিবুধী। জে যো চৌর সৗ দুষাধী ॥ ধ্রু। নিতে নিতে ঘিআলা যিহে যম জুঝঅ। ঢেন্টণপাএর গীত বি (চি)রলে বুঝঅ ॥ ধ্রু।
টিলায় আমার ঘর, প্রতিবেশী নাহি। হাঁড়িতে ভাত নেহি, নিত্য আবেশী (অতিথি) সমাগম। বেগে অথবা ব্যাঙের (সংসারের মতো) সংসার বাড়িয়াই চলে, অথবা অঙ্গহীন সংসার বাড়িয়াই চলে। দোয়া দুধ কি বাঁটে প্রবেশ করে? বলদ প্রসব করিল, গাভী বন্ধ্যা। পাত্র দোহন করা হইল এই তিন সন্ধ্যা। যে বুদ্ধিমান সেই নির্বোধ। যে চোর সেই সাধু, অথবা কোটাল বা চর। প্রতিদিন শৃগাল সিংহের সহিত যুদ্ধ করে। ঢেন্টণপদের গীত কম লোকেই বোঝে।
রাগ বরাড়ী ভুসুকুপাদানং জই তুমহে ভুসুকু অহেই জাইবেঁ মারিহসি পঞ্চজনা। নলণী বন পইসন্তে হোহিসি একমণা ॥ ধ্রু। জীবন্তে ভেলা বিহণী মএল ণএণি। হন বিনু মাঁসে ভুসুক পদ্মবণ পইসহিণী ॥ ধ্রু। মাআজাল পসরিউ রে বাধেলি মাআহরিণি। সদগুরু বোহেঁ বুঝি রে কাসু কদিনি।
যদি তুমি ভুসুক শিকারে যাইবে তবে পঞ্চজনকে মারিও। নলিনীবনে প্রবেশে একমনা হইও। জীবন্তে প্রভাত হইল, মরিল রজনী। নিহতের মাংস বিনা, ভুসুক, পদ্ম বনে প্রবেশ করিও না। মায়াজাল অপসারিত হইল, বাঁধা পড়িল মায়াহরিণী। সদগুরুরোধে বুঝি কিসের কি কাহিনী (বৃত্তান্ত)।
হরফের উদ্ভাবন এবং তার বিবর্তন শেষে এই অঞ্চলের জনমানুষের ধ্বনি ও শব্দ যোগে ভাব বিনিময়ে কোনো অসুবিধা আর থাকল না। ভাবকে হরফ বন্দি করার দক্ষতাও তারা ততদিনে অর্জন করেছে। নয়তো চর্যাপদ-এর প্রসার এবং সমাদর হতো না। ‘বঙ্গ’-শব্দটিও জাতি পরিচয় নিয়ে সিদ্ধ/যোগীদের গানে উঠে এসেছে-
অদঅ বঙ্গাল দেশ লুডিউ, আজি ভুষুক বঙ্গালী ভইলী।
বঙ্গালদেশ আজ লুণ্ঠিত। ভুষুক আজ তুমি বাঙ্গালী মাত্র। চর্যা-৪৯। ভুষুক পাদানাম।
বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের ‘বঙ্গাল’ ও ‘বাঙ্গালী’ শব্দ দু’টি পরবর্তী যুগে ফারসি ‘বাঙ্গালাহ’ শব্দের ওপর পূর্ব অঞ্চলের দেশটি জরিপকালে কোনো প্রভাব রেখেছিল কিনা তা নির্ণয় করা হয়নি। মনে হয় কালে কালে ‘বাঙ্গাল’ ও ‘বাঙ্গালী’ শব্দ দুটিও লোকমুখে ভিন্নরূপ নিতে থাকে। ‘বা-আল’ কথাটির ঐতিহ্যের প্রাচীনতা সম্ভবত এখানেই কিছুটা নির্ধারিত হয়ে আছে।
চর্যাপদ (পুঁথির নাম নিয়ে বিতর্ক রয়েছে) আবিষ্কার ও প্রকাশের পর তা মূলত বাংলাভাষা ও সাহিত্যের আদি নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিত হয়। কিছু গবেষক একে লোকসঙ্গীত বা লোকসাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন হিসেবেও চিহ্নিত করেন। ড. আনোয়ারুল করিম প্রমুখের নাম এক্ষেত্রে উল্লেখনীয়।
তিনি ‘বাংলাদেশের বাউল : সমাজ, সাহিত্য ও সঙ্গীত’ নামক গ্রন্থের ৩৯৫ পৃষ্ঠায় বলেন, ‘লোকধর্মভিত্তিক সাধনসঙ্গীতই বাংলাদেশের লোকসঙ্গীতের আদিতম প্রকাশ। চর্যাপদ বা বৌদ্ধগান ও দোহা শুধু বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদিম রূপের পরিচয় বহন করে না, বরং বাংলাদেশের মাটি ও মানুষের এযাবৎকাল আবিষ্কৃত লোকধর্মনির্ভর গণমুখী লোকসাহিত্যের সার্থক প্রকাশ বলেও তা স্বীকৃত। (বর্ণায়ন, জানুয়ারি ২০০২)।
মধ্যযুগেও চট্টগ্রামে যে রাগসঙ্গীতের প্রচলন ছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। চৈতন্যযুগে চট্টগ্রামে কীর্তন গানেরও প্রথম প্রচলন হয়। কারণ শ্রীচৈতন্যের অন্যতম পার্ষৎ পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ছিলেন হাটহাজারী থানার মেখলের অধিবাসী। চৈতন্যের দেহাবসানের পর পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি চট্টগ্রামে বসবাস করতে শুরু করেন এবং এতই পারঙ্গমতা অর্জন করেছিলেন যে চৈতন্যদেব আগ্রহ ভরে তাঁর কীর্তন শুনতেন।
মধ্য যুগে রাগসঙ্গীত চর্চার আরও প্রমাণ, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সংগৃহীত ১৯টি রাগনামা ও ১৩টি রাগতালনামা পুঁথি। এছাড়া ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকও রাগ-তাল সম্পর্কিত কয়েকটি পুঁথি চট্টগ্রামের পল্লী অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করেন। এসব পুঁথির রচয়িতারা চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ১
৭১৭ খ্রিস্টাব্দে রাউজানের তৎকালীন জমিদার ওয়াহিদ মুহম্মদ চৌধুরীর আদেশে ফাজিল নাসির মুহাম্মদ রচিত রাগমালা পুঁথির অবিকৃত রূপ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগে রক্ষিত আছে। মধ্যযুগে যাঁরা রাগসঙ্গীত চর্চা করতেন সাধারণভাবে তাঁদের ‘পণ্ডিত’ বলা হতো। এই পণ্ডিতদের মধ্যে চম্পাগাজী, কমর আলী, হারিস, গুলবকশ্, কাদের বক্শ, ওয়ারিশ প্রমুখের নাম আজও লোকস্মৃতিতে ক্ষীণভাবে বিদ্যমান।
এছাড়া আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত রাগমালাগুলোতে যে- ক’জন সঙ্গীত শাস্ত্রকারের নাম পাওয়া গেছে তাঁরা হচ্ছেন : ষোল শতকের মীর ফয়জুল্লাহ, সতেরো শতকের আলাওল, আঠার শতকের ফাজিল নাসির মুহম্মদ, কাজী দানিশ, শাহ আলী রজা, চম্পাগাজী, বখ্শ আলী, মুজফ্ফর, তাহির মাহমুদ, দ্বিজ রঘুনাথ, পঞ্চানন্দ, ভবানন্দ, দ্বিজ রামতনু, রামগোপাল, মুহাম্মদ পরাণ, গুল মুহাম্মদ খলিফা এবং আকবর শাহ পণ্ডিত।
সঙ্গীত শাস্ত্রকার আবদুল ওহাব চট্টগ্রামের আদি সঙ্গীত শাস্ত্রকারের বর্ণনা করেছেন এই ভাবে- প্রথমেতে দ্বিজ রঘুনাথ কবিবর মধ্যে মধ্যে ভবানন্দ গাহিছে সুন্দর। তার পাছে দানিশ কাজী অতি জ্ঞানবান, নিয়ম করিয়া দিল সময় কাটনি কোন্ সমে কোন্ রাগা গাহিব রাগিণী। উল্লেখ্য যে, আবদুল ওহাব তাঁর নিজের পরিচয় দিয়েছেন- পিতা মম তমিজুদ্দিন প্রকাশ সারাং নিবাসী ওয়াহেদপুর থানা মিরেরসরাই।
চট্টগ্রামে যখন থেকে জনবসতি শুরু হয়েছিল তখন থেকে আজ পর্যন্ত লোকসঙ্গীত চট্টগ্রামের লোকজীবনের ভূষণ হয়ে রয়েছে। লোকজীবনের গান সুপ্রাচীন কাল থেকেই এ দেশের গ্রামাঞ্চলের আকাশ-বাতাসকে মুখরিত করে রাখছে। রাজশাহী-রংপুর অঞ্চলের ভাওয়াইয়া, মালদহের গম্ভীরা, ভাটি অঞ্চলের ভাটিয়ালির মতো চট্টগ্রামের লোকসঙ্গীতও বাংলার লোকসঙ্গীতকে করেছে সমৃদ্ধ।
গাজির গান, হালদাফাটা গান, হঁঅলা, হাইল্যা সাইর, পাইন্যা সাইর, পালাগান বা গীতিকা, মাইজভাণ্ডারি, শিব-গৌরীর গান, উল্টা বাউলের গান, কানুফকিরের গান, আসকর আলী পণ্ডিদের গান, ফুলপাট গান, ওলশা মাছের গান চট্টগ্রামের একান্ত নিজস্ব সম্পদ। অতি বর্ষীয়ান ব্যক্তিদের মুখ থেকে জানা যায়, প্রাচীন চট্টগ্রামের জনজীবনে আরও অনেক রকমের গান প্রচলিত ছিল। বিয়ে ইত্যাদি সামাজিক অনুষ্ঠানে এসব গাওয়া হতো।
কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সেগুলো ক্রমে লোপ পেতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে ভারতে ব্রিটিশ শাসন ও পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে সমাজজীবনে ধীরে ধীরে যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তার প্রভাবে এ দেশের লোক সংস্কৃতিতেও ঘটেছে রূপান্তর। সমাজ বদলের সঙ্গে সঙ্গে রুচিরও পরিবর্তন হয়েছে। সংস্কৃতির রূপান্তরের কারণে এখানকার অনেক লোকসম্পদও ক্রমে বিলুপ্ত হয়েছে। কিন্তু এরপরও যা এখনো রয়েছে তার জন্য চট্টগ্রামবাসী গর্ব করতে পারে।
চট্টগ্রামী ভাষায় রচিত গ্রাম-চট্টলার জনমানুষের চিত্র সংবলিত গান এখনও দেশ-বিদেশের রসিক মনকে মোহিত করে। আজও চট্টগ্রামের শিল্পী শ্যামসুন্দর বৈষ্ণব-শেফলী ঘোষ জুটির কণ্ঠে গীত ‘চাঁটগাইয়া গান’ বাংলাদেশের বাইরেও সমাদৃত। চট্টগ্রামের লোকগীতি ছাড়াও এ দেশের মানুষ প্রাচীনকাল থেকে কীর্তন, শ্যামা সঙ্গীত, জারি, সারি, বারমাসি, বাউল-মুর্শিদি, মারফতি, কবিগান ইত্যাদির চর্চা করে আসছে। উপমহাদেশ জুড়ে রয়েছে চট্টগ্রামের কবিগান-এর খ্যাতি।
গাজির গান- সাধারণ মানুষের কাছে এলাকা ভেদে গাজির গান, গাইনের তামাসা, গাইনের পালা ইত্যাদি নামেও পরিচিত ছিল। চট্টগ্রামের লোক সাহিত্য গ্রন্থের লেখক কবি ওহীদুল আলম গাজির গানর সংজ্ঞা দিয়েছেন, ‘ধর্মযুদ্ধে যারা লড়াই করে, বীরত্ব দেখায় তারা গাজি, তাই গাজির গান বীরত্বব্যঞ্জক গান। ইহাতে লড়াইর বর্ণনা, শৌর্যবীর্যের কাহিনী বর্ণিত।’ কিন্তু চট্টগ্রামে সমাজ ও সংস্কৃতির গবেষক আবদুল হক চৌধুরী ভিন্নমত পোষণ করেন।
তাঁর মতে, গাজির গানে পালার গায়ক গায়েনই ‘গাজি’। এখানে গাজি রূপক, অর্থ-জ্ঞানী, গাজির গান- জ্ঞানীর গান।’ লোক-বিশ্বাস মতে, গাজি হলেন- গায়েরি পীর। সেকালে গ্রামের নিরক্ষর লোকজন রোগমুক্তি, সন্তান কামনা ইত্যাদির জন্য গাজির গানের আয়োজন ও মানত করতো। গাজির গানের মূল গায়ককে ‘গায়েন’ বলা হতো।
একজন গায়েন, ‘ন্যাউট্টা পোয়া’ বা নাটুয়া বালক, দোহারি ও ‘বাইন’ বা বাদক নিয়ে গাজির গানের দল গঠিত হতো। এ দেশে গণমানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, প্রেম-বিবাহ কিংবা ডাকাতের হৃদয় পরিবর্তনের কাহিনী বা নানা উপকথা নিয়ে গাজির গান রচিত ও গীত হতো। বিচিত্র ধরনের রঙিন পাজামা ও ঢোলা লম্বা আচকান পরে মাথায় পাগড়ি বেঁধে গাজির গানের মূল গায়েন আসরে নামতেন।
হালদা ফাডা গান- উত্তর চট্টগ্রামের হালদা নদীর নামানুসারে হয়েছে। নৌকা-সাম্পানের মাঝি-মাল্লারা নদীতে নৌকা-সাম্পান বেয়ে যাবার সময় এই গান গাইতেন। গান গাওয়া হতো উঁচু পর্দায়। হালদা ফাডা গান অনেকটা ভাটিয়ালি গানের মতো। তবে যন্ত্র ছাড়া সুরের সামঞ্জস্য রক্ষা করতে হয়। অধিকাংশ হালদা ফাডা গানে উপান্ত স্বরের মিল আছে।
হঁঅলা- চট্টগ্রামের গ্রামাঞ্চলে বিয়ে-শাদি, খৎনা, মেয়েদের কর্ণছেদন উপলক্ষে মহিলা মহলে মহিলারা নেচে নেচে এই গান গেয়ে থাকেন। হঁঅলা গানের মহলে পুরুষদের প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ। হঁঅলা গান এতই জনপ্রিয় ছিল যে পেশাদার হঁঅলা গায়িকারাও ছিলেন।
হাইল্যা সাইর- আমন মওসুমে ধান রোপণের সময় চাষিরা এ গান গাইতেন। এই গান সারি গানেরই মতো।
পাইন্যা সাইর- সন্দ্বীপের অধিবাসীরা হাইল্যা সাইরের গানকে পাইন্যা সাইর বলে থাকেন। এই গানের দলে ৮/১০ জন করে গায়ত থাকত। হাইল্যা সাইর ও পাইন্যা সাইর সমবেত সঙ্গীত। একই কণ্ঠে গাওয়া হলেও দোহারেরা ধুয়া ধরতেন।
পালাগান- মূলত কাব্যে বর্ণিত লোককাহিনীর গীতরূপ। চট্টগ্রামের লোকগীতিকা বা গাথাকাব্যে সুরারোপ করে তন্ত্রীলয় সমন্বিত করে অর্থাৎ তাল ও বাদ্যযন্ত্রী সহযোগেই পালাগান পরিবেশিত হতো। সাহিত্যিক আশুতোষ চৌধুরী দীর্ঘদিন ধরে বহু কষ্ট স্বীকার করে নেজাম ডাকাইতের পালা, কাফনচোরা ইত্যাদি প্রায় ৭৬টি লোকগীতিকা বা পালা সংগ্রহ করেছিলেন।
এ সবের মধ্যে ৯টি গীতিকা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত দীনেশ সেন সম্পাদিত পূর্ববঙ্গগীতিকা নামে গাথা কাব্য সংকলনে স্থান পেয়েছে। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকেও পালাগানের প্রচলন ছিল। পালাগান বা লোকগীতিকা সংগ্রহে ষাটের দশকে অসামান্য অবদান রেখেছেন আবদুস সাত্তার চৌধুরী।
বাংলা একাডেমি ঢাকায় নিয়োজিত সংগ্রাহক হিসেবে ১৯৬১ থেকে ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তিনি ২১টি পালাগান সংগ্রহ করে বাংলা একাডেমিতে জমা দেন। এসব পালাগানের মধ্যে ১৪টির পাঠ বাংলা একাডেমি প্রকাশিত ‘লোকসাহিত্য’ এবং ‘বাংলা একাডেমি ফোকলোর সংকলন’ সিরিজের বিভিন্ন খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।
এসব পালাগানের পাঠ বাংলা একাডেমি ফোকলোর আর্কাইভস-এ সংরক্ষিত আছে। এছাড়াও তিনি কিছু পালাগান সংগ্রহ করেছিলেন বলে জানা যায়। পালাগানের গায়কদের মধ্যে সেকান্দার বাইন, অলিয়র রহমান (অইল্যা আঁধা), অজু পাগলা, ওমর বৈদ্য, নবচন্দ্র ধুপি, নূর হোসেন, হায়দার আলী, আঁধা মকবুল, বেলায়েত আলী, হাকিম খাঁ, গুণা মিঞা, পৈথানচন্দ্র দে প্রমুখ শিল্পীর নাম পাওয়া যায়। এঁরা সকলে ছিলেন চট্টগ্রামের অধিবাসী।
মাইজভাণ্ডারি- ফটিকছড়ি থানার মাইজভাণ্ডার নিবাসী সুফি সাধক মওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ সাহেব প্রবর্তিত মাইজভাণ্ডারি তরিকার সাধন সঙ্গীত হিসেবে মাইজভাণ্ডরি গানের উদ্ভব। দলবদ্ধভাবে সুর, তান, লয়ে ঢোলকের তালে তালে এই গান গীত হয়। মাইজভাণ্ডারি গানের অন্যতম খ্যাতনামা শিল্পী ছিলেন কবিয়াল রমেশ শীল ও তাঁর সম্প্রদায়। বর্তমানে মুলকুতের রহমান, মহি আল ভাণ্ডারি, ইকবাল হায়দার, জুনু পাগলা প্রমুখ শিল্পী মাইজভাণ্ডারি গান পরিবেশন করে যাচ্ছেন।
ফুলপাট গান- নৃত্য সহযোগে পরিবেশন করতেন চট্টগ্রামের ডোম সম্প্রদায়।
লোক বাদ্যযন্ত্র- চট্টগ্রামে ঢোল, জোড়খাই, দবর, সানাই, নঅদি (নহবত), ঢাক, দোতারা, একতারা ইত্যাদিই প্রধান। হাড়ি ডোম ইত্যাদি মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের লোকরাই ঢোল, দবর, সানাই-এর মূল শিল্পী। এরা ঢাকি নামেও খ্যাত। অতীতে চট্টগ্রামে বেশ কয়েকজন ওস্তাদ ঢোল ও নঅদা বাদক ছিলেন।
দীনবন্ধু, ধনীরাম, হরিমোহন, জগৎ, উমাচরণ, অনন্ত প্রমুখ সেকালের কয়েকজন গুণী ঢোলবাদক ও সানাই বাদকের নাম সংগ্রহ করা গেছে। এরা সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণির বিধায় এইসব গুণী শিল্পীকে কেউ মনে রাখেননি। বর্ষীয়ান শিল্পী বিনয় বাঁশি দেশের একজন শ্রেষ্ঠ ঢোল বাদক ছিলেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গে বিয়েও ঢোলবাদনে অপূর্ব পারঙ্গমতা প্রদর্শন করেছেন।
চট্টগ্রামের বিভিন্ন প্রাচীন লোকগীতিগুলোর মধ্যে মাইজভাণ্ডারি গান ছাড়া অন্য ধরনের গানগুলো উঠে গেছে বললেই চলে। হঁঅলা গান গ্রামাঞ্চলে কোথাও কোথাও কদাচিৎ গীত হয়। তবে হালদা ফাডা গান এখনও গ্রামে-গঞ্জে শোনা যায়। এইচ এম ভি ১৯৪০-৪১ খ্রিস্টাব্দের দিকে চট্টগ্রামের পল্লীগীতি শিল্পী মোহাম্মদ নাসিরের কণ্ঠে হালদা ফাডা গান বা চট্টগ্রামের লোকসঙ্গীত রেকর্ড করে।
চট্টগ্রামে অনেকেই লোকসঙ্গীতের চর্চা করেছেন- এঁদের মধ্যে লক্ষ্মীপদ আচার্য, শাক্যমিত্র বড়ুয়া, এম এন আকতার, আবদুল গফুর হালী, নুরুল ইসলাম তালুদকার, কল্পনা লালা, সঞ্জিত আচার্য, কল্যাণী ঘোষ, আবদুর রহিম প্রমুখ রয়েছেন।
কীত্তন
চট্টগ্রামে অতীতে কীত্তন গানের খুব সমাদর ছিল এবং বর্তমানে হিন্দু সম্প্রদায়ের মহোৎসবগুলোতে অষ্টপ্রহর বা ষোড়শ প্রহর নাম সংকীর্ত্তন হয়। বর্তমান শতাব্দীর সত্তরের দশক পর্যন্ত পালা কীত্তনেরও প্রচলন ছিল। পালা কীত্তনের মধ্যে নিমাই সন্ন্যাস, নৌকা বিলাস, মাথুর প্রভৃতি পালা শহর ও গ্রামের জনগণকে আনন্দ দিত। পদাবলী কীত্তনিয়া মাখনলাল ব্যানার্জি ও তাঁর পুত্র গোপাল বানার্জী খুবই খ্যাতনামা ছিলেন।
পালা কীত্তনে, বামা ঠাকুর, শ্যামা ঠাকুর, কৃষ্ণ ঠাকুর সত্যেন্দ্র রুদ্র, মহেন্দ্র চক্রবর্তী, জ্ঞান সাধু, মনোরঞ্জন দে ছিলেন সুপরিচিত কীত্তনিয়া। সঙ্গীত গুণী প্রিয়দারঞ্জন সেনগুপ্তের পত্নী বনবীথি সেনগুপ্তও কীত্তন গানের শিল্পী ছিলেন। বিংশ শতকের ষাট ও সত্তর দশকে মায়া চক্রবর্তী ও প্রভা দে কীত্তনের শিল্পী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যেও কীত্তনের প্রচলন ছিল। সঙ্গীতজ্ঞ জগদানন্দ বড়ুয়ার পিতা শিক্ষাবিদ মোহনচন্দ্র বড়ুয়া বহু বৌদ্ধ কীত্তনের রচয়িতা। তিনি নিজেও ছিলেন কীত্তনিয়া। তাঁর রচিত সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ ও মার বিজয় ঢপকীত্তনের ঢঙে ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে পরিবেশিত হয়েছিল।
ইসলামি গান
প্রাচীনকাল থেকে চট্টগ্রামে কাওয়ালি, গজল, হামদ্, নাত্, মারফতি, মুর্শিদি ইত্যাদি ধর্মীয় ভক্তিগীতির চর্চা হয়ে আসছে। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে শিল্পী আবু কাওয়ালের খ্যাতি সুদূর কলকাতা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি মোটিয়াবুরুজের নবাব ওয়াজেদ আলি সাহেবের দরবারের ওস্তাদ বংশীয়দের কাছে তালিম নিয়েছিলেন। আবু কাওয়ালের সমকালীন ছিলেন রশীদ কাওয়াল ও উকিল কাওয়াল। পরবর্তীতে সেলিম নিজামী, ইসলাম কাওয়াল, আবদুল মান্নান কাওয়াল প্রমুখ কাওয়ালি পরিবেশন করে যাচ্ছেন।
কবি গান
কবিগানে চট্টগ্রামের অবদান ঐতিহাসিক। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে নাগরিক সংস্কৃতির বিকাশজনিত রুচি পরিবর্তনের কারণে কবিগান প্রায় বিবরবাসী হবার উপক্রম হয়েছিল। সেই দুঃসময়ে গণজাগরণে কবিগানের অন্তর্নির্হিত শক্তি পুনরাবিষ্কারে ঢাকা ও চট্টগ্রামের কবিয়াল দল এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন। কবিয়ালদের সেই ভূমিকা কবিগানে নতুন মাত্রা সংযোজন করে। বর্তমান শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে প্রগতিশীল বামপন্থীদের উদ্যোগে চট্টগ্রামেই প্রথম কবিয়ালদের সংগঠিত করার চেষ্টা হয়েছিল। এবং এর লক্ষ্য ছিল কবিগানকে অশ্লীলতা ও চটুলতা মুক্ত করে জনগণের আন্দোলন ও সংগ্রামের অন্যতম হাতিয়ার করে তোলা।
উনবিংশ শতাব্দীতে গঙ্গাচরণ জলদাস, প্রাণকৃষ্ণ জলদাস, সুবল ভট্ট, অন্নদা নট্ট, নবীন ঠাকুর, অপর্ণাচরণ জলদাস, চিন্তাহরণ, আজগর আলী, মোহন বাঁশি, হরকুমার শীল প্রমুখ কবিয়াল চট্টগ্রামে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এঁদের কেউ কেউ বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও জীবিত ছিলেন। কবিয়াল রমেশ শীল ছিলেন নবীর ঠাকুরের শিষ্য এবং আজগর আলি ছিলেন কবিয়াল করিম বকশের ওস্তাদ।
বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে চট্টগ্রাম শহরেও কবিগান-এর আসর বসতো। কবিয়াল রমেশ শীল তরুণ বয়সে এ ধরনের একটি আসরেই কবিয়াল মোহন বাঁশির বিপক্ষে লড়াইয়ে নেমে প্রথম জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। কবিয়াল রমেশ শীল কবিগানের যুগস্রষ্টা। ঢাকার হরিচরণ আচার্য ও তাঁর সম্প্রদায় কবিগানে ‘ভাষায় ও উপস্থাপনায় শালীনতা ও সমুন্নতি’ এনেছিলেন।
হরিচরণ যুগেই ‘অঞ্চল প্রীতির স্থলে স্বদেশ প্রীতি এবং জাত-পাতের ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িকতার স্থলে উদার মানসিকতার হাওয়া লেগেছিল’। কিন্তু তখনও কবিগানে দেশচেতনার সঙ্গে বিশ্বচেতনার, উদার মানবিকতার সঙ্গে সংগ্রামী বাস্তবতার, অসাম্প্রদায়িক লোকায়ত ধর্ম প্রবাহের সঙ্গে শ্রেণি চেতনার সমন্বয় ঘটেনি।
হরিচরণের এই অসমাপ্ত কাজ সম্পাদন করেন রমেশ শীলের নেতৃত্বে ফণী বড়ুয়া, রাইগোপাল, এয়াকুব আলী, হেমায়েত আলী প্রমুখ কবিয়াল। কবিগানের ঐতিহ্যবাহী আঙ্গিককে গণজাগৃতির হাতিয়ারে পরিণত করে রমেশ শীল সম্প্রদায় কবিগানের নবদিগন্ত উন্মোচন করেছেন।
১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে রমেশ শীলকে সভাপতি ও ফণী বড়ুয়াকে সম্পাদক করে ‘চট্টগ্রাম কবি সমিতি’ নামে গঠিত কবিয়ালদের সংগঠনই ছিল এই নতুন দিগন্ত উন্মোচনের সহায়ক শক্তি। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে রাউজানের বাগোয়ানে অনুষ্ঠিত চট্টগ্রাম জেলা কৃষক সম্মেলনের মণ্ডপে রমেশ শীলের নেতৃত্বে চাষি ও মজুতদার শীর্ষক এক কবির লড়াই হয়েছিল।
সম্ভবত এই সম্মেলনেই নতুন যুগের নতুন রীতির কবিগানের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। ১৯৬৯-৭০ সালে বাঙালি জাতীয়বাদী আন্দোলনে কবিয়াল এয়াকুব আলীর নেতৃত্বে কবিয়ালরা চট্টগ্রামসহ সমগ্র বাংলাদেশে কবিগান পরিবেশন করে স্বাধীনতা আন্দোলনের যে গণজোয়ার সৃষ্টি করেছিলেন তা স্বীকার না করলেই নয়।
চট্টগ্রামের কবিগানের স্বাতন্ত্র্য ও নতুনত্ব তথা কবি গানের নতুন ধারার প্রতি বঙ্গীয় সারস্বত সমাজের প্রথম দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল বঙ্গ প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পী সম্মেলনে। এর মূলে ছিল রমেশ শীলের প্রতিভা। এই সম্মেলনে কবিয়াল রমেশ শীল ও ফণী বড়ুয়া জুটি পশ্চিমবঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবিয়াল শেখ গোমানী ও তাঁর শিষ্য লম্বোদর চক্রবর্তীর জুটিকে কবির লড়াইতে পরাজিত করেন।
সে সময় এটা অভাবিত ছিল। পরবর্তীকালে রমেশ শীলের প্রভাব পশ্চিম বঙ্গের কবিগান তথা তরজা গানেও পড়ে। রমেশ শীল সম্প্রদায় ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারত শান্তি সম্মেলনেও কবিগান পরিবেশন করে কয়েক হাজার দর্শককে মুগ্ধ ও বিস্মিত করেছিলেন।
চট্টগ্রামের কবিগানের সমৃদ্ধিতে রমেশ শীলের সমকালীন কবিয়াল করিম বক্শের অবদান শ্রদ্ধাভরে স্মরণীয়। তাঁর সুযোগ্য শিষ্য কবিয়াল মনীন্দ্র দাসও কবিগানে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। কবিয়াল এয়াকুব আলী ও তাঁর সম্প্রদায় দীর্ঘ তিন দশক ধরে কবিগান পরিবেশন করে গেছেন। তিনি প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।
রমেশ শীলের পুত্র যজ্ঞেশ্বর শীল, অনুসারী রাইমোহন বড়ুয়া প্রমুখ চট্টগ্রামের কবিগানের ইতিহাসে স্মরণীয় নাম। রমেশ শীলের ঐতিহ্য-আদর্শকে সর্বদা সমুন্নত রাখতে আজীবন চেষ্টা করেছেন কবিয়াল ফণী বড়ুয়া ও কবিয়াল এয়াকুব আলী। বাংলা কবিগানে এবং নতুন যুগের কবিগানে রমেশ শীলের পরেই তাঁদের নাম স্মরণীয়।